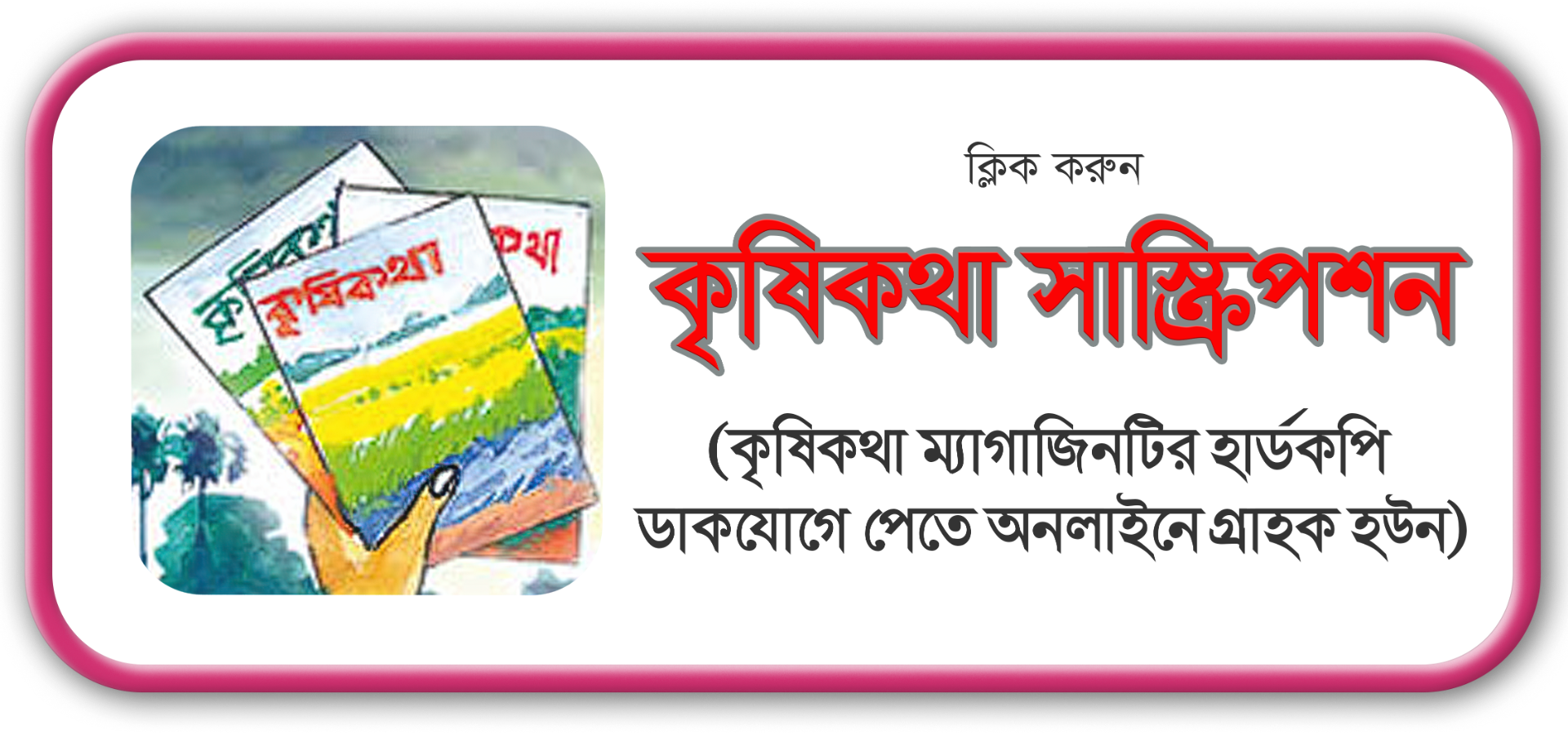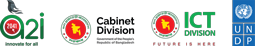Wellcome to National Portal
কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Text size
A
A
A
Color
C
C
C
C
কৃষি কথা

সম্পাদকীয়
সম্পাদকীয়
ফাল্গুন মাস। রবি মৌসুমের শেষান্তে। শীতে ম্রিয়মাণ প্রকৃতি বসন্তের জাদুময়ী স্পর্শে হয়ে উঠে প্রাণবন্ত। এ সময় আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি গাছ মুকুলে ভরে যায় এবং মুকুলের গন্ধে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রকৃতির সাথে আমাদের জনজীবনেও কাজের আগমন ঘটে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে বীর কৃষিজীবী ভাইবোনেরা পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য...
Details

সূচিপত্র
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ
বারি আলুবোখারা-১ এর আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি ৩
ড. শৈলেন্দ্র নাথ মজুমদার, ড. মো. আলাউদ্দিন খান, রূম্পা সরকার
মুগডালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং চাষাবাদ পদ্ধতি ৬
ড. এম. মনজুুরুল আলম মন্ডল
পরিবর্তিত জলাবায়ুতে টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ৮
হাছিনা আকতার
লিচুর গান্ধী পোকার ক্ষতি ও প্রতিকার ১০
শ্রীমা মন্ডল বর্ষা, ড. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
পাটের ফলন বৃদ্ধি ও পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় ন্যানো...
Details

বারি-আলুবোখারা-১-এর-আধুনিক- উৎপাদন-প্রযুক্তি
বারি আলুবোখারা-১ এর আধুনিক
উৎপাদন প্রযুক্তি
ড. শৈলেন্দ্র নাথ মজুমদার১
ড. মো. আলাউদ্দিন খান২ রূম্পা সরকার৩
আলুবোখারা মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি পত্রঝরা কাষ্ঠল জাতীয় ঝোপালো উদ্ভিদ। ফুলের রং সাদা। ডিম্বাকৃতি ফলের ভেতরে একটি কঠিন আবরণযুক্ত আঁটি থাকে এবং এর চারিদিকে ভক্ষণযোগ্য মাংসল বহিরাবরণ থাকে। অপরিপক্ব অবস্থায় ফলের রং সবুজ এবং পরিপক্ব অবস্থায় ফলের...
Details

মুগডালের-অর্থনৈতিক-গুরুত্ব-এবং-চাষাবাদ-পদ্ধতি
মুগডালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব
এবং চাষাবাদ পদ্ধতি
ড. এম. মনজুরুল আলম মন্ডল
বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি স্বল্পতা দূর করতে, মাটির হারানো উর্বরশক্তি ফিরে পেতে, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে মুগ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। এ দেশের সাধারণ গরিব মানুষের পক্ষে প্রাণিজ আমিষের উৎস...
Details

পরিবর্তিত-জলবায়ুতে-টেকসই-মৃত্তিকা-ব্যবস্থাপনা
পরিবর্তিত জলবায়ুতে টেকসই
মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা
হাছিনা আকতার
দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষি জমির উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অব্যাহত চাপ, প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য হারে কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে নানা প্রকারের দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন- অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, খরা,...
Details

লিচুর গান্ধী পোকার ক্ষতি ও প্রতিকার
লিচুর গান্ধী পোকার ক্ষতি ও প্রতিকার
শ্রীমা মন্ডল বর্ষা১ ড. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ২
লিচু বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ও সুস্বাদু গ্রীষ্মকালীন ফল, যা পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়। বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলায় বেশি পরিমাণে লিচু উৎপন্ন হয়। তবে বর্তমানে লিচু চাষে অন্যতম প্রধান বাধা হলো লিচুর গান্ধী...
Details

পাটের-ফলন-বৃদ্ধি-ও-পরিবেশ-ভারসাম্য- রক্ষায়-ন্যানো-সারের-ব্যবহার
পাটের ফলন বৃদ্ধি ও পরিবেশ ভারসাম্য
রক্ষায় ন্যানো সারের ব্যবহার
ড. মো. আবু সায়েম জিকু
বাংলাদেশে পাট ফসল আবাদ করার জন্য বপনের সময়, জমি নির্বাচন, জলবায়ু, সঠিক আন্তঃপরিচর্যা এবং পরিমাণ মতো সার প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। অন্যথায় পাট ফসলের কাক্সিক্ষত ফলন সম্ভব নয়। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া,...
Details

পুষ্টিমানে-ভরপুর-লাভজনক-ফসল-চিচিঙ্গা
পুষ্টিমানে ভরপুর লাভজনক ফসল চিচিঙ্গা
কৃষিবিদ মনিরুল হক রোমেল
চিচিঙ্গা বাংলাদেশের সকলের নিকট প্রিয় অন্যতম প্রধান গ্রীষ্মকালীন সবজি। এর অনেক ঔষধী গুণ আছে। এটা মূলত কুমড়াগোত্রীয় সবজি। চিচিংগা তরকারি, ভাজি ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় রান্না করে খাওয়া হয়। চিচিংগার ১০০ ভাগ ভক্ষণযোগ্য অংশে ৯৫ ভাগ পানি, ৩.২-৩.৭ গ্রাম শর্করা, ০.৪-০.৭ গ্রাম আমিষ, ...
Details

জারা-লেবুর-উৎপাদন-ও-ব্যবস্থাপনা
জারা লেবুর উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা
ডিপ্লোমা কৃষিবিদ মো: জুলফিকার আলী
জারা লেবু অত্যন্ত জনপ্রিয় ও রপ্তানিযোগ্য ফসল। সাধারণ লেবুর চেয়ে জারা লেবু একটু ব্যতিক্রমই বটে। জারা লেবুর রস নয় মূলত বাকল খাওয়া হয়। খাবার টেবিলে জারা লেবুর সালাদের বেশ কদর রয়েছে। লেবুটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আকার সাধারণ লেবুর চেয়ে বেশ বড়, এক...
Details

ছোট-মাছের-বড়-পুষ্টিগুণ
ছোট মাছের বড় পুষ্টিগুণ
ড. ডেভিড রিন্টু দাস১ শাহনাজ পারভিন২
নদীমাতৃক আমাদের এই দেশে অসংখ্য জলাশয় আছে। এসব জলাশয় ছোট-বড় মাছে ভরপুর। মিঠাপানিতে ২৬০ প্রজাতির মাছ রয়েছে। এগুলোকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। মূলত রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, আইর, বোয়াল, ইলিশ, পাঙ্গাস, চিতল এগুলো বড় মাছের তালিকায় রয়েছে। মাঝারি আকারের মাছের...
Details

মাটিতে-জৈব-পদার্থের-ঘাটতি-পূরণে- গোবর-সার-ও-পোল্ট্রি-ম্যানিওর
মাটিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি পূরণে
গোবর সার ও পোল্ট্রি ম্যানিওর
ডা: মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল এবং কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটিরও বেশি। দেশের প্রায় ৬৪ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল (বিশ^ব্যাংক, ২০১৭)। আর কৃষি উৎপাদনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত মাটির গুণাগুণ। আমাদের...
Details

কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা-ব্যবহারে-কৃষিক্ষেত্রে-বাড়বে-উৎপাদনশীলতা
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (অও) ব্যবহারে
কৃষিক্ষেত্রে বাড়বে উৎপাদনশীলতা
ড. মোঃ কামরুজ্জামান১ সৌরভ অধিকারী২
বাংলাদেশের কৃষি খাত দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি। কৃষিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ। যেমন : জনসংখ্যা ১.২০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনঘটিত প্রতিকূলতা যেমন-লবণাক্ততা, খরা, বন্যা ইত্যাদির কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার হেক্টর আবাদি জমি নষ্ট হচ্ছে। মাটির...
Details

তুলা-ফসলের-বহুমুখী-ব্যবহার-ও-অমিত-সম্ভাবনা
তুলা ফসলের বহুমুখী ব্যবহার
ও অমিত সম্ভাবনা
১ড. মোঃ গাজী গোলাম মর্তুজা ২ড. মোঃ কামরুল ইসলাম ৩অসীম চন্দ্র শিকদার
বিশ^ব্যাপী তুলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল এবং আন্তর্জাতিক শিল্প ফসল, যা বিশ^ব্যাপী ‘সাদা সোনা’ হিসেবে পরিচিত। অন্নের পরই বস্ত্রের অবস্থান। আর এই বস্ত্রের মূল উপাদান হল তুলা। বর্তমানে বাংলাদেশে তুলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল...
Details

কৃষি-পেশাকে-সম্মানজনক-অবস্থায়-পরিচিত-করানোই-মানিক-রাজার-আশা
কৃষি পেশাকে সম্মানজনক অবস্থায় পরিচিত করানোই মানিক রাজার আশা
মোঃ আবদুর রহমান
প্রতিটি পেশাকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব। একজন উদ্যোক্তা আত্মনির্ভরশীল হন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। কৃষিকে উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন। একজন কৃষি উদ্যোক্তার মূল লক্ষ্য বাজারজাতকরণ ও মুনাফা তৈরি। তাই একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির হতে...
Details

প্রশ্নোত্তর
প্রশ্নোত্তর
কৃষিবিদ ড. আকলিমা খাতুন
নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য আপনার ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও রোগ দমনে সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনা অনুসরণ করুন।
জনাব মো: মমিনুল ইসলাম, উপজেলা : কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা : কিশোরগঞ্জ
প্রশ্ন : তরমুজ চারার গোড়ার দিকে পানি ভেজা দাগ এবং শিকড় পচে যাচ্ছে এবং চারা নেতিয়ে পড়ে গাছ মারা যাচ্ছে, প্রতিকার কী?
উত্তর :...
Details

চৈত্র মাসের কৃষি (১৫ মার্চ-১৩ এপ্রিল)
চৈত্র মাসের কৃষি
(১৫ মার্চ-১৩ এপ্রিল)
কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
চৈত্র মাস। ১৪৩০ বঙ্গাব্দের শেষ মাস। এ সময় বসন্ত ঋতু নতুন করে সাজিয়ে দেয় প্রকৃতিকে। চৈতালী হাওয়া জানান দেয় গ্রীষ্মের আগমন। এ মাসে রবি ফসল ও গ্রীষ্মকালীন ফসলের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম একসাথে করতে হয় বলে কৃষকের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন আসুন আমরা জেনে...
Details