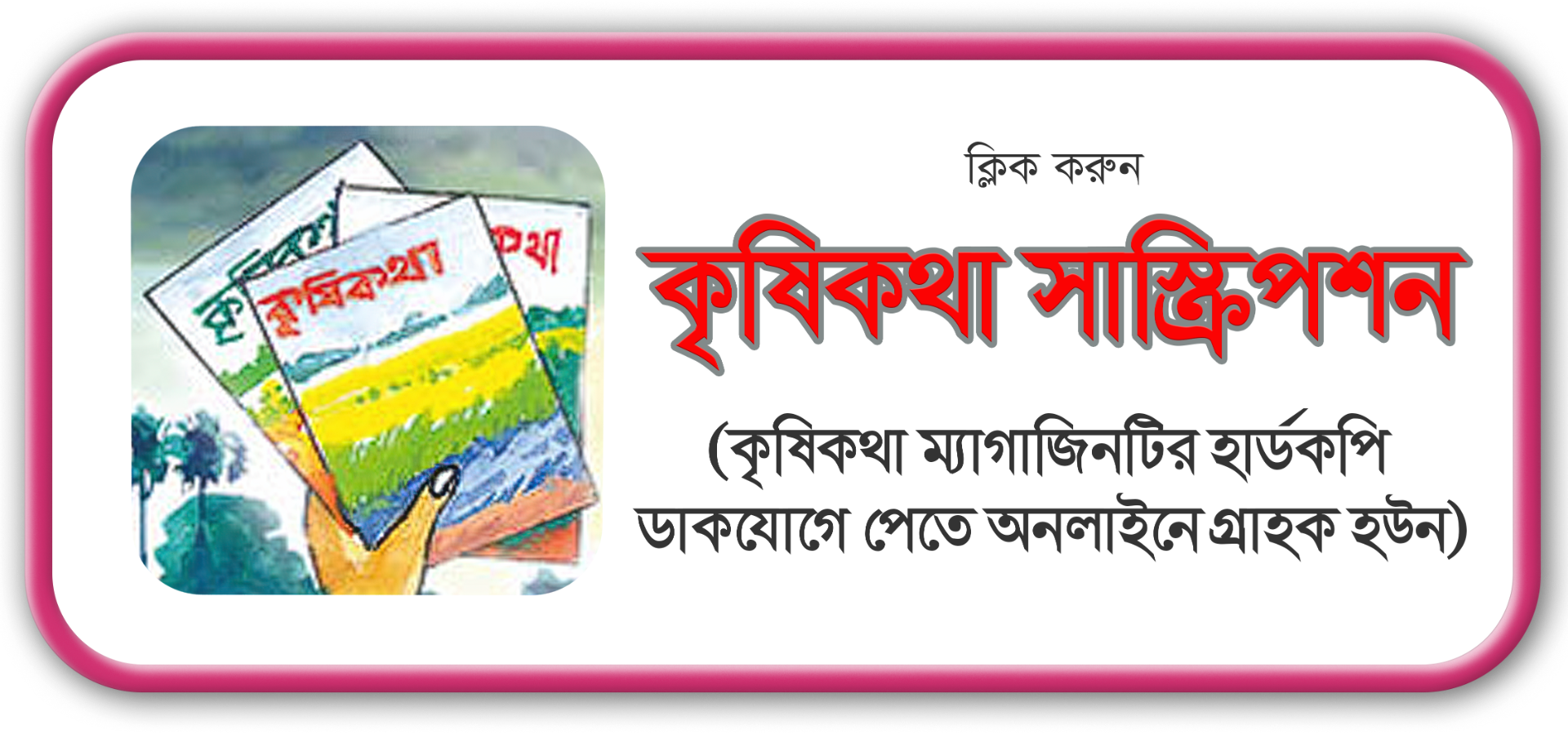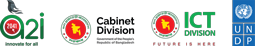ইঁদুরের সাথে চিরন্তন লড়াই

ইঁদুরের সাথে চিরন্তন লড়াই
মো: মোসাদ্দেক হোসেন১ ড. শেখ শামিউল হক২ ড. মো: মোফাজ্জল হোসেন৩
মানুষের সাথে ইঁদুরের লড়াই বহু বছরের পুরনো। সম্ভবত নব্য প্রস্তর যুগ থেকে চলে আসছে এই লড়াই। এই দুই প্রজাতি সব সময় পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলতে চেয়েছে। উজাড় করে দিতে চেয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে। কিন্তু পরিহাস, তারা বসবাসও করছে সবচেয়ে পাশাপাশি, বলতে গেলে গলায় গলায়। ইঁদুর মানুষকে ধ্বংস করতে চেয়েছে নানা রকম রোগ ছড়িয়ে। ইতিহাসে অন্তত দুবার প্লেগের কবলে পড়ে মানবজাতির প্রায় উজাড় হওয়ার দশা হয়েছিল। প্লেগ ছাড়াও আরও বিচিত্র রকম রোগ শরীরে নিয়ে ঘোরাফেরা করে ইঁদুর।
বর্তমান সময়েও ইঁদুরের উৎপাতে পড়ে নাই এমন মানুষ বোধ হয় খুব কম পাওয়া যাবে। এমন কিছু নেই, যা ইঁদুর নষ্ট করে না। বইপুস্তক, কাপড়চোপড়, দলিল-দস্তাবেজ, বিছানা-বালিশ, খাদ্যশস্য সবকিছুই ইঁদুরের দাঁতের শিকার হয়। কেটেকুটে নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু এসবের অধিকাংশই ইঁদুরের খাদ্য নয়। বরং সে যা খায়, তার চেয়ে নষ্ট করে প্রায় দশগুণ। ইঁদুরের চোয়ালের ওপর-নিচে মিলিয়ে মোট দুজোড়া দাঁত থাকে। একে বলে কৃদন্ত কৃদন্তের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই দাঁত সবসময় বাড়তে থাকে। এমনকি ইঁদুরের দৈহিক বৃদ্ধি শেষ হয়ে গেলেও এগুলো বাড়তে থাকে । দাঁতগুলো বেশি বড় হয়ে গেলে সেগুলো ইঁদুরের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই দাঁতগুলোকে ব্যবহার উপযোগী রাখতে ইঁদুরকে বাধ্য হয়ে সেগুলো ছোট রাখতে হয়। আর সেগুলোকে ছোট রাখার উপায় হচ্ছে সবসময় কিছু না কিছু কাটাকুটি করা। কোনো বস্তু কাটার ফলে তাদের দাঁতের সঙ্গে সেই বস্তুর ঘষায় দাঁতের দৈর্ঘ্য সবসময় ঠিক থাকে। যে অংশটা বাড়ত, সেটা এই ঘর্ষণে ক্ষয়ে যায়। আর তাতে দাঁতও থাকে ধারালো ও কার্যকরী। তাই ইঁদুর সময় সুযোগ পেলেই কাটাকুটি খেলায় মেতে ওঠে।
ইঁদুর (জধঃ) হলো কর্ডাটা শ্রেণিভুক্ত রোডেনশিয়া (জড়ফবহঃরধ) বর্গের মিউরিডি (গঁৎরফধব) গোত্রের লম্বা লেজবিশিষ্ট একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। ইঁদুর জধঃঃঁং ও এর নিকট সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি গণের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতি। ইঁদুর সব ধরনের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে এবং কুমেরু ছাড়া পৃথিবীর স্থলভাগের সর্বত্র বিস্তৃৃত। সব ধরনের খাদ্যে অভ্যস্ত হওয়ার সামর্থ্য ও অত্যধিক প্রজনন ক্ষমতার দারুণ পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজনে দক্ষতা রোডেনশিয়া বর্গের সাফল্যের মূল কারণ। চোয়ালের পেশীবিন্যাস ও করোটির নানা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রোডেন্ট বা ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের তিনটি দলে ভাগ করা হয়: কাঠবিড়ালীসদৃশ, ক্যাভিসদৃশ (গিনিপিগ ও অন্যান্য) ও ইঁদুরসদৃশ। স্তন্যপায়ীদের সর্বমোট প্রজাতির এক-চতুর্থাংশের বেশি তৃতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। মিউরিডি গোত্রের সহস্রাধিক প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে আছে ১৮টির অধিক প্রজাতির ইঁদুর।
সারা বিশ্বে বছরে ৩০ ভাগ ফসল ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির শিকার হয়। ইঁদুররা বার্ষিক ভিত্তিতে বিশ্বের অন্তত এক শতাংশ দানাশস্য ধ্বংস করে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে এই সংখ্যা ৩-৫ শতাংশের উপরে। ভারতে, আনুমানিক ২৫-৩০ শতাংশ ফসল কাটা-পরবর্তী শস্য প্রতি বছর ইঁদুরের কারণে নষ্ট হয়ে যায়। ভারত মহাসাগরের নিকটবর্তী অন্য দেশগুলোতেও ইঁদুর এখনও একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা মনে করা হয়। ধান কাটার পূর্বেই ইঁদুরের কাছে হারানো ধানের পরিমাণ হলো মালয়েশিয়াতে ৪-৫ শতাংশ, ফিলিপাইনে ৩-৫ শতাংশ (বিকল্প উৎস ৩০-৩৫ শতাংশ দাবি করে), থাইল্যান্ডে ৬-৭ শতাংশ, ভিয়েতনামে ১০-৩৫ শতাংশ এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৫-৩০ শতাংশ। বাংলাদেশে ইঁদুর ১২ থেকে ১৫ লাখ মেট্রিক টনের অধিক খাদ্যশস্য প্রতি বছর ক্ষতি করে (ডিএই, ২০১৩)। এভাবে ইঁদুর প্রায় সব দেশেই খাদ্য নিরাপত্তাকে বাধাগ্রস্ত করে। ভিটামিন এবং প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবারের ভোক্তা হিসাবে, ইঁদুর প্রায়ই ফসলের ভ্রƒণকে খায় এবং এই প্রক্রিয়ায় অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতা এবং পুষ্টিকে ছিনিয়ে নেয়। খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে দূষিত করে। ইঁদুর প্রতিদিন প্রায় ২৫ গ্রাম ধান বা চাল খায়। মানুষের এই খাদ্য সরবরাহ গ্রাস করার সময়, ইঁদুররা প্রস্রাব, মল এবং রোগজীবাণু জমা রেখে যায় যা মানুষের জন্য খাদ্যকে অখাদ্য করে।
আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তার সাথে ধান ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই ধানকে ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা করা ইঁদুর দমনের প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। বিভিন্ন ধরনের ইঁদুরের মধ্যে কালো ইঁদুর, মাঠের বড় কালো ইঁদুর, নরম পশমযুক্ত মাঠের ইঁদুর ও ছোট লেজযুক্ত ইঁদুর ধানের ক্ষতি করে। এদের মধ্যে কালো ইঁদুর মাঠে ও গুদামে এবং মাঠের বড় কালো ইঁদুর নিম্ন ভূমির জমিতে বেশি আক্রমণ করে। এই ধরনের ইঁদুরের উপস্থিতি সাধারণত কাদার পদচিহ্ন এবং নালায় গর্ত দ্বারা বুঝা যায়। এই প্রাণীর উপদ্রব মাঠে ধান ফসলের পাশাপাশি কর্তন পরবর্তী গুদামজাতকরণ ও সরবরাহের জন্য বড় ক্ষতির কারণ।
পোকামাকড়ের তুলনায় ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করা আপাতত খুব কঠিন মনে হলেও অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় সঠিক জ্ঞান এবং কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এর সংখ্যা লাগসইভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। ইঁদুরের সমস্যা গ্রামের লোকজন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না, সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় কোন পদ্ধতিও পর্যাপ্ত হয় না। তাই ইঁদুর সৃষ্ট এই ক্ষতি স্বাভাবিক হিসেবেই গ্রহণ করে থাকে। গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর ইঁদুর কি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা সঠিকভাবে বুঝে সঠিক সময়ে উপযুক্ত দমন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে পারাই বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
যুগ যুগ ধরে, ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা টোপযুক্ত, কৌশলগতভাবে স্থাপন করা ফাঁদ ব্যবহার করে ইঁদুরের সংখ্যা নির্মূল করার চেষ্টা করেছেন। এর ধারাবাহিকতায় এই উপদ্রব প্রতিরোধের প্রচেষ্টাকে পরিবেশভিত্তিক ইঁদুর ব্যবস্থাপনা (ঊপড়ষড়মরপধষষু-নধংবফ জড়ফবহঃ গধহধমবসবহঃ, ঊইজগ) নামে পরিচিত একটি সিস্টেম হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে, যেখানে ইঁদুর এবং ইঁদুরের আবাসস্থল এবং কৃষি ব্যবস্থাকে বিবেচনা করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ওজজও) এক সময়ের বন্যপ্রাণী গবেষক ড. গ্রান্ট সিঙ্গেলটনের মতে, ইবিআরএম হলো অত্যাবশ্যকীয় সম্পদ-যেমন খাদ্য এবং বাসা বাঁধার জায়গাকে কমানোর একটি প্রচেষ্টা যা ইঁদুরের বছরের পর বছর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। এখানে নিরাপত্তা, আর্থিক লাভ এবং স্থায়ী দমন ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। যদিও সিস্টেমটি এখনও কিছু পরিমাণে ইঁদুরনাশকের উপর নির্ভর করে, এই রাসায়নিকগুলোকে আরও পরিবেশগতভাবে নিরাপদ এবং অ-লক্ষ্য (হড়হ-ঃধৎমবঃ) প্রাণীদের প্রতি বিপদমুক্ত করতে গবেষণা অব্যাহত আছে। আমাদের দেশে ইঁদুর দমনের জন্য মূলত বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ ও রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সঠিকভাবে প্রয়োগ না করার কারণে ইঁদুর দমন কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয় না। প্রাথমিকভাবে রাসায়নিক বালাইনাশককে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের ফলাফল প্রায়ই ব্যর্থ হয়। ইহার কারণ হলো সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার না করা, রাসায়নিক বিষে ইঁদুর প্রতিরোধী হয়ে যাওয়া এবং বিষটোপ লাজুকতা দেখা দেওয়া । ফাঁদ ও রাসায়নিক বিষের সাথে সাথে অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারলে আর্থিক ও পরিবেশগত দিক থেকে ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা টেকসই হবে।
ইঁদুর দমনের পদ্ধতিসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১) ভৌত ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের মাধ্যমে দমন পদ্ধতি ২) রাসায়নিক পদ্ধতিতে দমন এবং ৩) জৈবিক পদ্ধতিতে দমন।
ভৌত ও যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। যেমন- গর্ত খুঁড়ে ইঁদুর বের করে মেরে ফেলা। ইঁদুরের গর্তে পানি ঢেলে এবং মরিচ/খড়/সালফারের ধোঁয়া দিয়ে ইঁদুর বের করে মেরে ফেলা। জমির আইল চিকন রাখা (যেমন ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি), রোপণ দূরত্ব বাড়ানো। বাঁশের, কাঠের, লোহার ও মাটির তৈরি বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করা। যেমন- কেঁচিকল , বাঁশের কল, বাঁশের ফাঁদ, জীবন্ত ইঁদুর ধরার ফাঁদ, মাটির ফাঁদ। উক্ত ফাঁদগুলো আবার দুই ধরনের-জীবন্ত ও মৃত ফাঁদ। জীবন্ত ফাঁদ ব্যবহার করে ব্রি-র মাঠে কার্যকরভাবে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। ফাঁদে খাবার হিসেবে ধান বা চালের সাথে নারিকেল তৈলের মিশ্রণ তৈরি করে নাইলন বা মশারির কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে টোপ হিসেবে দিতে হয়। এ ছাড়াও শুঁটকি মাছ, চিংড়ি মাছ, শামুকের মাংসল অংশ ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাপকভাবে ফাঁদ ব্যবহার কষ্টসাধ্য হলেও ইহার মাধ্যমে ইঁদুরের সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব। বন্যাপ্রবণ এলাকায় কলা গাছের ভেলার উপর ফাঁদ স্থাপন করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। যখন দলগত বা সামাজিকভাবে বৃহৎ এলাকায় ফাঁদ ব্যবহার করা হয় তখন ইহা খুবই কার্যকরী হয়। ফাঁদ দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায় এবং রাসায়নিক ইঁদুরনাশক ব্যবহারের তুলনায় সাশ্রয়ী হয়। যে কোন খাদ্য ও তার অবশিষ্টাংশ অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে, পশুখাদ্য খোলাস্থানে রাখা যাবে না। একই এলাকার ধান ফসল একই সময়ে লাগানো ও কর্তন করতে হবে।
কৃষিক্ষেত্রে অল্প এলাকায় ব্যবহার করা যায়। একটি টোপ ফাঁদ ফসল (আগাম পাকে) চাষ করে ইঁদুর ঢুকতে না পারে এরকম বেড়া দিয়ে এবং বেড়ার মাঝে মাঝে ফাঁক তৈরি করলে ফাঁকের ভেতরের দিকে এক সাথে অনেক ইঁদুর ধরা পড়ে। এভাবে ইঁদুর খাবারের আকর্ষণে ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকার চেষ্টা করলে ধরা পড়বে। এই পদ্ধতির সফলতা পেতে হলে কাছাকাছি সময়ে (১৫ দিনের মধ্যে) আশেপাশের সকল কৃষক এক সাথে ফসল লাগাতে হবে। বেড়ার টোপে ফসল আগাম পাকতে হয়। এই টোপ ফাঁদ বেড়া পদ্ধতি তৈরি করতে যে খরচ হবে তা সকল কৃষক ভাগ করে নিলে খরচ কম হয়। কোন এলাকায় প্রতি বছর ইঁদুরের দ্বারা ১০ ভাগের বেশি ক্ষতি হলে ট্র্যাপ ব্যারিয়ার সিস্টেম গ্রহণ করা দরকার।
পরিশেষে বলা প্রয়োজন, ইঁদুরকে আমাদের পরিবেশের জীববৈচিত্র্য এবং খাদ্য শৃংখলের অংশ বিবেচনা করে ইঁদুর দমন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় প্রজন্মের ইঁদুরনাশক (ক্লের্যাট, ল্যানির্যাট, ব্রোমাপয়েন্ট) ব্যবহারে খুব সতর্ক থাকতে হতে হবে। কারণ এই ইঁদুরনাশকগুলোর দীর্ঘস্থায়ী অবশেষ থাকা এবং কোষকলায় সঞ্চয়নের কারণে আমাদের পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী বিশেষ করে পাখির জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি তৈরি করে।
লেখক : ১প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মোবাইল : ০১৭১২৬২৬৪৫০, ২মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, মোবাইল : ০১৭১৫০১১৩৫১, ৩মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মোবাইল : ০১৭৩১৩৮৬১১৩, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিআরআরআই, গাজীপুর-১৭০১, ই- মেইল : shamiulent@gmail.com