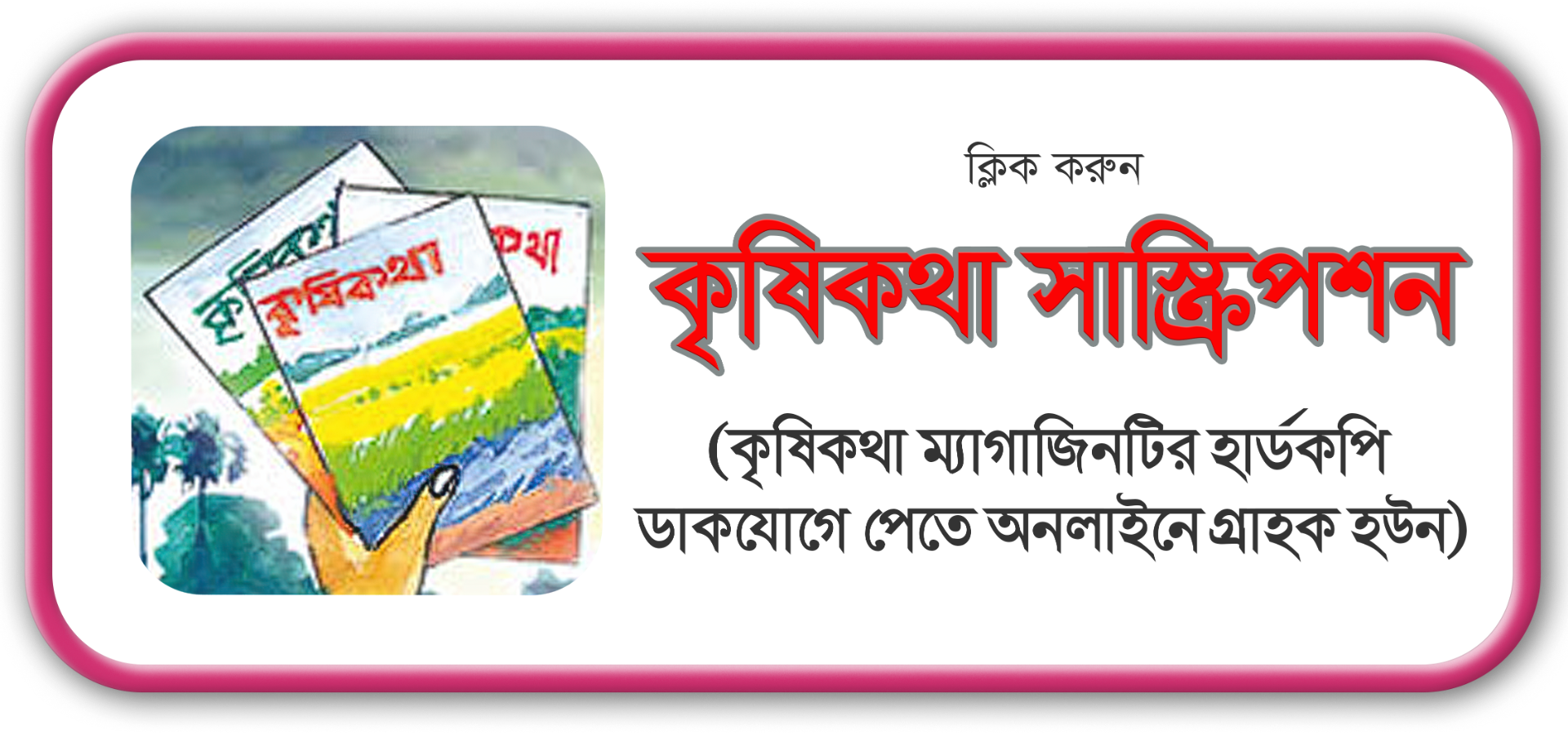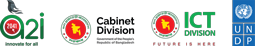যেসব ফলের অস্তিত্ব আছে, খুঁজলে পাওয়া যায় কিন্তু যখন তখন চোখে পড়ে না; দেশের সব এলাকায় জন্মে না; গাছের দেখা মেলে খুব অল্প; চাহিদা কম, প্রাপ্যতা কম, এদের অনেকে বনে বাদাড়ে নিতান্ত অনাদরে অবহেলায় বেড়ে ওঠে; প্রগতির ধারায় কেউ এদের পরিকল্পনায় আনে না; চাষাবাদ দূরে থাক প্রয়োজনীয় খাবার কিংবা পানিও অনেকের ভাগ্যে জোটে না; কোনো কোনোটার ঔষধিগুণ ও মানুষের জন্য উপকারী নিয়ামক, ধাতব ও অন্যান্য প্রাণরাসায়নিক দ্রব্যদিতে সমৃদ্ধ হলেও মানুষের রসনাকে তৃপ্ত করতে পারছে না; অতীতে ফলের সংখ্যা আরও বেশি ছিল। নানা কারণে এবং আমাদের অসচেতনতায় সেসব ফলের অনেকই দেশ থেকে বিল্প্তু হয়ে যাচ্ছে। এরা দিন দিন বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে; এমন ফলকে বিলুপ্তপ্রায় ফল বলা হয়। যেমন- টাকিটুকি, পানকি, চুনকি, লুকলুকি, উড়িআম, বৈঁচি, চামফল, নোয়াল, রক্তগোটা, মাখনা, আমঝুম, মুড়মুড়ি, তিনকরা, সাতকরা, তৈকর, আদা জামির, ডেফল, কাউফল, বনলেবু, চালতা ইত্যাদি।
কিছু কিছু ফল আছে যেগুলোর স্বাদ অনেকের কাছে ভালো লাগে আবার অনেকের কাছে ভালো লাগে না যেমন- ডেওয়া। কলা বা আমের মতো সর্বজনীন আবেদন নিয়ে টেবিলে আসতে পারছে না বলে এরা অচ্ছুত হয়ে পড়েছে। তাই এরা বিলুপ্তির পথে আগাচ্ছে।
ওয়ার্ল্ড কনজার্ভেশন ইউনিয়েনের মতে, পৃথিবীতে প্রায় ৮০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ বিপন্ন প্রায়। এ সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর প্রায় ১৫ লাখ হেক্টর বনভূমি বিলিন হচ্ছে। চলতি সময়ে গবেষকরা বলছেন, প্রায় ২২ থেকে ৪৭ শতাংশ উদ্ভিদ প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। সম্ভবত এগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই ঘটছে। এসব গাছ খরা, ঘূর্র্ণিঝড় ও তাপমাত্রায় প্রতি খুবই সংবেদনশীল, সুতরাং বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদগুলোকে যত্ন নিয়ে সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি। বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ হলো- বৈরী জলবায়ু (সামঞ্জস্যহীন আবহাওয়া, মাটির পিএইচের পরিবর্তন, ভারি ধাতব পদার্থের চাপ, খরা, লবণাক্ততা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা) এবং মানুষ্যজনিত কার্যকলাপ (নিজের স্বার্থে ভূমির অতিরিক্ত ব্যবহার, আবাসভূমি ধ্বংস, নগরায়ন বৃদ্ধি, শিল্পায়ন বৃদ্ধি, কৌলিতাত্ত্বিক ক্ষয়, প্রাকৃতিকভাবে ভূমির ক্ষয়, উচ্চতা হ্রাস, বায়ু দূষণ, জীবনযাপনের পরিবর্তন, আধুনিকায়ন ও ভূমির যথাযথ ব্যবহারে পরিবর্তন ইত্যাদি)।
বাংলাদেশে বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এসব ফলকে আমরা অনেকেই চিনি না, যেমন- লুকলুকি, ডেওয়া, ডেফল, কড়মচা, জঙ্গি বাদাম, কাঠ বাদাম, কাজু বাদাম, গোলাপ জাম, পানি জাম, কালো জাম, তুঁত, তিনকরা, অবরবই, সাতকরা, আদা জামির, কাটালেবু, শাঁসনিলেবু, গ্রেপফ্রুট, তাবা, ত্রিপত্রিকলেবু, জামির, স্টার আপেল, মনফল, আঁশফল, তারকা ফল, দেশি গাব, বিলাতি গাব, আতা, শরিফা, কাউফল, তৈকর, গুটি জাম, খেজুর, জাম, জামরুল, আমলকী, চেস্টনাট, তরমুজ লালিম, টক লেবু, চালতা, ডুমুর, বৈঁচি, টক আতা, তেঁতুল, পানি ফল, সিঙ্গাড়া ফল, দেশি আমড়া, বন্য ডুমুর, বাঙি, চাপালিশ, জিলাপি ফল, পদ্মফল, মাখনা, রুটি ফল, বকুল, ফলসা, ট্যাংফল, চুকুর, রাম কলা, কেন ফল, চিনার, রক্ত গোটা, চিকান, পানকি, চুনকি, টুকটুকি বা টাকিটাকি, আমরুল, পেয়ালাগোটা, চিনাডুলি, লতা ডুমুর, বুদুমচোরা, টমিটমি, কোয়াগোলা, গুটগুটি, বিলিম্বি, কেক ফল, অমৃত ফল, চাউর, আলুবোখারা, চেরি, লকুয়াট, খিরনী, বকুল, ফলসা, বহেড়া, হরীতকী, মহুয়া, পানিফল, মাখনা, পদ্ম ফল ইত্যাদি অন্যতম । এ ফলগুলোর অধিকাংশই এখন বিপন্ন। বসতবাড়িতে দু-একটি গাছ রয়েছে, বনে জঙ্গলেও কিছু আছে। অথচ পুষ্টিগুণ এবং ভেষজ মূল্য একেক ফলে একেক রকম। অথচ এক রকম অবহেলা করেই আমরা আমাদের এসব ফলকে হারাতে বসেছি। তবে আমাদের সৌভাগ্য যে, এখনও অল্প স্বল্প হলেও এর অনেক ফলই দেশের মাটিতে টিকে আছে।
একদিকে প্রধান ফলের চাষ ও উৎপাদন বাড়াতে হবে এ কথা যেমন সত্য তেমনি আমাদের বৈচিত্র্যময় ফলের ভাণ্ডারকেও ধরে রাখতে হবে। এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, আজকের একটি বিলুপ্ত প্রায় ফল আবার আগামী দিনের প্রধান ফল হিসেবে গণ্য হয়ে উঠতে পারে। অনেক স্বল্প পরিচিত অপরিচিত ফলেরও যথেষ্ট বাণিজ্যিক এমনকি রফতানি সম্ভাবনা রয়েছে। সুযোগ রয়েছে জাত উন্নয়নের। লটকন ফলটি এরই মধ্যে ধীরে ধীরে সে জায়গা করে নিচ্ছে। নরসিংদী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ইত্যাদি এলাকায় এখন অনেকেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লটকনের চাষ করে লাখোপতি হয়ে গেছেন। থাইল্যান্ড আঁশফলের মতো অবহেলার এক ফলকে নিয়ে গবেষণা করে এমন রসাল, সুস্বাদু ও অধিক শাঁস বিশিষ্ট জাত উদ্ভাবন করেছে যা রফতানি করে তারা এখন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। থাই লংগানের কথা এখন কে না জানে। টক তেঁতুলকেও তারা মিষ্টি তেঁতুলে পরিণত করে কিছু এলাকায় তার নিবিড় উৎপাদন এলাকা গড়ে তুলেছে থাইল্যান্ড। বহু দেশে রফতানি করছে। ওরা পারে, আমরা পারছি না। অথচ ফল বৈচিত্র্যে আমাদের ঐতিহ্যের অহঙ্কার ওদের চেয়ে কম ছিল না। তাই আমরাও যদি বিলুপ্ত প্রায় কিছু ফল নিয়ে এ ধরনের গবেষণা করতে পারি তাহলে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরাও তাদের মতো মিষ্টি অড়বরই, ম্যাঙ্গোস্টিন, বড় বড় রসাল শাঁসের আঁশফল, হেযারি লিচু রাম্বুটান, ডুরিয়ান, সালাক, ল্যাংসাট, পার্সিমন ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারবেন।
ফল থেকে জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, চাটনি এমনকি আস্ত ফল ক্যানিং (টিনে সংরক্ষণ) ব্যবস্থা নেয়া হলে, অসময়ে দীর্ঘ কাল ধরে খাবার-বাজারজাত করার সুবিধা হবে। মৌসুমে ফলের অপচয় রোধ হবে, বেশি দাম পাওয়া (ভ্যালুঅ্যাড) যাবে। আম, আনারসসহ বেশ কিছু ফল প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রির প্রবণাতা বাড়লেও, কাঁঠাল কলার মতো গুরুত্বপূর্ণ ফল দুটি প্রক্রিয়াজাতকরণের তেমন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। বিপন্ন প্রজাতির ফলগুলোকে সংরক্ষণ করে গবেষণার মাধ্যমে উন্নত জাতে রূপান্তরিত করে প্রক্রিয়াজতের মাধ্যমে খাবার-বাজারজাত করার দিকে এগোতে হবে। ফল রফতানির সুযোগ আহরণ করা উচিত। প্রয়োজনে রফতানিকারককে সম্ভাব্য সব ধরনের সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিলে উৎপাদক ভালো মূল্য পাবে, ফল উৎপাদন সম্প্রসারণে উৎসাহিত হবে, সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের সুযোগ বাড়বে। বর্তমানে আনারস (হানিকুইন), আম, পেঁপে, লটকন, লেবু, সাতকড়া, বরই, জলপাই, আমড়া, এসব ফল বিদেশে (যুক্তরাজ্য, ইতালি, ফ্রান্স, জাপান, কানাডা, আরব ইত্যাদি দেশে রফতানি হচ্ছে। তবে কাঁঠাল ও কলার মতো গুরুত্বপূর্ণ ফল দুটি রফতানির তেমন উদ্যোগ নেই। টিন জাত বা জুস করে ফল রফতানির সুযোগ যথেষ্ট রয়েছে। গবেষকরা মনে করে, বিপন্ন প্রজাতির ফলগুলোর অনেক ফলেরই দেশে এবং বিদেশে অনেক চাহিদা আছে, শুধু দরকার সংরক্ষণ, গবেষণা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ।
তবে এখন যেটা জরুরি, সেটা হলো- এসব বিলুপ্তপ্রায় ও বিপন্ন প্রায় প্রজাতির জার্মপ্লাজমকে দেশের মধ্যে টিকিয়ে রাখা। বিলুপ্ত হওয়ার আগেই পদক্ষেপ নেয়া দরকার। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. এম এ রহিমের প্রচেষ্টায় সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশনের অর্থায়নে ইন্টার কোঅপারেশন-এগ্রো ফরেস্ট্রি ইমপ্রুভমেন্ট পার্টনারশিপের ব্যবস্থাপনায় একটি ফলের জার্মপ্লাজম সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে, গবেষণাও চলছে সেখানে। বাউ-জার্মপ্লাজম সেন্টার, বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সেন্টারটির রটি গোড়াপত্তন হয় ১৯৯১ সনে। তখন প্রকল্পের নাম দেয়া হয় ফ্রুট স্টাডিজ, পরবর্তীকালে এ প্রকল্পের নাম দেয়া হয়, ফল গাছ উন্নয়ন প্রকল্প, এখন এটাকে ফলদ বৃক্ষের ‘জার্মপ্লাজম সেন্টার’ বলা হয়। বর্তমানে এ সেন্টারটি বাংলাদেশ তথা এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ফলদ বৃক্ষের সংগ্রহশালা। ১৯৯১ সনে প্রকল্পটি মাত্র এক একর জায়গা নিয়ে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে কর্মমুখর হয়ে ওঠে, যার ফলাফল ক্রমেই ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষির উন্নয়নে গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণের বিকাশের অগ্রযাত্রায় বিগত ২৮/৭/২০০৭ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ২৭৮তম অধিবেশনে গৃহীত ৩০নং সিদ্ধান্ত মূলে দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির নানা ধরনের ফলের জাত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন বৈশিষ্ট্যায়ন, নিশ্চিতকরণ, বংশ বৃদ্ধিকরণ ও সরকারি ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ‘বাউ-জার্মপ্লাজম সেন্টার’ নামে একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সেন্টারটি ৩২ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এ সেন্টারে ১৮১ প্রজাতির ১১৮৫ জাতের ১০,২৭৩টি মাতৃগাছ আছে। প্রধানত চার ধরনের ফল নিয়ে এ সেন্টারটি তার মূল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন- ১. দেশি প্রধান ফল ২. দেশি অপ্রধান ফল (বিলুপ্তপ্রায় ফলগুলো) ৩. বিদেশি ফল এবং ৪. ঔষধি ফল গাছ। বাউ-জার্মপ্লাজম সেন্টারের মাধ্যমে উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এ দেশের সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক পরিবর্তন ও পুষ্টির অভাব দূরীকরণে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাউ-জার্মপ্লাজম সেন্টারে প্যাসন ফল, জাবাটিকাবা, শানতোল, রাম্বুটান, লংগান, ম্যাঙ্গোস্টিন, সিডলেস লিচু, ডুরিয়ান, অ্যাভোকেডো ইত্যাদি ফল বা ফলের গাছ নিয়ে গবেষণা করছেন ভবিষ্যতে নতুন জাত হিসেবে এ দেশে মুক্তি দিতে।
উপরোল্লিখিত বিলুপ্ত-বিপন্ন প্রায় সব ফলগুলো বাউ-জামপ্লাজম সেন্টার বন, জঙ্গল, পাহাড়, বসতভিটাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সন্ধানের মাধ্যমে সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে এবং এর ওপর নিবিড় গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এটি আশার কথা। সরকারও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসব ফলকে জনপ্রিয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর জাতীয় পর্যায়ে ফল প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন। দেশের প্রতিটি বাড়িতে এ বৃক্ষ রোপণ মৌসুমে বিলুপ্ত প্রায় ফলের অন্তত একটি চারা রোপণ করা উচিত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তা হলে হয়তো খুব অল্প সময়েই জেগে উঠতে পারে হারানো ফলের হারানো রাজ্য, বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে অনেক ফল প্রজাতি। তবে তার আগে যেটা দরকার সেটা হল বিলুপ্ত প্রায় ফলগুলো চিহ্নিত করা এবং এগুলোর ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করা, যেগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পথে সেগুলো রক্ষা করার চেষ্টা করা। আর যেগুলো অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে আছে তাদের উপরে তোলার পথ খোঁজা।
এসব বিলুপ্ত-বিপন্ন প্রায় ফলকে অন্যন্যা বাণিজ্যিক ফলের মতো সঠিকভাবে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা মাফিক চাষ করতে পারলে এসব ফল বিদেশে রফতানি করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আসতে পারে। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে-
অপ্রচলিত ফলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমপ্রসারণ করা।
প্রচলিত চাষ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে পরিকল্পনা মতো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্দিষ্ট ফলের জন্য নির্দিষ্ট উৎপাদন এলাকা গড়ে তুলতে হবে। যেমন- বরিশালে আমড়া, সাতক্ষীরায় ক্ষীরনী, সিলেটে লেবু, বাগেরহাটে কাউফল ইত্যাদি। সেসব অঞ্চলেই এসব ফলভিত্তিক শিল্প কারখানা ও প্রক্রিয়াজতকরণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যমান শিল্পকারখানাগুলোর আধুনিকায়ন করতে হবে।
অপ্রচলিত ফলের প্রতি গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
আধুনিক প্রযুক্তিতে ফল চাষের ওপর জোর দিতে হবে। এজন্য জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও প্রযুক্তি, তথ্য সম্প্রসারণে প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিতে হবে।
গতানুগতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার বদলে বাজারমুখী উৎপাদনের দিকে জোড় দিতে হবে।
ফলের সুষ্ঠু প্রক্রিয়াজাতকরণ, গেডিং, প্যাকিং ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।
উপযুক্ত বিপণন কাঠামো ও নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিপমেন্ট, ওয়্যারহাউস, বিদেশে বাজার খোঁজ ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।
দেশেই এ ফলের অধিক মূল্য সংযোজনের জন্য ফলভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপনে উৎসাহিত করতে হবে।
এ ফলের মানসম্মত চারা-কলম তৈরির জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য বাজারের সাথে তাল রেখে সঠিক প্রজাতি ও জাত নির্বাচন, মাতৃগাছ নির্বাচন, বর্ধন ও সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর জোর দিতে হবে।
উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা গঠন ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি করতে হবে।
ফল উৎপাদনে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন ও নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন ‘ভূমি সংস্কার নীতি’ ‘কৃষি নীতি’ মৃত্তিকা স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।
উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো এগিয়ে আসতে হবে। কৃষি উৎপাদনে ঝুঁকি বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ মৌসুমে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগবালাই, বন্যা ইত্যাদির ফলে কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা হতে পারে। তাই উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। ঝুঁকি কমানো জন্য বীমা প্রচলন করতে হবে। ঝুঁকি বিবেচনা করে জাত নির্বাচন, করতে হবে।
প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পরিকল্পিতভাবে অধিক পরিমাণ জমি সেচের আওতায় আনতে হবে। পানি সেচের উৎসে পানি ধরে রাখার প্রয়োজনীয ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন অনুসারে সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।
উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বাজারে সহজলভ্য হতে হবে। এছাড়াও কৃষকরা যাতে কৃষি উপকরণাদি ন্যায্য মূল্যে পেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
টিস্যু কালচারের মাধ্যেমে বিপন্ন প্রজাতিকে ধরে রাখা সম্ভব। এজন্য এ পদ্ধিতির সম্প্রসারণ হওয়া উচিত।
বৈরী আবহাওয়ায় যেসব প্রজাতি যেসব এলাকায় জন্মানো কঠিন ওইসব এলাকায় টিস্যু কালচার ও ক্রাইয়োপ্রিজারভেশনের মাধ্যমে ওই প্রজাতিকে সংরক্ষণ করে গবেষণার মাধ্যমে অনুপোযোগী এলাকার জাত উদ্ভাবন সম্ভব।
এতে কৌলিতাত্ত্বিক ক্ষয় রোধে সহায়ক হবে। বায়োডাইভার্সিটি নিয়ন্ত্রণে আসবে। পুষ্টিমান সম্পন্ন জাত উদ্ভাবন সম্ভব হবে। দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।
পতিত জমির সদ্য ব্যবহার : চাষযোগ্য পতিত ৩.২৩ লাখ হেক্টর জমিসহ পাহাড়ি, সমুদ্র উপকূলবর্তী ২০ লাখ হেক্টর এবং চর এলাকার প্রায় ২ লাখ হেক্টর জমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চাষাবাদের আওতায় আনা যায়।
সমবায় সমিতির প্রবর্তন ও চাষিদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে আমারা সুফল পেতে পারি। বাংলাদেশে বহুপতিত জমি, খাল-বিল, ডোবা, পাহাড়, চরাঞ্চল, বরেন্দ্র, সমুদ্র উপকূলীয় অধিকাংশ এলাকা এখন অনাবাদি। এগুলো চাষোপযোগী করলে আমারা অধিক পরিমাণে খাদ্য ফলাতে পারি।
খাল কেটে পানি সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন, পোকামাকড় ধ্বংস, প্লাবন ও লোনা পানির হাত হতে ফসল রক্ষ করতে পারেলে খাদ্য ঘাটতি বহুল পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব।
গবেষণা-সম্প্রসারণ-কৃষক-বাজার সংযোগ শক্তিশালী করা। মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
উদ্ভিাবিত নতুন প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষণ, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ইত্যাদি।
প্রফেসর ড. এম এ রহিম*
ড. মো. শামছুল আলম মিঠু**
*পরিচালক, বাউ-জার্মপ্লাজম সেন্টার **সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, বাউ-জার্মপ্লাজম সেন্টার, বাকৃবি, ময়মনসিংহ