কৃষি কথা
 পুষ্টিতে ঠাসা দেশের অবহেলিত জাতীয় ফল
পুষ্টিতে ঠাসা দেশের অবহেলিত জাতীয় ফল
পুষ্টিতে ঠাসা দেশের অবহেলিত জাতীয় ফল
কৃষিবিদ ড. এম. মনির উদ্দিন
কাঁঠাল মূলত ভারতীয় উপ-মহাদেশের ফল, বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনসহ অন্যান্য গ্রীস্মম-লীয় দেশে জন্মায়। সারাদেশেই কমবেশি উৎপাদন হওয়ায় কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল হিসেবে বিবেচিত। কাঁঠালের বৈজ্ঞানিক নাম অৎঃড়পধৎঢ়ঁং ঐড়ষরপবৎড়ঢ়যুষঁং। কাঁঠাল উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। দেশে এমন কোনো জেলা নেই যেখানে কাঁঠাল হয় না। লালমাটি কাঁঠাল উৎপাদনের জন্য সর্বোত্তম। আর এ জন্য সবচেয়ে বেশি কাঁঠাল উৎপাদন হয় মধুপুর ও ভাওয়াল গড় এলাকা ও তিন পার্বত্য জেলায়।
কাঁঠালের খুব বিস্তৃত কৃষি-বাস্তুসংস্থানীয় অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে যার কারণে দেশের প্রতিটি গ্রামেই কাঁঠাল গাছ দেখা যায়। ফল ছাড়া কাঁঠাল গাছের অন্য সব অংশের অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে। দেশে বিশেষ কিছু এলাকায় কাঁঠাল বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে, যার মধ্যে মধুপুর ও ভাওয়াল গড়, পার্বত্য জেলা বান্দরবন, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট উল্লেখযোগ্য। ২০ বছর আগে কাঁঠাল ও আম এ দেশের প্রধান ফল ছিল। সময়ের ব্যবধানে দেশের ফল উৎপাদনে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এখন কাঁঠালের মৌসুমে বাহারি রকমের আম, লিচু, আনারস, পেয়ারাসহ বিভিন্ন রকম ফলের উৎপাদন বেড়েছে যার কারণে চাহিদা কমেছে জাতীয় ফল কাঁঠালের। ২০১৬ সালে, মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণ ছিল প্রতিদিন ৩৫.৮ গ্রাম যা এখন বেড়ে ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছে ৯৫.৪ গ্রাম (ঐওঊঝ, ২০২২)। দেশে এখন ৭২ প্রজাতির ফলের চাষ হচ্ছে যা আগে ছিল ৫৬ প্রজাতির।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বছরে প্রায় ১৯ লাখ টন কাঁঠাল উৎপাদিত হয় এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ এই ফলটির ৪০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১৫ লাখ টন কাঁঠাল উৎপাদিত হয়। অন্য সূত্র মতে, ২০২১ সালে ৬৫,৩৬৪ হেক্টর জমিতে ১৮.৬৯ লাখ টন কাঁঠাল উৎপাদিত হয়েছে, যার ফলন হেক্টরপ্রতি ২৮.৫৯ টন। আগের বছরের তুলনায় উৎপাদন বেড়েছে ৩,৪৯০ টন। কাঁঠাল দেশের মোট ফল উৎপাদনের প্রায় ২২ শতাংশ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে, দেশের মোট ফল উৎপাদন ছিল ১.২২ কোটি টন। দেশের ৩২.১ মিলিয়ন পরিবারের বসতবাড়িতে অবহেলা ও অযতেœ জন্মায় এই জাতীয় ফল।
কাঁঠাল হলো শীর্ষ শ্রেণীর ফল যার মধ্যে পুষ্টির মাত্রা সর্Ÿোচ্চ। দেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় কাঁঠাল ফাইবার, ভিটামিন, প্রোটিন, খনিজ এবং ক্যালরির উৎস হিসেবে গ্রামীণ ও শহরের মানুষের পুষ্টিতে অবদান রাখে। তাছাড়াও কাঁচা ও পাকা উভয় কাঁঠালের মধ্যে যে সব পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়-ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, আয়রণ, ফসফরাস, পটাশিয়াম, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, ভিটামিন-এ, থায়ামিন, রিবোফ্লাবিন, ভিটামিন-সি, পাইরিডক্সিন, নায়াসিন, ফলিক এসিড উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রকার ডালে ২০-২৬ শতাংশ প্রোটিন থাকে, গরুর মাংসে প্রোটিন ২৬-২৭ শতাংশ, মুরগীর মাংসে ৩১ শতাংশ, মাছে ১০-১৭ শতাংশ, আর কাঁচা কাঁঠালে প্রোটিন পাওয়া যায় ১০ শতাংশ। তাই, কাঁঠাল হতে পারে মাছ বা মাংসের বিকল্প খাদ্য উৎস।
গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমাদের শরীরের অর্ধেকেরও বেশি ক্যালরি আসে মাত্র ৯টি উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে যদিও আনুমানিক ২৭,৫০০টি ভোজ্য উদ্ভিদ সারাবিশ্বে রয়েছে। অব্যবহৃত ধরনের খাদ্যের বৈচিত্র্য আনা হলো খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নত করার একটি অন্যতম উপায়। আর তার সহজ এক উদাহরণ হলো কাঁঠালের খাদ্যপণ্যের উৎপাদনের মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসা। বর্তমানে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ও বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কারণে এক শ্রেণীর মানুষের বিশেষ করে চল্লিশর্ধো মানুষের অনেকেই পাকা কাঁঠাল খেতে পারছেন না। অন্যদিকে আঠাযুক্ত হওয়ার কারণে নুতন প্রজন্মের মধ্যেও পাকা কাঁঠাল খাওয়ার প্রবণতা অনেক কম। আর এ সমস্ত কারণে কাঁঠালের এই ব্যাপক পরিমাণ অপচয় হয়ে থাকে।
এই সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে দেশের গবেষকরা কাঁঠাল দিয়ে এমন কিছু খাদ্যপণ্য তৈরি করার চেষ্টা করছেন যা কয়েক মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে। আরেকটি বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশে শুধু পাকা কাঁঠাল খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেহেতু পাকা কাঁঠাল খাওয়ার প্রবণতা বিভিন্ন কারণে কমে গিয়েছে তাই এর বিকল্প অর্থাৎ কাঁচা কাঁঠালের ব্যবহার বাড়াতে হবে। সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে উঠে এসেছে, কাঁচা কাঁঠালের মধ্যে ১০ শতাংশ পর্যন্ত প্রোটিন পাওয়া যায়, যা মাংস বা মাছের বিকল্প হিসেবে খাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কাঁচা কাঁঠালের ব্যবহার যত বেশি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে ততবেশি এই ফলের অপচয় কমে আসবে। কাঁঠাল উৎপাদনের বড় একটি অংশ যদি কাঁচা হিসেবে ব্যবহার বাড়ানো যায়, তা একদিকে যেমন খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়ক হবে সেইসাথে মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তায়ও ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।
অনেক মানুষের ধারণা যে, কাঁঠাল শুধু পাকলেই খাওয়া যায়। কাঁচা কাঁঠাল যে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত পণ্য তৈরি করে খাওয়া যায় এবং পাকা কাঠালের পাল্প বা কোয়া খাওয়া হয়। কাঁঠাল স্বাদের দিক দিয়ে দুই রকমের হয়ে থাকে। প্রথমত, খাজা কাঁঠাল যার পাল্প কিছুটা শক্ত প্রকৃতির, খেতে কচ কচ করে এবং অনেকের কাছে এই কাঁঠাল বেশি পছন্দের। অন্যটি গালা কাঁঠাল যার পাল্প নরম ও রসালো এবং এটি রস করে খাওয়ার জন্য খুবই উপযোগী। কাঁঠালের বীজ একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্যপণ্য যা বিভিন্নভাবে খাওয়া যায়। গ্রামীণ এলাকায় কাঁঠালের বীজ সিদ্ধ করে ভর্তা বানিয়ে ভাতের সাথে খাওয়া একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। অন্যান্য তরকারির সাথেও কাঁঠালের বীজ ব্যবহার করা হয়। আবার বীজ ভেজে খাওয়া যায় যার অন্যরকম একটি স্বাদ রয়েছে।
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কাঁঠাল থেকে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার তৈরি করে সফল হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে কাঁঠালের জ্যাম, আচার, চাটনি, চিপস, কাটলেট, আইসক্রিম, দই, মাংসের বিকল্প হিসেবে কাঁচা কাঁঠালের সবজি বা তরকারী রান্না করে খাওয়া, কাঁঠালের পাউডার, কাঁঠালের বীজের পাউডার এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্যাকেটজাত পণ্য যাতে করে গ্রাহকরা সারাবছর কাঁঠালের তৈরি বিভিন্ন পণ্য বাজারে পেতে পারেন। অর্থাৎ কাঁঠাল থেকে ৩০টিরও বেশি বিকল্প খাদ্যপণ্য তৈরি করে সারাবছর ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে বাজারে কাঁচা কাঁঠালের ভেজিটেবল রোল, কাটলেট, সিংগারা তৈরি করে বাজারে বিক্রয় হচ্ছে। আবার পাকা কাঁঠালের রস দিয়ে আইসক্রিম, কেক, ফ্রুট রোল-আপ তৈরি হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁঠালের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, কাঁঠাল রপ্তানি ক্রমেই বাড়ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কাঁঠাল রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১,০০০ টন। হবিগঞ্জের বড় ও ভালমানের কাঁঠাল রপ্তানি হয় কাতার, ওমান, বাহরাইন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাস্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে। প্রক্রিয়াজাত কাঁঠালও রপ্তানির তালিকায় রয়েছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে প্রক্রিয়াজাত কাঁঠাল পণ্য রপ্তানি শুরু করে এবং এর মাধ্যমে দেশের রপ্তানির পরিসরে বৈচিত্র্য আসে। বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনকারী এবং বণিক সমিতির (ইঅচচগঅ) অধীনে ২০১৯ সালে বেশ কয়েকটি কোম্পানি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশে কাঁঠাল থেকে তৈরি অসমেটিক ডিহাইড্রেটেড খাবার ও কাঁঠালের বীজের গুঁড়া রপ্তানি করেছে।
একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ পাকা কাঁঠালের ১০-১২টি কোয়া খেলে তার অর্ধেক দিনের আহার হয়ে যায়। কাঁঠাল পাকার পর বেশিদিন সংরক্ষণ করা য়ায় না। তাই এর বিকল্প ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে সকল শ্রেণীর মানুষের পুষ্টিমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। কাঁঠালের বীজ ও ফল শুকিয়ে বেকিং ময়দা তৈরি করা যায় যা যে কোন সবজি বা তরকারিতে ব্যবহার করে খাদ্যের মান বাড়ানো যায়। বিএআরসি (ইঅজঈ) কাঁঠালের বার্গারের ফুড ভ্যালু পরীক্ষা করে যা পেয়েছে তাতে কাঁচা কাঁঠালের তৈরি বার্গারের প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁঠালের প্যাটিতে ৯.৭৮ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১০.৮৭ গ্রাম প্রোটিন, ৮.৪৭ গ্রাম চর্বি, ১৯.৩২ গ্রাম ডায়েটারি ফাইবার এবং ১৫৯ কিলোক্যালরি শক্তি থাকে। নিরামিষভোজীদের জন্য কাঁচা কাঁঠালের বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্য জোগান দিতে পারে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও চর্বি। অথচ যথাযথ প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে এই ফলের বিভিন্ন খাদ্যপণ্য দেশের মানুষের পুষ্টিমান উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্বের অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের পুষ্টি উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।
গেইন বাংলাদেশ পুষ্টি সমৃদ্ধ এই জাতীয় ফলটিকে ঘিরে দেশের শিশু, কিশোর, যুবক, মহিলাদের পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখছে। গেইন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. রুদাবা খন্দকার আশা পোষণ করেন যে, কাঁচা ও পাকা কাঁঠাল থেকে বৈচিত্র্যময় নানা ধরনের খাদ্যপণ্য তৈরির মাধ্যমে শিশুসহ সকল শ্রেণীর মানুষের পুষ্টিমান উন্নয়নে সফল ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে এবং কাঁঠালকে নিয়ে এর বহুমুখী ব্যবহার বাড়ানোর জন্য গেইন পরিকল্পনা করছে। সেইসাথে গেইন বাংলাদেশের পোর্টফলিও লিড ও ফুড টেকনোলজি স্পেশালিস্ট ড. আশেক মাহফুজ বলেন, যেহেতু কাঁঠালের বড় একটি অংশ পাকার পর সঠিক প্রক্রিয়াজাত ব্যবস্থা না থাকায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেহেতু কাঁচা কাঁঠালের ব্যবহার যত বেশি বাড়ানো যাবে, এর অপচয় ততটাই কমে আসবে। তাই গেইন কাচা কাঁঠালকে কেন্দ্র করে বৈচিত্র্যময় খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর জোর দেবে যাতে সারাবছর এই বিকল্প খাদ্যপণ্য বাজারে সহজলভ্য হয় এবং একই সাথে দেশের মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখতে পারে।
সবশেষে এটা বলা যায় যে, দেশে প্রতি বছর উৎপাদিত প্রায় ১৯ লাখ টন কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং এজন্য সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এবং দেশের প্রাইভেট সেক্টরগুলোকে একসাথে মিলে কাজ করে যেতে হবে। আর এভাবেই দেশের জাতীয় ফলের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে এর অপচয় রোধ হবে।
লেখক : কনসালট্যান্ট, গেইন বাংলাদেশ, মোবাইল : ০১৭১১৯৮৭১১৩, ই-মেইল : সড়হরৎ.ঁফফরহ@ৎড়পশবঃসধরষ.পড়স
 বালাইনাশকের নিরাপদ ব্যবহারে করণীয়
বালাইনাশকের নিরাপদ ব্যবহারে করণীয়
 জীবনের উৎস মাটি ও পানি
জীবনের উৎস মাটি ও পানি
জীবনের উৎস মাটি ও পানি
হাছিনা আকতার
প্রকৃতির তিনটি প্রধান অমূল্য সম্পদ হচ্ছে- বাতাস, পানি ও মাটি। এই তিনটি উপাদান না থাকলে হয়তো পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বই থাকত না। জীবন ও সভ্যতা শুরু হয় মৃত্তিকা ও পানির আন্তঃসম্পর্কের ক্রিয়াবিক্রিয়ার ফলে। তাই মাটির স্বাস্থ্য ও পানির গুণগত মান ও প্রাপ্যতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যেখানে মাটি ও পানির সমন্বয় নেই-সেখানে জীবন নেই, সভ্যতাও নেই, জীবনের কোলাহল নেই। আমাদের ৯৫ শতাংশ খাদ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আসে মাটি থেকেই। আর একটি আদর্শ মাটিতে প্রায় ৪৫% খনিজ পদার্থ, ৫% জৈব পদার্থ, ২০-৩০% বাতাস এবং ২০-৩০% পানি থাকে; যাতে- মাটি, পানি এবং বাতাস এই তিনটি উপাদানেরই সমন্বয় ঘটেছে। এতে যে কোন একটি উপাদানের ঘাটতি দেখা দিলে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। মাটি ও পানি হলো সেই মাধ্যম যেখানে গাছপালা বেড়ে উঠে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ করে। অনুপযুক্ত মাটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলো মাটির ক্ষয়, মাটির জীববৈচিত্র্য, মাটির উর্বরতা এবং পানির গুণমান এবং পরিমাণকে প্রভাবিত করে। মাটিতে বসবাসকারী জীব নিয়ে গঠিত হয়েছে বিশাল মৃত্তিকা জীববৈচিত্র্য জগৎ। জাতিসংঘের দেওয়া (ওয়ার্ল্ড সয়েল ডে, ২০২২ ওয়েবপেজ) হিসাব অনুযায়ী এক টেবিল চামচ পরিমাণ উর্বর মাটিতে বসবাস করে ৮০০ কোটিরও বেশি জীব। কাজেই মাটিকে শুধু নিরেট জড় পদার্থ হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক নয়। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (যুক্তরাষ্ট্র) বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী প্রফেসর উইলিয়াম হার্সবার্গার সায়েন্স পত্রিকায় ‘মাটি, এক জীবন্ত জিনিস’ শিরোনামে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি অনুর্বর মাটিকে মৃত এবং উর্বর মাটিকে জীবন্ত বলে উল্লেখ করেছিলেন। অতএব, যার জীবন আছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদও রয়েছে।
মাটিকে জীবন্ত বা উর্বর রাখার জন্য মৃত্তিকা জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্যময় উপস্থিতি প্রয়োজন। ভারসাম্যময় অবস্থায় প্রতিনিয়ত এ সব জীব-অণুজীব তাদের জীবন প্রবাহে মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ ডিকম্পোজ করে- মাটি তৈরি, মাটির গঠন উন্নয়ন, পুষ্টি চক্র তৈরি, পানি ধরে রাখা ও তাকে বিশুদ্ধ করা, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ, মৃত্তিকা দূষণ প্রতিকার, ওষুধের উৎস, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ইত্যাদি করে থাকে। এভাবে এক বর্গ সেন্টিমিটার মাটি তৈরি হতে ২০-১০০০ বছর সময় লাগে। বলা হয়ে থাকে, মৃত্তিকা জীববৈচিত্র্য আছে বলেই পৃথিবীর জীব-ভূরাসায়নিক চক্র বজায় আছে এবং এর ফলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকে আছে। কিন্তু মাটি ও পানির অবক্ষয় মাটির জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। আসলে বাংলাদেশে মেরুদ-ী প্রাণী ছাড়া অমেরুদ-ী প্রাণী কিংবা অন্যান্য আণুবীক্ষণিক প্রাণী বা জীব সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত খুবই অপ্রতুল। অথচ এরাই জীববৈচিত্র্যের ৮০ শতাংশেরও বেশি। সব ধরনের বাস্তুতন্ত্রের জন্য এরা অপরিহার্য জীব। বাংলাদেশে এদের বেশির ভাগ সদস্য অনাবিষ্কৃত। সমুদ্রের পর বিশ্বব্যাপী মৃত্তিকা হচ্ছে দ্বিতীয় বড় কার্বন আধার। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) হিসাব অনুযায়ী, মাটির ওপর থেকে ৩০ সেমি. নিচ পর্যন্ত বায়ুম-লের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি কার্বন আছে অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর মৃত্তিকা বায়ুমন্ডল থেকে কার্বনকে আলাদা করে কার্বনের আধার হিসেবে কাজ করে। আর এই কার্বন জমাকরণে মাটিতে থাকা অণুজীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘ মাটিকে অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। কারণ মাটির অবনয়ন (ডিগ্রেডেশন) যত দ্রুত ঘটে থাকে, তত দ্রুত মাটি তৈরি হতে পারে না। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বব্যাপী মাটি ও পানির অবক্ষয় ঘটেছে ব্যাপকভাবে। এফএওর হিসাব অনুযায়ী, পৃথিবীর ৩৩ শতাংশ মাটির অবনয়ন ঘটেছে অর্থাৎ অনুর্বর হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে বছরে এক কোটি ২০ লাখ হেক্টর অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ২৩ হেক্টর ভূমির অবনয়ন ঘটছে। ভূমিক্ষয়ের কারণে প্রতি বছর দুই হাজার ৪০০ টন উর্বর মাটি হারিয়ে যাচ্ছে।
বাংলাদেশে বর্তমানে ফসলি জমি প্রায় ৭.২৯ মিলিয়ন হেক্টর। পৃথিবীর মোট ভুখ-ের প্রায় ১০ শতাংশ জায়গায় ফসল আবাদ হলেও বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ৬০ শতাংশ জমিতে চাষাবাদ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার দক্ষতা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। নিবিড় চাষাবাদের হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্বে একেবারে প্রথম সারিতে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও নগরায়নের জন্য মাটির উপর চাপ বেড়েই চলেছে। আমাদের আবাদী জমি কমে যাচ্ছে অব্যাহতভাবে।
দেশের দক্ষিণের ১৯ জেলার অর্ধেক চাষের জমি লবণাক্ততার শিকার বলে জানা যাচ্ছে (কালের কণ্ঠ, ১৯ নভেম্বর ২০২২)। উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ১৭টি রাসায়নিক পুষ্টি উপাদানের ১৪টি উপাদানই পেয়ে থাকে মাটি ও পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। বাকি ৩টি উদ্ভিদ গ্রহণ করে পানি ও বাতাস থেকে। বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) থেকে প্রকাশিত (২০২০ খ্রি:) একটি গ্রন্থে ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, দেশের কৃষি জমিতে অম্লত্ব বেড়েছে। অন্যদিকে ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, জিংক, বোরন ইত্যাদির পরিমাণ কমেছে। এই অবস্থা নির্দেশ করছে যে, বাংলাদেশের মাটি ক্রমাগতভাবে অবনয়ন হচ্ছে। মাটিতে ৩-৫% জৈব পদার্থ থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ গড়ে ১% এর কাছাকাছি। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ ০.৮% এর নিচে চলে গেলে সে মাটি আর কোন কৃষি কাজের উপযোগী থাকে না।
উক্ত গ্রন্থে নাইট্রোজেন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ক্রমাগতভাবে এই উপাদানও হ্রাসমান। নাইট্রোজেন মাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। নাইট্রোজেন গাছের গ্রহণ উপযোগী করার জন্য এমোনিয়াম অথবা নাইট্রেটে রূপান্তর করতে হয়। এ রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন হয় ইউরেজ নামক এনজাইম, যা তৈরিতে মাটিতে বিদ্যমান অণুজীব প্রধান ভূমিকা পালন করে। মাটির ঘাটতি পূরণের জন্য নাইট্রোজেন সার দেয়া হয়। কিন্তু সে সার ফসলের ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রয়োজীয় অণুজীব মাটিতে না থাকায় প্রয়োগকৃত সারের মাত্র ৩৫% গাছ গ্রহণ করতে পারে, বাকি ৬৫% বাতাসে উড়ে যায় অথবা পানিতে ভেসে যায়। ফলে দূষিত হচ্ছে বাতাস এবং নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-জলাশয়ের পানি। ফলে গাছে নাইট্রোজেনের ঘাটতি থেকেই যায়। ঘাটতি জনিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। আরো বেশি পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা হয়। মাটিতে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন বিষের মতো কাজ করে। মাটি দূষণের ফলে সকল অণুজীব মারা যায়। ফলশ্রুতিতে বেড়ে যাচ্ছে মাটির অম্লত্ব এবং তৈরি হচ্ছে শক্ত কর্ষণস্তর। এছাড়া অণুজীবের ক্রিয়ার দ্বারা তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড যেমন: হিউমিক এসিড, ফালবিক এসিড, কার্বনিক এসিড ইত্যাদি যা সারের সকল উপাদানকে গাছের জন্য গ্রহণোপযোগী করে তোলে। এতে সার প্রয়োগের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং অপচয় কম হয়।
মাটির ক্ষয় এবং দৃঢ়ীকরণ (পড়সঢ়ধপঃরড়হ) মাটির পানি সঞ্চয়, নিষ্কাশন এবং ফিল্টার করার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে এবং বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। স্বাস্থ্যকর মাটি প্রাকৃতিক ফিল্টার হিসাবে গুরুত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এটি মাটিতে অনুপ্রবেশের সাথে সাথে পানিকে বিশুদ্ধ করে এবং সংরক্ষণ করে।
মৃত্তিকা ও পানি অবক্ষয়ের প্রাকৃতিক কারণগুলো হচ্ছে-বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, যার ফলে উপকূল অঞ্চলের মাটিতে সমুদ্রের লবণ পানির অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং ভূগর্ভস্থ পানিতেও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণেও বাঁধ ভেঙে বা বাঁধ উপচে লবণ পানি কৃষি জমিতে ঢুকে জমির লবণাক্ততা বাড়িয়ে স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত করছে। এ ছাড়া শুষ্ক মৌসুমে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানির সাথে লবণ উপরে উঠে আসে। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ২৮.৬ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় এলাকার মধ্যে প্রায় ১০.৫৬ লক্ষ হেক্টর এলাকা বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা কবলিত। মৃত্তিকা ও পানি অবক্ষয়ের জন্য প্রাকৃতিক কারণগুলোর চেয়ে বাংলাদেশে মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলো অধিকতর দায়ী। যেমন: নিম্নমানের সেচ ও নিষ্কাশন পদ্ধতি, ঘেরে লোনাপানি প্রবেশ করিয়ে চিংড়ি চাষ, সমুদ্রের পানি আটকে রেখে লবণ চাষ, পাহাড় কেটে ধ্বংস করা, পাহাড়ের ঢালে জুম চাষের মাধ্যমে আদা, হলুদ চাষ, নির্বিচারে বনায়ন ধ্বংস করা, ভূগর্ভস্থ পানির অধিক ব্যবহার যাতে করে ভারি ধাতুগুলো দ্বারা মৃত্তিকা ও পানি দূষিত হয়, মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, ফসলের অবশিষ্টাংশ জমিতে মিশতে না দেওয়া, শিল্প-কলকারখানা ও ই-বর্জ্য মাটি ও পানিতে ফেলা, অধিক পরিমাণে প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার, শস্য আবর্তন অনুশীলন না করে বার বার একই ফসলের চাষ, জমির অধিক কর্ষণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
যেহেতু মাটি ও পানি খাদ্য উৎপাদন, বাস্তুতন্ত্র এবং মানুষের কল্যাণের জন্য ভিত্তি প্রদান করে, তাই তাদের অমূল্য ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই সম্পদগুলোকে সুরক্ষিত করার জন্য আমরা যে সমস্ত সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে পারি; তা হচ্ছে-
টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা
-অধিক পরিমাণে জৈব পদার্থের ব্যবহার, জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর মৃত্তিকা পানি ধারণ ও প্রাপ্যতা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
-মানসম্পন্ন পানির দক্ষ ব্যবহার, উপযুক্ত সেচ পদ্ধতি ব্যবহার, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ, পাম্পিং নিয়ন্ত্রণ, মাটি ও লবণাক্ততার মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা।
-মৃত্তিকা পরীক্ষা করে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা এবং কীটনাশক এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
-বৃষ্টির পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা, ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে সবুজ কৃষির অনুশীলন করা।
-শস্য আবর্তন অনুসরণ করা এবং ফসলের অবশিষ্টাংশ মাটিতে মিশতে দেওয়া।
-মাটিকে যতদূর সম্ভব কম কর্ষণ করা বা শূন্য কর্ষণ অনুশীলন করা।
- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাহাড়ে চাষাবাদ, আচ্ছাদনযুক্ত ও বহুবর্ষজীবী ফসল চাষ করা।
টেকসই বন ব্যবস্থাপনা
টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও টেকসই কৃষির পাশাপাশি টেকসই বনায়ন সংরক্ষণ অপরিহার্য। গাছের সুরক্ষা না থাকলে জমি শুকিয়ে যায় এবং ক্ষয় হতে থাকে। অতএব, দূষণের হাত থেকে মাটিকে বাঁচাতে টেকসই বনায়ন বা গাছ কাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
পরিষ্কার করা
পরিবেশগত প্রতিকারের মধ্যে রয়েছে মাটি, ভূগর্ভস্থ পানি বা ভূপৃষ্ঠের পানি থেকে দূষণ অপসারণ। বায়োরিমিডিয়েশন (অণুজীব) এবং ফাইটোরিমিডিয়েশন (উদ্ভিদ) দূষণকারীকে বিশুদ্ধ পণ্যে রূপান্তর করতে ব্যবহার করা।
সঠিক বর্জ্য নিষ্পত্তি
শিল্প-কলকারখানা বা গৃহস্থালির বর্জ্য দক্ষ বর্জ্য নিষ্পত্তি ভূমি দূষণ রোধের অন্যতম কার্যকর উপায়। এটি বিশেষ করে বিষাক্ত ও বিপজ্জনক বর্জ্য নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, বিপজ্জনক উপাদান দ্বারা জমি ভরাট করা মাটি দূষণের কারণ হতে পারে। এই আবর্জনা দ্বারা ভূগর্ভস্থ জলও দূষিত হতে পারে।
“৩ জং” (জবফঁপব,জবঁংব,জবপুপষব) নিয়ম ও শিক্ষা
নন-বায়োডিগ্রেডেবল পণ্যের ব্যবহার কমানোর(জবফঁপব) ফলে প্লাস্টিক দূষণ কমবে এবং ভূমি দূষণের উপর প্রভাব ফেলবে। এই জন্য প্রতিটি সম্ভাব্য পণ্য পুনঃব্যবহার (জবঁংব) এবং পুনর্ব্যবহার (জবপুপষব) করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমি দূষণ থেকে পরিবেশ রক্ষার প্রচেষ্টায় শিক্ষাকেও প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।
পরিশেষে বলতে চাই, নীতিনির্ধারক, খাদ্য উৎপাদনকারী, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিজ্ঞানী, এনজিও, সুশীলসমাজ, ভূমি ব্যবহারকারী এবং আদিবাসীদের পাশাপাশি স্থানীয় সম্প্রদায়, শিল্প এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিসহ সকল স্তরের বিস্তৃত অংশগ্রহণই পারে এ অমূল্য সম্পদগুলোকে সংরক্ষণ করতে। এছাড়া শুধু দিবস পালন নয়, আগামীর দক্ষ মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হলে, যাদের নিবিড় স্পর্শে মৃত্তিকাকে করে তোলে আরো উর্বর, আরো সুফলা, অভিজ্ঞ মৃত্তিকা ব্যবস্থাপক বাংলার সেই মহান কৃষককে ফসলের মাঠে রাখতেই হবে।
লেখক : প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক গবেষণাগার, গোপালগঞ্জ, মোবাইল: ০১৯১১৬২১৪১৫, ইমেইল: যধংরহধংৎফর@মসধরষ.পড়স
 মাটির পুষ্টি উপাদান ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাটের গুরুত্ব
মাটির পুষ্টি উপাদান ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাটের গুরুত্ব
মাটির পুষ্টি উপাদান ও পরিবেশের
ভারসাম্য রক্ষায় পাটের গুরুত্ব
ড. মো. আবদুল আউয়াল১ ড. মো. আবু সায়েম জিকু২
পাট পরিবেশবান্ধব, বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক আঁশ, যা গোল্ডেন ফাইবার নামে পরিচিত এবং এটি আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে জড়িত। বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ৫% পাট থেকে আসে এবং দেশের জিডিপিতে এর অবদান প্রায় শতকরা ৪ ভাগ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পাটজাত পণ্যকে ২০২৩ সালের বর্ষপণ্য এবং ১লা মার্চ ২০২৩ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর তথ্য মতে, বর্তমানে পাট উৎপাদন ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে ১ম স্থান দখল করে আছে।
পাট একটি ফটোপিরিয়ড সংবেদনশীল এবং স্বল্প দিনের উদ্ভিদ। দিনের দৈর্ঘ্য ১২.৫ ঘণ্টা বা তার নিচে হলেই আগাম ফুল আসতে পারে, আবার ১২.৫ ঘণ্টা বা তার বেশি হলে ফুল আসা বিলম্বিত হতে পারে। তাই নির্ধারিত সময়ের আগে বীজ বপন করলে পাট ফসলে আগাম ফুল আসে, তখন গাছের মাথা ফেটে যায়, অবাঞ্ছিত শাখা-প্রশাখা জন্মায়, গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, আঁশের গুণগতমান খারাপ হয় এবং ফলনও কম হয়। আবার দেরিতে বপন করলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না, কাজেই ভালো ফলন এবং তিন অথবা চার ফসলি শস্যপর্যায়ে পাটকে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে যথাসময়ে বীজ বপন করা অপরিহার্য। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) দেশের কৃষি পরিবেশ ও কৃষকদের চাহিদা বিবেচনায় নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে এবং পাট ফসলের উপর বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ৫৬টি পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতার সংক্ষিপ্ত আকারে পাটের কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যা ও মাটির পুষ্টি উপাদান ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এর গুরুত্ব তুলে ধরা হলো।
পাটের কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যা
বাংলাদেশে পাট ফসল আবাদ করার জন্য বপনের সময়, জমি নির্বাচন, জলবায়ু, সঠিক আন্তঃপরিচর্যা এবং সমন্বিত মাটি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। তা না হলে পাট ফসলের কাক্সিক্ষত ফলন সম্ভব নয়।
বপনের সময়
বীজ ফসলের ফুল ধরার জন্য দিনের দৈর্ঘ্য কম দরকার হয় বলে, আগস্ট-সেপ্টেম্বর (ভাদ্র-আশি^ন) মাসে বীজ বপন করা হয় যাতে ফুল আসার আগেই গাছটি যথেষ্ট অঙ্গজ বৃদ্ধি হতে পারে। বপনের ৩-৪ মাস পরে ডিসেম্বর-জানুয়ারি (অগ্রহায়ণ-পৌষ) মাসে বীজ সংগ্রহ করা হয়। যদিও এ সময় পাট গাছের দৈর্ঘ্য লম্বায় ২-৪ ফুট কম হলেও অধিকসংখ্যক ডালপালাসহ সুপুষ্ট ফল ধারণ করে, যা থেকে অধিক পরিমাণ ও গুণগত মানসম্পন্ন উন্নত মানের বীজ পাওয়া যায়। অন্যদিকে, আঁশ হিসেবে পাট চাষ করার জন্য মার্চ-এপ্রিল মাস (মধ্য চৈত্র হতে মধ্য বৈশাখ) পাট বীজ বপন করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, তবে তোষা পাটের ক্ষেত্রে মধ্য মে পর্যন্ত বপন করা যায়।
বীজের পরিমাণ ও বপন পদ্ধতি
ছিটিয়ে বপন পদ্ধতির ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ৭.৫ কেজি (প্রতি শতাংশে ৩০ গ্রাম) এবং সারিতে বপন পদ্ধতির ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ৬.২৫ কেজি (প্রতি শতাংশে ২৫ গ্রাম) পরিমাণ বীজ প্রয়োজন হয়। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি. (প্রায় ১ ফুট) এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭ সেমি. (প্রায় ৩ ইঞ্চি) রাখা ভালো।
জমি নির্বাচন
জমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত তোষা পাটের জন্য দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি সমৃদ্ধ উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করা ভালো, যেখানে বৃষ্টি বা বন্যার পানি না জমে অর্থ্যাৎ দ্রুত পানি নিষ্কাশিত হয়। দেশী পাট মাঝারি উঁচু থেকে নিচু জমি এবং কেনাফ/মেস্তা উঁচু নিচু অথবা অসমতল এমনকি পতিত জমিতেও চাষ করা যায়।
পাট বীজের সঠিক অঙ্কুরোদগমের জন্য সুষম চাষের প্রয়োজন কারণ পাটের বীজ আকারে খুবই ছোট। চাষের সংখ্যা সাধারণত মাটির ধরনের উপর নির্ভর করে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, মাটির ধরন/টেক্সচার অনুযায়ী ৩-৬ চাষ দেওয়া যেতে পারে। চাষের সময় আগাছা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে, তা না হলে জমিতে আগাছার পরিমাণ বেশি হবে এবং নিড়ানি খরচ বৃদ্ধি পাবে যার ফলশ্রুতিতে, ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটবে, রোগ ও পোকামাকড় এর আক্রমণ বৃদ্ধি পাবে এবং ফলন কম হবে। চাষের পরে ক্ষেতের মাটি যথাযথভাবে সমতল/সমান করতে হবে।
তাপমাত্রা ও জলবায়ু
পাটের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর তাপমাত্রা প্রয়োজন। ভালো বৃদ্ধি ও উচ্চমাত্রার ফলনের জন্য ২৫০ মিমি থেকে ২৭০ মিমি বৃষ্টিপাত দরকার হয়। এ ছাড়াও সঠিক বীজের হার সর্বাধিক ফলনের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
সার প্রয়োগ
পাট বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জমিতে শেষ চাষের সময়, নির্দিষ্ট ডোজের ইউরিয়া (১৫০ গ্রাম/শতাংশ), টিএসপি (২০০ গ্রাম/শতাংশ) ও এমওপি (১২০ গ্রাম/শতাংশ) প্রযোগ করতে হবে। মাটি পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় জমিতে জিপসাম, জিংক ও বোরিক এসিড এর অভাব রয়েছে তাহলে প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম জিপসাম, ৫০ গ্রাম জিংক ও ৫০ গ্রাম বোরিক এসিড প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তির সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, দুই-এক দিন পূর্বেই নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং ৩য় বা শেষ কিস্তির সার প্রয়োগের পূর্বে একইভাবে আগাছা পরিষ্কার করে উপরিপ্রয়োগ হিসাবে শুধুমাত্র প্রতি শতাংশে ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া সারপ্রয়োগ করতে হবে যেন বীজ উৎপাদনের ফলনে কোন ঘাটতি না হয়। তবে উপরিপ্রয়োগের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, সাধারণত শুকনো ঝুরঝুরে মাটি বা ছাইয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে উপরিপ্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।
আঁশ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইউরিয়া (৮১০ গ্রাম/শতাংশ), টিএসপি (২০০ গ্রাম/শতাংশ), এমওপি (৩৬০ গ্রাম/শতাংশ), সালফার (১৮০ গ্রাম/শতাংশ) ও জিংক সালফেট (মনো) (৩৬০ গ্রাম/শতাংশ) প্রযোগ করতে হবে। শুধুমাত্র ইউরিয়া সার ৩টি সমান কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং বাদবাকি সার শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। জাত ও অঞ্চলভেদে সারের মাত্রার ভিন্নতা হতে পারে।
আন্তঃপরিচর্যা
পাট উৎপাদনের জন্য আন্তঃপরিচর্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই নজর দিতে হবে আগাছা দমনের ক্ষেত্রে। সাধারণত বপনের ২০-২৫ দিন পর প্রথম, ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয় ও ৬০-৬৫ দিন পর ৩য় নিড়ানি দিতে হবে। তবে উল্লেখ্য যে, শস্য-আছাগা প্রতিযোগিতার প্রথম ৪০ দিন আগাছামুক্ত রাখতে হবে। নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে যেন আলো-বাতাস চলাচলে বিঘœ না ঘটে। যার ফলে মাটিতে দীর্ঘদিন রস জমা থাকবে এবং ফসল কাটা পর্যন্ত রসের সাধারণত অভাব হবে না এবং গাছের বৃদ্ধিও অবহ্যাত থাকবে। অন্য কোন গাছের মিশ্রণ এড়াতে ফসলের উৎপাদনের সময় অবাঞ্ছিত গাছ তুলে ফেলা অথবা অন্য জাতের বা আগাছার গাছ বা সন্দেহ যুক্ত যেকোন গাছসহ অতিরিক্ত গাছ বীজ ফসলের জমি হতে তুলে ফেলতে হবে। মানসম্মত পাট আঁশ ও বীজ উৎপাদন করার ক্ষেত্রে পোকামাকড় দমন করাও খুবই জরুরি।
অধিক ফলন ও গুণগত মানসম্পন্ন আঁশ পাওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ে বপনকৃত পাট গাছ ১০০-১২০ দিনে কাটা ভালো। পাট গাছ কাটার পর ১০-১২টি পাট গাছ একত্রে করে আটি বেঁধে ৩-৪ দিন জমিতে খাঁড়া করে রেখে দিয়ে জাগ দিলে, আঁশের রং উজ্জ্বল হয় পাশাপাশি আঁশ ছড়ানোও সহজতর হয়।
মাটির পুষ্টি উপাদান ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাটের গুরুত্ব
মাটি হচ্ছে কৃষির অন্যতম উপাদান। উপযুক্ত মাটি (প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ মাটি) না হলে, কাক্সিক্ষত ফলন আশা করা যায় না। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় পাট ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। পাট ফসল পরিবেশবান্ধব হওয়ার কারণে পাট আবাদকৃত জমির মাটি তুলনামূলকভাবে অন্য ফসল আবাদকৃত জমির মাটি অপেক্ষা অধিক পুষ্টি ও গুণগতমান সম্পন্ন হয়।
পাট গাছের পাতায় প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও সোডিয়াম থাকে। জমিতে পাটের পাতা ও গোড়া পচে জমির উর্বরতা বাড়ায়। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, পাট উৎপাদন কালে হেক্টরপ্রতি ৫ থেকে ৬ টন পাট পাতা মাটিতে পড়ে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ পাট হয়, তা হতে বছরে গড়ে ৯৫৬.৩৮ হাজার টন পাতা এবং ৪২৩.৪ হাজার টন মূল মাটিতে যুক্ত হয়, যা পচে মাটির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, ডলোমাইট, ফেরাস সালফেট প্রদানের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এতে পরবর্তী ফসল উৎপাদনের সময় সারের খরচ কম লাগে। যে জমিতে পাট চাষ হয়, সেখানে অন্যান্য ফসলের ফলনও ভালো হয়। পাটগাছের মূল মাটির ১০-১২ ইঞ্চি বা তারও অধিক গভীরে প্রবেশ করে যা মাটির উপরিস্তরের প্লাওপ্যান ভেঙে দেয় এবং মাটি হতে পুষ্টি উপাদান গ্রহণে সহজলভ্য করে তোলে। এ ছাড়াও পাটজাত পণ্য শতভাগ পচনশীল হওয়ায়, এটি পলিথিনের মতো মাটির ছোট ছোট ছিদ্রগুলোকে বন্ধ করে না। ফলে মাটিতে অক্সিজেন সরবরাহ ভালো থাকে এবং মাটির বিভিন্ন উপকারী অণুজীবের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। গবেষণার তথ্য মতে, ১০০ দিন সময়ের মধ্যে এক হেক্টর পাট ফসল বাতাস থেকে প্রায় ১৪.৬৬ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং ১০.৬৬ টন অক্সিজেন ত্যাগ করে বায়ুম-লকে পরিশোধিত করে। ফলে পাট ফসল পৃথিবীর গ্রিন হাউজ গ্যাস ও তার পরিপ্রেক্ষিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে কিছুটা হলেও ব্যাহত করে। এ ছাড়াও পাট পচানোর সময় যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাতে ৫০% থেকে ৬০% মিথেন থাকে, যা থেকে বসতবাড়িতে বা শিল্প কারখানায় ব্যবহার উপযোগী জ্বালানি গ্যাস তৈরি করা যেতে পারে।
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাটের শিল্প গবেষণার মাধ্যমে জুট-জিও-টেক্সটাইল উদ্ভাবন করেছে। এ সস্তা এবং পরিবেশবান্ধব পণ্যটির মাধ্যমে ভূমির ক্ষয়রোধ করাসহ রাস্তার উপরিভাগে রাস্তার মাটি ধস ঠেকাতে, নদীর বাঁধ/তীর, পাহাড়ের ঢাল, সেচ নালার ভাঙন প্রতিরোধসহ বিভিন্ন প্রকার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দির জঙ্গল বাড়ির গড়াই নদীতে ৪০০ মিটার, গোলালগঞ্জ এর আঁড়িয়াল খাঁ নদীর পাড়ে ২০০ মিটার ও ঢাকার হাতিরঝিল প্রকল্পসহ বিভিন্ন স্থানে জুট-জিও-টেক্সটাইল ব্যবহার করা হয়েছে। পাট পরিবেশবান্ধব যে কারণে বিশ^ব্যাপী পাটের ব্যবহারও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্ব
পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসল হতে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ছাড়াও বর্তমানে পাটপাতা থেকে তৈরি হচ্ছে অর্গানিক চা। এটি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এর মাধ্যমে দেশীয় যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাটের আরেকটি সম্ভাবনাময় দিক হলো মেস্তাপাট। পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে মেস্তা পাট থেকে তৈরি হচ্ছে আইসক্রিম, চা, জ্যাম, জেলি, জুস, আচার ও পানীয়সহ হরেকরকম খাদ্যপণ্য। ধারণা করা হচ্ছে, এসব খাদ্যপণ্য বাজারজাত করা গেলে দেশের অর্থনীতিতে যোগ হবে হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশে প্রতি বছর পাটকাঠির গড় উৎপাদন ২৪৮০.৬২ হাজার টন। কাঠের জায়গায় পাট দিয়ে কাগজের পাল্প তৈরি করলে কাগজের উৎপাদন খরচ কমবে। পাটের কাঠি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হলে কাঠের ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে, যা বনভূমি উজাড় কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।
বর্তমান সরকারের নানা পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও সোনার বাংলা গড়ার যে প্রত্যয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছানোর যে লক্ষ্য, সেটি অর্জনে আমাদের অন্যতম চালিকাশক্তি হবে পাট ও পাটজাতীয় পণ্য। পরিশেষে, আসুন আমরা সকলে মিলে পাটজাত পণ্য ব্যবহার করি এবং মাটি ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করি।
লেখক : মহাপরিচালক১ ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা২ মৃত্তিকা বিজ্ঞান শাখা, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫। মোবাইল : ০১৭১৭৫৬২৬৭৩, ই-মেইল : লরশঁষু@মসধরষ.পড়স
 উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে ধানের আবাদ ও ফলন বৃদ্ধিতে করণীয়
উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে ধানের আবাদ ও ফলন বৃদ্ধিতে করণীয়
 ভোজ্যতেলের নানাবিধ ব্যবহারে তিল তেল এবং তিল ফসলের সম্ভাবনা
ভোজ্যতেলের নানাবিধ ব্যবহারে তিল তেল এবং তিল ফসলের সম্ভাবনা
ভোজ্যতেলের নানাবিধ ব্যবহারে তিল তেল
এবং তিল ফসলের সম্ভাবনা
ড. আব্দুল মালেক
তিল তেল উচ্চপুষ্টিসমৃদ্ধ ভোজ্যতেল। তিলতেলে বেশ কিছু ভিটামিন যেমন- ভিটামিন-ই, বি কমপ্লেক্স ও ডি এবং খনিজ উপাদান কপার, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে। ফলে এ তেলে রান্না করা খাবার খেলে হাড়ের ক্ষয়রোধের পাশাপাশি অস্টিওপোরোসিস রোধসহ হাড়ের জোড়ায় ব্যথাজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণেও কাজ করে। কাজেই প্রতিদিনের রান্নায় তিল তেলকে সয়াবিনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গবেষণার তথ্য মতে, তিলতেল রক্তচাপের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। তিলতেলে থাকা ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন-ই এবং এন্টিঅক্সিডেন্টসমূহ রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে হৃদযন্ত্রকে ভাল রাখতে সহায়তা করে। তিলবীজে ৪২-৪৫% তেল এবং ২০-২৮% আমিষ থাকে। তিলতেলে মানব শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ৮০-৮২% এর বেশি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড আছে যা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমকে শক্তিশালী রাখতে এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে রাখতে ভূমিকা রাখে। তাছাড়া তিল তেলে ‘টাইরোসিন’ নামের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। যা মানসিক অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তা দূর করতে সাহায্য করে। তিল তেল প্রয়োজনীয় এনজাইম ও হরমোন সরবরাহ করার মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে মন-মেজাজও ভালো রাখে।
নানাবিধ পুষ্টিগত গুণাগুণের কারণে আদিকাল থেকেই ভোজ্যতেল হিসেবে তিল তেল ব্যবহার হয়ে আসছে। রান্নার কাজে ব্যবহার ছাড়াও শরীর ও মাথায় ব্যবহারেও তিল তেলের আলাদা কদর রয়েছে। তিল তেল চুল পড়া কমায়, চুল পাকা রোধ করে, প্রাকৃতিক সানস্ক্রিন হিসেবে কাজ করে এবং ত্বকের স্থিতিস্থাপকতাও বাড়ায়। তিল তেলে এন্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান থাকায় এটি স্কিনের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া তিল তেল একটি অসাধারণ ময়েশ্চারাইজার এবং এতে ডিটক্সিফাইং উপাদান থাকায় শুষ্ক ও মৃত কোষ দূর করার মাধ্যমে ত্বককে নরম ও কোমল রাখে এবং এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে বলে অ্যান্টি-এজিং হিসেবে কাজ করে ও ত্বকের কুচকিয়ে যাওয়া প্রতিহত করতে সাহায্য করে।
ভোজ্যতেলের প্রয়োজনীয়তা : মানবদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ফ্যাট বা চর্বি অর্থাৎ তেল। এই ফ্যাট দেহের তাপশক্তি উৎপাদন, মস্তিষ্কের বিকাশ, বিভিন্ন হরমোনের উৎপাদন, চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (এ. ডি. ই. কে) শোষণ এবং ত্বক ও অন্যান্য অঙ্গের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। মূলত ফ্যাট দেহের সঠিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, মনোআনস্যাচুরেটেড ও পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটগুলো মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটগুলো দেহের কোষের বিকাশ, কোলেস্টেরলের মাত্রা স্থিতিশীল রাখা এবং হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অ্যাভোকাডো, বাদাম ও বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জ তেল (ক্যানোলা/সরিষা, জলপাই, চীনাবাদাম, তিল তেল) মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটের ভালো উৎস। অন্য দিকে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট প্রধানত উদ্ভিজ্জ তেল (সূর্যমুখী, তিল, সয়াবিন, কর্নওয়েল) ও সামুদ্রিক মাছে পাওয়া যায়। এ ফ্যাট খাওয়ার ফলে এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস পায়। অপর দিকে খারাপ ফ্যাট বা ট্রান্সফ্যাট জাতীয় খাদ্য শরীরের জন্য ক্ষতিকর, খারাপ কোলেস্টেরল এলডিএলের পরিমাণ বাড়ায় এবং ভাল কোলেস্টেরল কমিয়ে দেয়। চর্বিযুক্ত মাংস, ক্রিম, বাটার, চিজ, পাম অয়েল, নারকেল তেল, ফ্রাই করা খাদ্যে এ ফ্যাট বেশি পাওয়া যায়। তাই ফ্যাটজাতীয় খাবারকে একেবারে বাদ না দিয়ে, ভাল ফ্যাট গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ এবং খারাপ ফ্যাট বর্জনের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ভাল তেল রক্তের এইচডিএল অর্থাৎ শরীরের জন্য উপকারী ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি করে। মানবদেহে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বা খারাপ কোলেস্টেরল এলডিএল বেশি থাকলে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে উদ্ভিজ্জ তেল। উদ্ভিজ্জ তেল হৃদরোগ ও রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমিয়ে দেয় আর লিভারকে সচল রাখে। তাই পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটযুক্ত উদ্ভিজ্জ তেল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশ নিরাপদ হিসেবে বিবেচিত।
বাংলাদেশে ভোজ্যতেল আমদানি ও উৎপাদন পরিস্থিতি : দেশে সরিষা, তিল এবং সূর্যমুখী হতে প্রাপ্ত ভোজ্যতেল উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৩ লাখ মে. টনের মতো, কিন্তু আমাদের দেশীয় চাহিদা মোট ২৪ লাখ মে. টন। অর্থাৎ চাহিদার সিংহভাগই এখনো আমদানি নির্ভর। বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) হিসেবে, সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থবছরে আমাদের দেশে ১৩ লাখ ৫৫ হাজার টন পাম তেল এবং ৭ লাখ ৮০ হাজার টন সয়াবিন তেল আমদানি করা হয়েছে এবং এতে ব্যয় হয়েছে বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা। এমতাবস্থায় ভোজ্যতেলের উৎপাদনের মাধ্যমে দেশীয় চাহিদা মেটাতে সরিষার পাশাপাশি তিলের আবাদ এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি করতে হবে।
দানাদার ফসল, ফল ও সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করতে পারলেও ভোজ্যতেল উৎপাদনের পরিমাণ বিগত বছরগুলোতে ছিল চাহিদার তুলনায় মাত্র ১২ শতাংশ, যা সাম্প্রতিককালে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এখনই সময় তিলসহ অন্যান্য ভোজ্যতেলের উৎপাদনে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করার।
দেশে তিল উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা : বাংলাদেশে তেলবীজ ফসলের মধ্যে তিলের অবস্থান চতুর্থ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২১-২০২২) অনুসারে দেশে গড়ে প্রায় ৩৩ হাজার হেক্টর জমিতে তিল চাষ হয় এবং মোট উৎপাদন প্রায় ৩১ হাজার মেট্রিক টন। খরিফ-১ এবং রবি উভয় মৌসুমেই তিলের চাষ হলেও বর্তমানে দুই-তৃতীয়াংশ তিলের আবাদ হয় খরিফ-১ মৌসুমে। খরিফ-১ মৌসুমের জন্য পাবনা, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, রাজশাহী, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, রাঙ্গামাটি এবং এই জেলাগুলোর নিকটবর্তী অঞ্চল তিল চাষের জন্য অধিক উপযোগী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২১-’২২) অনুযায়ী ২০১৯-’২০ থেকে ২০২১-’২২ পর্যন্ত তিলের জাতীয় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৯৪৪ কেজি, যা ২০০১-২০১৭ পর্যন্ত ছিল মাত্র ৮৪০ কেজি। স্বাভাবিক ফলনের তুলনায় তিলের জাতীয় গড় ফলন কম হওয়ার মূল কারণগুলো হলো অনাকাক্সিক্ষত ঝড় এবং ফুল আসা পর্যায়ে শুরুতে/শেষে অথবা ফলধারণ পর্যায়ে অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন, উপযুক্ত পরিচর্যা এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ না হওয়া। আবহাওয়ার গতিবিধি বিবেচনায় সঠিক সময়ে সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, উন্নত জাতের ব্যবহার, উপযুক্ত পরিচর্যাসহ আধুনিক চাষাবাদ কৌশল অবলম্বনে তিলের ফলন হেক্টরপ্রতি ১২০০-১৫০০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব।
বাংলাদেশে ভোজ্যতেল উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
বাংলাদেশে ভোজ্যতেল উৎপাদন বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনাসমূহকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন সমম্বিত উদ্যোগ। বিভিন্ন উচ্চফলনশীল জাত ব্যবহার করে তেলজাতীয় ফসলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা অনেকাংশেই সম্ভব। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা যেমন- সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও চট্টগ্রামে; চর এলাকা যেমন- নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, ফরিদপুর, ভোলা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জে বাদাম, তিল, সূর্যমুখী ও সরিষা এবং পার্বত্য এলাকা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে সরিষা ও তিল চাষের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে উচ্চফলনশীল তিলের জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে তিলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার যথেষ্ঠ সুযোগ আছে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার আন্তরিক ইচ্ছায় সময়োপযোগী কৃষিবান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে কৃষিতে এক দুর্বার গতি সঞ্চারিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী দুই বছরে (জুন ২০২৫ পর্যন্ত) দেশের ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমপক্ষে ৪০% কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।
লেখক : পরিচালক (গবেষণা) বিনা। বাংলাদেশ কৃষি বিশ^বিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ময়মনসিংহ-২২০২, মোবাইল : ০১৭১২১০৬৬২০, ই-মেইল : সধষবশনরহধ@মসধরষ.পড়স
 চরাঞ্চলে-মিষ্টিকুমড়ার-আবাদ
চরাঞ্চলে-মিষ্টিকুমড়ার-আবাদ
চরাঞ্চলে মিষ্টিকুমড়ার আবাদ
ড. বাহাউদ্দিন আহমেদ
মিষ্টিকুমড়া সকলের প্রিয় একটি সবজি। এটিকে গরিবের পুষ্টি বলা হয়। বাংলাদেশে প্রায় সকল বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ২/১ টি মিষ্টিকুমড়ার গাছ দেখা যায়। তাছাড়া বাণিজ্যিক ভাবেও এর ব্যাপক চাষ হচ্ছে। কচি মিষ্টিকুমড়া সব্জি হিসেবে এবং পাকা ফল দীর্ঘদিন রেখে সব্জি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পরিপক্ব ফল শুষ্ক ঘরে সাধারণ তাপমাত্রায় প্রায় ৪-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়। পরিপক্ব ফলের বিটা-ক্যারোটিন রাতকানা রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। মিষ্টিকুমড়া ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। পরিপক্ব ফলের প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে প্রোটিন ১.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০০ মিগ্রা:, ফসফরাস ৩০.০ মিগ্রা:, বিটা ক্যারোটিন ৫০ মাইক্রো গ্রাম এবং ভিটামিন-সি ২.০ গ্রাম। এর কচি ডগা, পাতা এবং ফুল সব্জি হিসেবে খুবই মুখোরোচক।
বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং অপরদিকে নদীতে চর জেগে উঠছে। চরের লোকেদের দরিদ্রতার অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে নদী ভাঙন, মাটির অনুর্বরতা এবং স্থানীয় জাতের ব্যবহার অন্যতম। অধিকাংশ চরের জমিগুলো রবি মৌসুমে চাষের উপযোগী থাকে, কারণ এই সময় নদীর পানি নিচে নেমে যায় এবং চরগুলো জেগে উঠে। কিছু কিছু চর এলাকা বড় দ্বীপের মতো হয়। এগুলো কখনো ডুবে যায় না। লোকজন সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। সেই সমস্ত চরগুলোতে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির চাষাবাদ হয়, তার মধ্যে মিষ্টিকুমড়া অন্যতম। চরাঞ্চলের পলি মাটিতে মিষ্টিকুমড়ার ফলন খুব ভালো হয়। একটি গবেষণায় দেখা যায় যে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ১০টি জেলায় প্রায় ১,২০,০০০ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের সবজি আবাদের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অপুষ্টি দূর করতে সক্ষম হয়েছে।
জাত পরিচিতি : বর্তমানে বাজারে যে সব কোম্পানির বীজ বিক্রি হয় তাদের মধ্যে লালতীর কোম্পানির বীজ তুলনামূলকভাবে ভালো। তাছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) হতে এ পর্যন্ত ৫টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে ৩টি হাইব্রিড ও ২টি মুক্তপরাগায়িত জাত রয়েছে। জাতগুলো হলোঃ-
(ক) বারি মিষ্টিকুমড়া-১ (মাঝারি আকারের)
খ) বারি মিষ্টিকুমড়া - ২ (ছোট আকারের)
গ) বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-১ (মাঝারি আকারের)
ঘ) বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-২ (মাঝারি আকারের)
ঙ) বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-৩ (মাঝারি আকারের)
উক্ত মিষ্টিকুমড়ার জাতগুলোর মধ্যে বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া -রংপুর, বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলার দুর্গম চরে ব্যাপকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা হতে উদ্ভাবিত জাতগুলোর ফলের আকার, আকৃতি, শাঁস এর রং, শাঁসের মিষ্টতা, গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ইত্যাদির দিক থেকে অন্য যে কোন জাতের চেয়ে উৎকৃষ্ট। উক্ত জাতগুলো নিশ্চিতভাবে চরাঞ্চলে কৃষকের কাছে অধিক জনপ্রিয়তা পাবে। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত চরাঞ্চলগুলো বারি উদ্ভাবিত সবজি জাতগুলো প্রসারে ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
চাষাবাদ পদ্ধতি : চরাঞ্চলে সবজি চাষাবাদ প্রক্রিয়া অন্য যে কোন স্থানে চাষাবাদ পদ্ধতি হতে ভিন্ন, যেহেতু চরাঞ্চলের কৃষি পরিবেশিক অবস্থা অন্য যে কোন স্থান এর তুলনায় ভিন্ন। চরাঞ্চলে মিষ্টিকুমড়া চাষাবাদের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের চাষাবাদ কৌশলে অবলম্বন করতে হয় যাকে ‘সানবার’ (ঝঁহনধৎ) পদ্ধতি বলে। সানবার হলো নদীর পলি ও বালু দ্বারা প্লাবিত বড় অস্থায়ী ও উন্মুক্ত একটি স্থান যা বন্যার পর পরেই পানি নেমে যেয়ে তৈরি হয়। সাধারণত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে যখন নদীর পানি আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে তখন ‘সানবার’ দৃশ্যমান হতে থাকে এবং ‘সানবার’ পদ্ধতিতে মিষ্টিকুমড়ার আবাদ শুরু করা যায়। ‘সানবার’ চাষাবাদ পদ্ধতি হলো অনেকটা মাদাতে সবজি চাষের মতোই। এক্ষেত্রে ৭-৮ ফুট দূরে দূরে সারি করে ৩ ফুট গভীর ও ৩ ফুট চওড়া করে গর্ত তৈরি করতে হয়। এর পর উক্ত গর্তে ৫-৬ কেজি পচা গোবর/অন্য যে কোন জৈবসার, টিএসপি ৭০ গ্রাম, এমপি ৩০ গ্রাম, জিপসাম ৪০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৪ গ্রাম, বোরিক এসিড ৪ গ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ৫ গ্রাম, পিটের মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হয়। মিষ্টিকুমড়া দীঘদিন বেচে থাকে এবং অনেক লম্বা সময়ব্যাপী ফল দিয়ে থাকে কাজেই এসব ফসলের সফল চাষ করতে হলে গাছের জন্য পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয় । এরপর উক্ত পিটে ৪-৫টি বীজ বপন করতে হয় অথবা পলি ব্যাগে চারা করেও পিটে লাগানো যায় এবং প্রয়োজনীয় পানি দিতে হবে। চারা গজানোর পর ২টি চারা রেখে বাকি চারাগুলো তুলে ফেলে দিতে হবে। মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য পিটকে খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং সপ্তাহে ২-৩ বার পানি দিতে হবে। চারা গাছের বয়স যখন ২৫ দিন হবে তখন প্রতি পিটে ৩৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। এই ভাবে ৩৫ গ্রাম ইউরিয়া ৪০ দিন, ৬০ দিন ও ৭৫ দিন বয়সে পিটে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবারেই সার দেওয়ার পরপর পিট পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। মিষ্টিকুমড়া পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। বিশেষ করে ফল ধরার সময় প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে, ফল শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ পর্যন্ত ঝরে যেতে পারে। শুষ্ক মৌসুমে প্রতি ৫-৭ দিন পরপর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। মিষ্টিকুমড়া গাছকে মাটিতে বাইতে দিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কচি ফল প্রথম থেকেই খড় বা শুকনো কচুরিপানার উপর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, এতে করে প্রচ- গরমে বালি উত্তপ্ত হয়ে গেলেও ফল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
বিশেষ পরিচর্যা
শোষক শাখা অপসারণ : গাছের গোড়ার দিকে ছোট ছোট শাখা হয়। সেগুলোকে শোষক শাখা বলা হয়। এগুলো গাছের ফলনে এবং যথাযথ শারীরিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যস্ত শাখাগুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।
ফল ধারণ বৃদ্ধিতে কৃত্রিম পরাগায়ন : মিষ্টিকুমড়ার পরাগায়ন প্রাকৃতিকভাবে প্রধাণত মৌমাছির দ্বারা স¤পন্ন হয়। বর্তমানে প্রকৃতিতে মৌমাছির পরিমাণ পর্যাপ্ত নহে। কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে মিষ্টিকুমড়ার ফলন শতকরা ২৫-৩০ ভাগ বাড়ানো যায়। মিষ্টিকুমড়ার ফুল খুব সকালে ফোটে। ফুল ফোটার পর যত তাড়াতাড়ি পরাগায়ন করা যায় ততই ভালো ফল পাওয়া যাবে। মিষ্টিকুমড়ায় কৃত্রিম পরাগায়ন সকাল ৯ ঘটিকার মধ্যে স¤পন্ন করতে হবে। কৃত্রিম পরাগায়নের নিয়ম হলো ফুল ফোটার পর পুরুষ ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ফুলের পাপড়ি অপসারণ করা হয় এবং ফুলের পরাগধানী (যার মধ্যে পরাগরেণু থাকে) আস্তে করে স্ত্রী ফুলের গর্ভমু-ে (যেটি গর্ভাশয়ের পেছনে পাপড়ির মাঝখানে থাকে) ঘষে দেয়া হয়।
ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : ফলের বোঁটা যখন খড়ের রং ধারণ করে তখনই মিষ্টিকুমড়া সংগ্রহ করা উচিত। এর পূর্বে সংগ্রহ করলে মিষ্টিকুমড়ার মান ভালো থাকে না এবং বেশি দিন সংরক্ষণ করে রাখা যায় না। পাকা ফল সংগ্রহের পূর্বে সেচ দেওয়া কমিয়ে ফেলতে হবে। ফল সংগ্রহের ২/৩ সপ্তাহ পূর্বে সেচ দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। এতে ফলের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পাবে।
ফলন : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে উদ্ভাবিত জাতগুলো যথাযথভাবে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ৩০-৫০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে।
পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা : ফলের মাছি পোকা মিষ্টিকুমড়ার জন্য একটি মারাত্মক পোকা। স্ত্রী মাছি কচি ফলে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়াগুলো ফলের শাস খায়, ফল পচে যায় এবং অকালে ঝরে পড়ে এক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ আক্রান্ত ও পচা ফল জমিতে না ফেলে তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদ যৌথভাবে জমিতে ব্যবহার করতে হবে। বর্তমানে বিভিন্ন কীটনাশক এর দোকানে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ সহজেই পাওয়া যায়। বিষটোপের জন্য থেঁতলানো ১০০ গ্রাম পাকা/আদা পাকা মিষ্টিকুমড়ার সাথে সামান্য একটু সেভিন পাউডার মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিষটোপ ৩/৪ দিন পরপর পরিবর্তন করতে হবে । এছাড়াও পামকিন বিটল নামক আরেকটি পোকা মিষ্টিকুমড়ার চারা গাছের খুব ক্ষতি সাধন করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই পোকার কীড়া গাছের গোড়ায় বাস করে এবং শিকড়ের ক্ষতি করে বড় গাছ মেরে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পোকা হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলতে হবে। যদি তাতে কাজ না হয় তবে ২ গ্রাম সেভিন প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে চারা গাছে স্প্রে করতে হবে। কীড়া দমনের জন্য প্রতি গাছের গোড়ায় ২-৫ গ্রাম বাসুডিন/সানফুরান মাটিতে দিয়ে সেচ দিতে হবে। মিষ্টিকুমড়াতে সবচেয়ে যে রোগটি বেশি দেখা যায় তা হলো সাদা গুড়া রোগ বা পাউডারী মিলডিউ। এক্ষেত্রে পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডার বা গুঁড়া দেখা যায়, ধীরে ধীরে এ দাগগুলো বড় ও বাদামি হয়ে পাতা শুকিয়ে যায় এবং ফল ঝরে যেতে পারে। এ রোগ আক্রান্ত পাতা ও গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলে এবং প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম থিওভিট বা সালফোলাক্স/কুমুলাস পাউডার অথবা ১০ গ্রাম ক্যালিক্সিন ১৫ দিন পর পর ২ বার ¯েপ্র করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে । বর্তমানে মিষ্টি কুমড়াতে আরো একটি বড় সমস্যা দেখা যাচ্ছে তা হলো ভাইরাস রোগ। এই রোগে আক্রান্ত পাতা সবুজ ও হলুদের ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায় এবং কচি পাতা আস্তে আস্তে কুঁকড়িয়ে যেতে থাকে। এই ভাইরাস রোগ কোন প্রকার ওষুধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সেক্ষেত্রে একমাত্র পথ হলো ভাইরাস আক্রান্ত গাছ জমিতে দেখা মাত্রই তা জমি থেকে তুলে ফেলে দিতে হবে এবং ভাইরাসমুক্ত গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। তবেই কেবল মাত্র এ রোগ হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।
চরাঞ্চলে কৃষক ভাইয়েরা উপরোক্ত নিয়ম মেনে মিষ্টিকুমাড়া আবাদ করলে আর্ধিকভাবে অনেক লাভবান হতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিক খেয়াল রাখতে হবে তা হলো হাইব্রিড জাতগুলো ব্যবহার করলে কোন অবস্থাতেই তার বীজ পরবর্তী বছর ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা যাবে না। প্রতি বছর নতুনভাবে বীজ সংগ্রহ করে তা লাগাতে হবে, তবেই কেবল ফলন ঠিক থাকবে।
লেখক : ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, মোবাইল : ০১৫৫৬৩৬৩৯০১ ই-মেইল : নধযধঁফফরহধযসবফ৫৭@ুধযড়ড়.পড়স
 স্বপ্ন দেখাচ্ছে কৃষি পর্যটন
স্বপ্ন দেখাচ্ছে কৃষি পর্যটন
স্বপ্ন দেখাচ্ছে কৃষি পর্যটন
কৃষিবিদ মো. বশিরুল ইসলাম
বর্তমান প্রজন্ম বিশেষ করে শহরের অনেক ছেলেমেয়ে ভাত খায় ঠিকই কিন্তু কিভাবে ধান হয় তা হয়তো কখনো দেখেনি। কৃষক কিভাবে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে ফসল ফলাচ্ছে, পুকুরে মাছ ধরছে, কৃষাণীরা কিভাবে ঢেঁকিতে ধান ভাঙছে, উঠান ঝাড়– দিচ্ছে তা হয়তো শুধু টিভিতে দেখলেও বাস্তবে উপলব্ধি করেনি অনেকেই। সকালবেলা ফুল কুড়ানো, মাটির চুলায় রান্না করে খাওয়া এসবই শহুরে মানুষদের কাছে স্বপ্নের মতোই মনে হলেও বাস্তবে এসব দেখা সুযোগ করে দিতে পারে কৃষি পর্যটন। যদিও আমাদের গ্রামগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ছোঁয়া লেগেছে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পরে তিনি তার গ্রামে বসবাস করবেন বলে একাধিক সময় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘যখনই আমি রাজনীতি থেকে অবসর নেবো, আমি আমার গ্রামে চলে যাবো এবং এটিই আমার সিদ্ধান্ত’ (আনছার ভিডিপির ৩৯তম জাতীয় সমাবেশ)। কৃষি পর্যটন হতে পারে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে এক ব্যতিক্রম আইডিয়া, যা বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত শক্ত হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণকে রূপান্তরের মাধ্যমে ভ্রমণপিপাসু বিশ্ববাসীর সামনে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে পর্যটন শিল্পকে আরো লাভজনক শিল্প হিসেবে গড়ে উঠা সম্ভব।
কৃষি পর্যটনের মাধ্যমে পর্যটকরা গ্রামীণ কৃষির ঐতিহ্য, দর্শন, সংরক্ষণ ও উক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনধারা উপলব্ধি করতে পারবে খুব সহজে। এই জাতীয় পর্যটন গ্রামীণ সংস্কৃতির স্থায়িত্বকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারে। ভ্রমণকারীরা আবিষ্কার করবে জীবনের নতুন গল্প। এরই মধ্যে বান্দরবনের লামা, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু ইকোভিত্তিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম বাগান, দিনাজপুরের লিচু বাগান, স্বরূপকাঠির পেয়ারা বাগান, যশোরের ফুলের বাগান, নরসিংদীর লটকন বাগান-এমন আরও অসংখ্য কৃষি পর্যটন। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে ভ্রমণের জন্য এই জায়গাগুলো এরই মধ্যে বেশ পরিচিতি লাভ করে ফেলেছে। যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রগুলো আরো প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করা সম্ভব।
আমরা যারা গ্রামের জন্মগ্রহণ করেছি আমাদের কাছে গ্রাম ও প্রকৃতির প্রতি আলাদা একটা আকর্ষণ আছে। তাছাড়া তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে কৃষির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকনের এখন সব বয়সী মানুষের মধ্যেই বাড়ছে দিন দিন। মানুষ শিকড়মুখী হতে চায়, পুকুরে সাঁতার কাটতে চায়, নিজ হাতে মাছ ধরতে চায়, গাছ থেকে ফল-ফলাদি পেড়ে খেতে চায়। যতই দিন যাবে মানুষ অর্গানিক আর বিষমুক্ত কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়বে। এই কারণে অদূর ভবিষ্যতে মানুষ ওয়েবসাইট বা অ্যাপস ঘেঁটে তার আশপাশের কৃষি ও কৃষ্টির দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করতে চাইবে। আর তরুণ উদ্যোক্তারা এই সুযোগটি লুফে নিতে পারে ব্যবসার জন্য। এতে ক্রেতা ও কৃষক উভয়ই উপকৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ ছাড়া ভোক্তার কাছে সরাসরি পণ্য বিক্রি করতে পারলে কৃষক ন্যায্যমূল্য পাবে।
বরগুনা কৃষি পর্যটন বিকাশে নতুন উদ্যোক্তাদের সাফল্যের মাঠ পর্যায়ের ট্র্যাভেল শো শুরু করেছে। বরগুনা জেলার গ্রামগঞ্জে আনাচে-কানাচে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। বড় বড় কৃষি খামার দেখার মতো একটি গ্রাম। সারাদিনের ভ্রমণের জন্য অনেক জায়গা আছে। ছুটির দিনে শহরের ইট পাথর থেকে মাটির রাস্তা ধরে কোন একটি গ্রামে সারা দিনের জন্য ভ্রমণ করার বরগুনায় অনেক জায়গায়। সেসব জায়গায় যাওয়ার জন্য ‘জল তরণী’ ভ্রমণ সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কোথায় যাবে, কি খাবে, কি দেখবে, কিসে যাবে, সব ধরনের সেবা দিয়ে থাকে জল তরণী।
সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার দত্তরাইল গ্রামে পাহাড়-টিলা ঘিরে গড়ে উঠেছে কৃষি পর্যটন। সারি সারি উচু-নিচু পাহাড়-টিলা। ভাঁজে ভাঁজে আনারস, কমলা, মাল্টা আর লেবু গাছ। আছে কাজুবাদাম আর কফিগাছও। টিকিট কেটে মানুষজন ফলবাগানে ঢুকছে, ঘুরছে, দেখছে। টিলায় বসে অনেকেই কিনে খাচ্ছে টাটকা আনারস আর লেবুর জুস। কেউ কেউ কিনে ব্যাগ ভরে নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতেও। এসব টিলা আগে অনাবাদি ছিল। গত দুই বছরে দৃশ্যপট বদলে যায়। পতিত পাহাড়-টিলা ভরে গেছে আনারসের চারায়। এখন আনারস বিক্রি করেই কোনো কোনো চাষি বছরে কোটি টাকা আয় করছে। এসব ফলবাগানের উদ্যোক্তাদের প্রায় সবাই প্রবাসী।
ঢাকার অদূরেই কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া গ্রামে গ্রিনারি এগ্রোর খামার। ঢুকতেই চোখে পড়বে বিশাল কয়েকটি পুকুর। এসব পুকুরে চাষ হচ্ছে মাছ। মাছের খাবারে কোনো ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার হয় না। পাশেই রয়েছে সবজিক্ষেত। মৌসুমভেদে শাক ও সবজি ফলানো হয় এখানে। আরও উৎপাদন হয় মৌসুমি ধান ও গম। রয়েছে দেশীয় ফলের সমাহার। আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, ডাব- কী নেই এখানে।
গাজীপুরের শ্রীপুর পৌর এলাকার কেওয়া পূর্ব খ- গ্রামের দেলোয়ার হোসেন ও সেলিনা হোসেন দম্পতি ২০২০ সালে প্রথমবার দেশে টিউলিপ ফুল ফুটিয়ে সাড়া জাগিয়েছিল। বিস্তৃত জায়গাজুড়ে শুধু বাহারি রঙিন ফুলের খেলা। এ যেন দেশের বুকে এক টুকরো নেদারল্যান্ডস। নয়নাভিরাম টিউলিপ বাগান দেখতে প্রতিনিয়ত ভিড় করছেন প্রকৃতিপ্রেমীরা। বাগানে টকটকে লাল, গাঢ় হলুদ, হালকা বেগুনি, পিংকসহ ছয় রঙের বাহারি সব টিউলিপ ফুলের সমারোহ। নানা রঙের টিউলিপ দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আকর্ষণীয় এই ফুলের বাগানটি দেখতে এরই মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দপ্তরের বড় কর্মকর্তারা ঘুরে গেছে।
এই আমের মৌসুমে রংপুরের বদরগঞ্জে পরিবার নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলাম। দেখলাম সেখানে বিভিন্ন বয়সের মানুষ আম কিনতে এসেছে। গাছগুলোতে ঝুলছে থোকায় থোকায় পাকা আম। আমের ভারে নুয়ে পড়ছে গাছ ডালপালা। বিমুগ্ধ হয়ে ছবি তুলছে অনেকে! আর আমরা বাগান মালিকের অনুমতি নিয়ে গাছ থেকে পাকা আম পেড়ে খাচ্ছি। সে এক অন্য রকম অনুভূতি।
বাংলাদেশের ভাসমান সবজি চাষ বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী চাষপদ্ধতির স্বীকৃতি পেয়েছে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে। বিশ্ব ঐতিহ্যের এই স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ইউনেস্কো, জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক তহবিল (জিইএফ) যৌথভাবে এই স্বীকৃতি দেয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশের ফুল চাষ, প্রচলিত পদ্ধতিতে ধান চাষ, পাহাড়ে জুমচাষ এবং একসঙ্গে ধান ও মাছ চাষের পদ্ধতি বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী চাষপদ্ধতির সম্ভাব্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কৃষিভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন অঞ্চলকে অবশ্যই মূলধারার পর্যটন খাতের স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন এবং এসব স্থান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে করা উচিত। নীতিমালা প্রণয়নের সুবিধার্থে এবং পর্যটন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নীতি কাঠামোতে কৃষি পর্যটন স্বীকৃত।
সরকারের কৃষি বিনিয়োগের পাশাপাশি কৃষি পর্যটনে কিভাবে কৃষকদের সম্পৃক্ত করা যায়, তাদের কৃষিভিত্তিক পর্যটনের ওপর ট্রেনিং, কৃষি পর্যটনে আপামর জনসাধারণকে উদ্বুুদ্ধকরণ, এর জাতীয়ভিত্তিক প্রচারণার মাধ্যমে কৃষি পর্যটনকে জিডিপি আয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে। জাতীয় কৃষি নীতিমালা ২০১৮ এবং জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা ২০২০ কৃষি পর্যটনকে উন্নত করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা কৃষি পর্যটনের সম্ভাবনার কয়েকটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে।
কৃষি সভ্যতার বিকাশের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতির। এই ঐতিহ্য পর্যটনে ব্যবহৃত হতে পারে সহজেই। কৃষিতে পর্যটন যোগ করা হলে কৃষক এবং গ্রামীণ এলাকার জন্য বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব, যা গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবিকা নির্বাহে অবদান রাখতে পারে।
এগিয়ে যাক বাংলাদেশের কৃষি, এগিয়ে যাক বাংলাদেশের পর্যটন।
লেখক : উপ-পরিচালক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল : সনধংযরৎঢ়ৎড়১৯৮৬@মসধরষ.পড়স, মোবাইল : ০১৩০৩-৭০৬৮২০
 আধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা : বাড়বে মাছের উৎপাদন, মজবুত হবে অর্থনীতির ভিত
আধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা : বাড়বে মাছের উৎপাদন, মজবুত হবে অর্থনীতির ভিত
আধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা : বাড়বে মাছের উৎপাদন, মজবুত হবে অর্থনীতির ভিত
কৃষিবিদ মো. সামছুল আলম
জাতীয় অর্থনীতিতে এবং বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার সমৃদ্ধ-স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মৎস্য খাতের ভূমিকা হবে অনন্য-অসাধারণ। দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে, পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, উদ্যোক্তা তৈরিতে, বেকারত্ব দূর করতে, গ্রামীণ অর্থনীআধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা : বাড়বে মাছের উৎপাদন, মজবুত হবে অর্থনীতির ভিততি সচল রাখতে সকল ক্ষেত্রেই মৎস্য খাতের অবদান রয়েছে। শুধু তাই নয়, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। স্মার্ট টেকনোলজি প্রয়োগের জন্য মৎস্য খাতে বিশাল সুযোগ রয়েছে। সমুদ্র থেকে শুরু করে উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য খাতে স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। মাছের উৎপাদন, আহরণ, পরীক্ষা, বিপণন ও বহুমুখী ব্যবহারে স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।
মৎস্য খাতে স্মার্ট প্রযুক্তি যেমন রিমোট কন্ট্রোল অপারেটেড ফিশ ফিডার, অটোমেটিক পদ্ধতিতে পানির গুণাগুণ নির্ণয়, স্মার্ট সেন্সর, স্মার্ট আন্ডারওয়াটার ক্যামেরা, আইওটি ভিত্তিক স্মার্ট মৎস্য খামার ব্যবস্থাপনা, রিমোট সেনসিং এবং জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে রোগের পূর্বাভাস প্রদান ও দমন,পানির গুণাগুণ নির্ণয়, রোবটিক্সের ব্যবহার ইত্যাদি অন্যতম। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর যুগে আমাদের স্বল্প সময় ও কম খরচে অধিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এসব স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন অটোমেটিক ফিশ ফিলেটিং মেশিন, অটোমেটিক ফিশ ইনস্পেকশন সেন্সর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমাদের মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় এসব প্রযুক্তিও ব্যবহার করা যাবে। দেশের মৎস্য চাষি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার মনস্ক ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। এতে মৎস্য খাতে আধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে, মাছের উৎপাদন বাড়বে এবং অর্থনীতির ভিত মজবুত হবে।
আইইউসিএন ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ঁহরড়হ ভড়ৎ পড়হংবৎাধঃরড়হ ড়ভ হধঃঁৎব. (২০১৫) এর তথ্য মতে, আমাদের মিঠাপানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৬৪ প্রজাতির মাছ বিপন্নের তালিকায় চলে গিয়েছিল। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে বিভিন্ন বায়োটেকনোলজি ব্যবহার করে বিপন্ন প্রজাতির ৩৯টি মাছের প্রজনন এবং চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। দেশে প্রথমবারের মতো ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহের স্বাদুপানি কেন্দ্রে দেশীয় মাছের লাইভ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত এ লাইভ জিন ব্যাংকে মিঠাপানির ১১২ প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রকৃতিতে কোনো মাছ হারিয়ে গেলে কিংবা বিপন্ন হলে লাইভ জিন ব্যাংকের মাছ থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এসব মাছ পুনরুদ্ধার করা যাবে। এভাবে এসব স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মাছের সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
এছাড়াও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিএফআরআই) ইতোমধ্যে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৭৫টি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মৎস্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে সাম্প্রতিককালে দেশে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তির মধ্যে বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও চাষ, কৈ মাছের রোগ নিরাময়ে ভ্যাকসিন তৈরি, অ্যাকোয়াপনিক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও সবজি উৎপাদন, নোনাপানির চিত্রা ও দাতিনা মাছের পোনা উৎপাদন, অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ যেমন-কুঁচিয়া ও কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন এবং চাষ, মিঠাপানির ঝিনুকে ইমেজ মুক্তা উৎপাদন, সাগর উপকূলে সিউইড চাষ ও এর ব্যবহার, বিএফআরআই মেকানিক্যাল ফিশ ড্রায়ার ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন শুঁটকি মাছ উৎপাদন এবং ইলিশের ছয়টি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা অন্যতম। মৎস্য উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে ব্যবহার ও সরকারের মৎস্যবান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দেশে মাছের উৎপাদন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৯.১৫ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে।
তছাড়াও প্রচলিত মৎস্যসম্পদের পাশাপাশি বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ যেমন কুঁচিয়া, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, সিউইড ইত্যাদি সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আমাদের খাদ্যতালিকায় এসব অপ্রচলিত প্রজাতি না থাকলেও বিদেশে এদের প্রচুর চাহিদা ও বাজারমূল্য রয়েছে। এসব পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। এ পরিপ্রেক্ষিতে কুঁচিয়া, কাঁকড়া, শামুক ও ঝিনুক সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজ করছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনে ইনস্টিটিউট এখন সক্ষমতা অর্জন করেছে।
প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন এখন সময়ের দাবি । বাংলাদেশ বর্তমানে প্রায় ৫২টি দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করছে। মানসম্মত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য পরীক্ষার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় আন্তর্জাতিক মানের তিনটি মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে মৎস্য ও মৎস্যজাতীয় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আমাদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, সঠিক পরিচর্যা ও বাজারজাতকরণের অভাবে মাছে শতকরা ৩০-৪০ ভাগ পুষ্টি কম পাওয় যায়। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের স্মার্ট ব্যবস্থাপনার অভাবে কাক্সিক্ষত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ ও বিস্তৃতি নির্ণয় এবং সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ণয়ের লক্ষ্যে সমুদ্রে জরিপকার্য পরিচালনা করা হয়েছে। মৎস্যসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
তাছাড়া সাগর ও নদীতে সরকারের বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ ও বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই এর উৎপাদন বেড়েছে। অপর ১০টি দেশে ইলিশ উৎপাদন কমেছে। দেশে মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান ১২.২২ ভাগ, যার বর্তমান বাজারমূল্য ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা মেটাতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।
এছাড়া সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সমুদ্রে প্রচলিত ও অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও টেকসই আহরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং তা এসডিজির সঙ্গে সমন্বয় করে হালনাগাদ করা হয়েছে। এরই মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ ও সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের সমুদ্রসীমায় মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভিল্যান্স জোরদারকরণে ১০ হাজার আর্টিসানাল মৎস্য নৌযান ও ৫টি বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান প্রযুক্তিভিত্তিক ভেসেল মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে।
লাভজনক এ মৎস্যখাতে উৎপাদন, আহরণ, বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানিসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় এক কোটি ৯৫ লাখ মানুষ সম্পৃক্ত। এক সময় মাছ চাষে অনেকের অনাগ্রহ ছিল। এখন শিক্ষিত জনগোষ্ঠী মাছ চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিতে সম্পৃক্ত হয়েছে। মৎস্য খাতকে বিকশিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বলেছিলেন, মাছ হবে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে নানা প্রযুক্তির ব্যবহারে এখাতের ব্যবহার দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে ও এর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বে সাফল্যের রেকর্ড সৃষ্টি করছে।
জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ‘দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচার ২০২২’ শীর্ষক বৈশ্বিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, চাষের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয় অবস্থান অর্জন করেছে। বাংলাদেশের আগে রয়েছে কেবল ভারত ও চীন। ছয় বছর ধরে বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে পঞ্চম অবস্থানে ছিল। এ অর্জন অত্যন্ত গৌরব ও সম্মানের। এ ছাড়াও এফএওর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছ আহরণে বাংলাদেশ তৃতীয়, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিশ উৎপাদনে যথাক্রমে ৮ম ও ১১তম স্থান অধিকার করেছে। তাছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম, তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ এবং এশিয়ার তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এছাড়া ইলিশ আহরণে প্রথম (বর্তমানে ইলিশের মোট উৎপাদন ৫ লাখ ৬৭ হাজার মেট্রিক টন) অবস্থানে রয়েছে।
মাছ থেকে পুডিং, বিস্কিট, চকোলেট, বার্গার, ফিশ ফিংগার, ফিশ বল, চিপস বা অন্য কোন সুস্বাদু খাবার তৈরি করলে সেটা নতুন প্রজন্ম সহজেই মৎস্যজাত খাবার গ্রহণ করবে।
২০১০ সালের খানা জরিপে জানা গেছে, বাংলাদেশে বছরে প্রতিজন প্রায় ১২ কেজি মাছ খেতো। এখন সেটা ৩০ কেজিতে পৌঁছেছে। দেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান ১৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ। জিডিপিতে কৃষির অবদান কমলেও মৎস্য উপখাতের (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩) বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও ২০২২-’২৩ অর্থবছরে ৬৯ হাজার ৮৮০ দশমিক ৫৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশের আয় হয়েছে ৪ হাজার ৭৯০ কোটি ৩০ লাখ টাকা।
অতএব, সর্বোপুরি বলা যায়, মৎস্য খাতে আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণসহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নিরাপদ মৎস্যসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে অর্জিত হবে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এবং মৎস্যখাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে দেশ।
লেখক : গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মোবা: ০১৭৪৬৭৪৯০২০, ই-মেইল : ধষধস৪১৬২@মসধরষ.পড়স
 শেরেবাংলা কৃষি বিশ^বিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত SAU স্মার্ট সিকিউরিটি গার্ড
শেরেবাংলা কৃষি বিশ^বিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত SAU স্মার্ট সিকিউরিটি গার্ড
শেরেবাংলা কৃষি বিশ^বিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত SAU স্মার্ট সিকিউরিটি গার্ড
মো: মাসুদ রানা
বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে, এদেশের পুকুর, ঘের, বিল, হাওর, বাঁওড় এমনকি নদীতেও খাঁচায় ব্যাপকভাবে মাছ চাষ হয়। মৎস্য খামারিদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা বিশ্বে মাছ উৎপাদনে ৪র্থ স্থানে অবস্থান করছি, স্বাদু পানির মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে ২য় স্থান ধরে রেখেছি। মৎস্য খামারিরা মাছ উৎপাদন করার নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তার মধ্যে মাছ চুরি অন্যতম। একটা পুকুরে চুরি হলে খামারিদের পথে বসতে হয় কেননা বর্তমান সময়ে মাছ উৎপাদনের খরচ গত কয়েক বছরের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছ চাষিদের এই চুরি ঠেকানো এবং চাষকৃত পুকুর বা জলাশয়ের সঠিক দেখভালের জন্য শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপান বাংলাদেশ রোবটিক্স উদ্ভাবন করেছে স্মার্ট সিকিউরিটি গার্ড নামক যন্ত্র যার নাম দিয়েছে ঝঅট স্মার্ট সিকিউরিটি গার্ড।
স্মার্ট সিকিউরিটি গার্ড নামক যন্ত্রটির বিশেষত্ব হলো যন্ত্রটিতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যন্ত্রটিতে একটি উচ্চ বিকিরণ সম্পূর্ণ ঘূর্ণায়মান লাইট ও তার সাথে একটি উচ্চ রেজুলেশন সম্পন্ন ক্যামেরা লাগানো আছে। যন্ত্রটিতে কিছু নিখুঁত প্রোগ্রাম সেট করা হয়েছে, যা ঐ খামারের যে কোন কর্মচারীর নিখুত কণ্ঠ নিশ্চিত করতে পারবে। যন্ত্রটি সম্পূর্ণ রিনিউয়েবল এনার্জি দিয়ে চলবে সে জন্য যন্ত্রটির সাথে সোলার প্যানেল ও ব্যাটারি সংযুক্ত করা হয়েছে। যন্ত্রটি ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছাড়া কার্যকর থাকবে ফলে যন্ত্রটি ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন সাপোর্ট দিবে।
যন্ত্রটির সাথে পকেট রাউটার সংযুক্ত করা আছে ফলে যন্ত্রটিতে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সংযোগ থাকবে যা যন্ত্রটি দিয়ে তোলা ছবি বা ভিডিও দ্রুত সময়ের মধ্যে মোবাইল অ্যাপস ঝঅট স্মার্ট সিকিউরিটি গার্ড এ সংযুক্ত হবে। ফলশ্রুতিতে খামারি যে কোন স্থানে বসে ২৪ ঘণ্টা খামারের সচিত্র রূপ দেখতে পাবেন। যন্ত্রটিতে রোবটিক্স ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি (অও) ব্যবহার করা হয়েছে ফলে রাতের বেলা যন্ত্রটি থেকে খামারে কর্মরত একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তিকে ডেকে লাইট জ্বালাতে বলবে এবং তৎক্ষণাৎ যন্ত্রটিতে সন্নিবেশিত উচ্চক্ষমতার লাইট জ্বলবে এবং তা পুরো পুকুর প্রদক্ষিণ করবে ফলে চোর শুধু না অনান্য নিশাচর প্রাণী ভয় পেয়ে কাছেও আসবে না, আবার মালিক ঘরে বসেও রাতের সে দৃশ্য মোবাইল অ্যাপস এ দেখতে পারবে এবং সে চাইলে যা বলবে তা পুকুর পাড়ে বেজে উঠবে। এভাবে যন্ত্রটি পুকুর/ খামারকে নিরাপদ রাখবে।
এ ছাড়া যন্ত্রটিতে ইমেজ প্রসেসিং টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রতি ১৫ মিনিট পর পর পুকুরের চারপাশের যে চিত্র মোবাইলে সন্নিবেশিত হবে তা অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রসেস করে বলতে পারবে পুকুর পাড়ে মানুষ না অন্য কোন প্রাণি চলাফেরা করছে, শুধু তাই না যদি মানুষের উপস্থিতি শনাক্ত হয় তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাপসের মাধ্যমে মোবাইলে নোটিফিকেশন আসবে যা দেখে খামারি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুকুর বা খামারের চুরি ঠেকাতে সক্ষম হবে। শেরে বাংলা কৃষি বিশ^বিদ্যালয় উদ্ভাবিত ঝঅট স্মার্ট সিকিউরিটি গার্ড নামক যন্ত্রটি ইতোমধ্যে গাজীপুরের একটি খামারে ব্যবহার হচ্ছে যেখানে কয়েকটি বড় পুকুরকে একটি মাত্র যন্ত্রের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছেন খামারটির মালিক যা তার নিরাপত্তাজনিত খরচ ৬০% কমিয়ে দিয়েছে।
স্মার্ট সিকিউরিটি গার্ড নামক যন্ত্রটি প্রতিস্থাপন ব্যয় প্রায় এক লক্ষ টাকা মাত্র এবং যন্ত্রটিতে পকেট রাউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য মাসিক ব্যয় হবে ২৫০-৩০০ টাকা যা একটি খামারের ৪-৫টি পুকুরকে (৪০-৬০ শতাংশ) ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। বাংলাদেশের যে কোন বাণিজ্যিক খামারির জন্য যন্ত্রটি প্রতিস্থাপন ব্যয় বহন করা সম্ভব। ঝঅট স্মার্ট সিকিউরিটি গার্ড নামক যন্ত্রটি যদি কোন খামারি তার খামার বা ঘেরে প্রতিস্থাপন করতে আগ্রহী হলে ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশিং এন্ড পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগে যোগাযোগ করে সেবা নিতে পারবেন।
খামারিদের উৎপাদন খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ, মাছচাষিরা সরাসরি বাজারে প্রবেশ করতে না পারায় খামারিরা তাদের কাক্সিক্ষত মুনাফা পান না তার উপর যদি পুকুরে চুরি হয় তাহলে মাছচাষির রাস্তায় বসা ছাড়া উপায় থাকবে না। উদ্ভাবিত যন্ত্রটি পুকুর, ঘের বা খামারের নিরাপত্তা দেবার পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিশন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মৎস্য সেক্টরে স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে যা খামারির আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটাবে এবং স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট ইকোনমি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।
লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ফিশিং এন্ড পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৭, মোবাইল : ০১৭৪৫-৬২৬১৫৩, ই-মেইল : ranadof@gmail.com
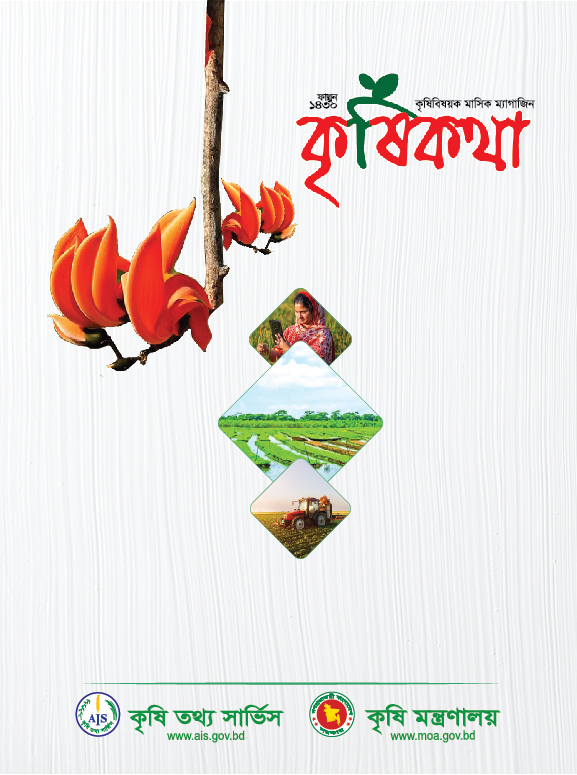 ভেড়ার-বাণিজ্যিক-পালন-পদ্ধতি
ভেড়ার-বাণিজ্যিক-পালন-পদ্ধতি
 প্রশ্নোত্তর
প্রশ্নোত্তর
প্রশ্নোত্তর
কৃষিবিদ আকলিমা খাতুন
নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য আপনার ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও রোগ দমনে সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনা অনুসরণ করুন।
আবু বক্কর সিদ্দিকী, উপজেলা : হাতীবান্ধা, জেলা : লালমনিরহাট
প্রশ্ন : ঢেঁড়সের পাতায় হলুদ-সবুজ রঙের দাগ পড়েছে এবং শিরাগুলো স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, কী করণীয়?
উত্তর : ঢেঁড়সের পাতার মোজাইক ও শিরা স্বচ্ছতা রোগ ণবষষড়ি াবরহ পষবধৎরহম সড়ংধরপ ারৎঁং এর আক্রমণে হয়। এর ফলে সব পাতা হলুদ ও সবুজ রঙের ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়। পাতার শিরাগুলো স্বচ্ছ ও হলুদ হয়ে যায়। গাছের পাতা ছোট ও খর্বাকৃতি হয়। ভাইরাসের বাহক পোকা সাদা মাছি এ রোগ ছড়ায়। আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তুলে নষ্ট অথবা পুড়ে ফেলতে হবে। আক্রান্ত ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না। বাহকপোকা (জ্যাসিড/সাদা মাছি) দমনের জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক যথা: ইমিডাক্লোরপ্রিড গ্রুপের টিডো বা এডমায়ার ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ৩ বার ১০ দিন পরপর।
রেজাউল ইসলাম, উপজেলা : ডিমলা, জেলা : নীলফামারী
প্রশ্ন : তরমুজের পাতায় কালো কালো দাগ দেখা যাচ্ছে, করণীয় কী?
উত্তর : তরমুজের এ্যানথ্রাকনোজ রোগ পড়ষষবঃড়ঃৎরপযঁস ংঢ়. ছত্রাকজনিত রোগ। পাতায় বাদামি থেকে কালো দাগ দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণে পাতার বোটা, কা- ও ফলে কালো দাগ দেখা যায়। এ রোগ তাড়াতাড়ি বিস্তার লাভ করে এবং গাছ ও ফল সমূহের ক্ষতি করে। এরোগ দমনে ক্ষেত পরিষ্কার রাখতে হবে। রোগাক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট বা পুড়ে ফেলতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে প্রোভেক্স বা ভিটাভেক্স ২.৫ গ্রাম বা ব্যাভিস্টিন-২ গ্রাম দ্বারা প্রতি কেজি বীজ শোধন করতে হবে। রোগের আক্রমণ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের (ব্যাভিস্টিন) ১ গ্রাম বা ম্যানকোজেব গ্রুপের (ডাইথেন এম ৪৫) ছত্রাকনাশক ২.৫ গ্রাম প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।
জহুরুল ইসলাম, উপজেলা : বোদা, জেলা : পঞ্চগড়
প্রশ্ন : চিচিঙ্গার পাতায় আঁকা বাঁকা রেখার মতো দাগ পড়েছে, কী করতে হবে?
উত্তর : চিচিঙ্গার পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকার কীড়া পাতার দুইপাশের সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। তাই পাতার উপর আঁকাবাঁকা রেখার মতো দাগ পড়ে এবং পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়। আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে বা পুড়ে ফেলতে হবে। আঠালো হলুদ ফাঁদ স্থাপন করতে হবে। সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক (কট ১০ ইসি বা রিপকর্ড) ১ মিলি./লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ৩ বার। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া যাবে না বা বিক্রি করা যাবে না।
নাঈম হোসেন, উপজেলা : সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা: সিরাজগঞ্জ
প্রশ্ন : পাট চাষের জন্য বীজ হার ও সারের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চাই।
উত্তর : পাটের বীজ ছিটিয়ে বুনলে ৬.৫-৭.৫ কেজি/ হেক্টর, লাইন করে বুনলে ৩.৫-৫.০০ কেজি/ হেক্টর। লাইন করে বুনলে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৩০ সেমি. বা একফুট এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭-১০ সেমি. বা ৩-৪ ইঞ্চি হতে হবে। ভালোভাবে প্রস্তুতকৃত জমিতে বপনের ২-৩ সপ্তাহ আগে হেক্টরপ্রতি ৩.৫ টন গোবর সার মিশিয়ে দিতে হবে। বপনের দিন ১৫ কেজি ইউরিয়া, ১৭ কেজি টিএসপি ও ২২ কেজি এমওপি সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। অতঃপর বীজবপনের ৬-৭ সপ্তাহ পর ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার ও চারা পাতলা করে হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া সার জমিতে পুনরায় ছিটিয়ে দিতে হবে।
আব্দুর রহিম, উপজেলা : রাজারহাট, জেলা : কুড়িগ্রাম
প্রশ্ন : পুঁইশাকের শিকড়ে গিট দেখা যাচ্ছে, কী করণীয়?
উত্তর : পুঁইশাকের শিকড়ে কৃমির আক্রমণে ছোট ছোট গিট দেখা যায়। গিটগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়। আক্রান্ত গাছ ছোট, দুর্বল ও হলদে হয়ে যায়। রোগাক্রান্ত শিকড়ে সহজেই পচন ধরে। একসময় গাছ মরে যায়। এ রোগ দমনে কার্বোফুরান হেক্টরপ্রতি ৪৫ কেজি হারে ব্যবহার করতে হবে। একই জমিতে বারবার পুঁইশাক চাষ করা যাবে না। চারা উৎপাদনের আগে বীজতলায় ৬ সেমি. পুরু স্তরে কাঠের গুঁড়া বিছিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে কৃমি ও অন্যান্য রোগজীবাণু দমন করতে হবে। বীজ বা চারা লাগানোর তিন সপ্তাহ আগে হেক্টর প্রতি আধা পচা মুরগির বিষ্ঠা ৫-১০ টন ও সরিষার খৈল ৩০০-৬০০ কেজি প্রয়োগ করে জমিতে পচালে কৃমি দমন করা যায়।
জনাব সবুজ, উপজেলা : মধুখালী, জেলা : ফরিদপুর
প্রশ্ন : টমেটোর পাতায় ভেজা কালচে দাগ দেখা যাচ্ছে। করণীয় কী?
উত্তর : এটি টমেটোর নাবী ধসা রোগ ঐধষরপ ঋমংঃ রহভবংঃড়হং নামক ছত্রাক দ্বারা এই রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত পাতায় প্রথমে ফ্যাকাশে অথবা ফিকে সবুজ গোলাকার বা এলোমেলো পানি ভেজা দাগ পড়ে। পরবর্তীতে তা কালচে থেকে বাদামি রং ধারণ করে। বেশি আক্রমণে কা- ও আক্রান্ত হয় এবং গাছ ঝলসে মারা যায়। ম্যানকোজেব+মেটালিক্সিল গ্রুপের রিডোমিল গোল্ড/করমিল/ মেটারিল ২ গ্রাম অথবা ম্যানকোজেব+ফেনামিডন গ্রুপের সিকিউর ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
জনাব মেহেদি, উপজেলা : পার্বতীপুর, জেলা : দিনাজপুর
প্রশ্ন : কাঁকরোলের গায়ে ছিদ্র দেখা যায়। কারণ ও প্রতিকার কী?
উত্তর : এটি কাঁকরোলের ফল ছিদ্রকারী পোকা। এ পোকার কীড়া কচি ফল ও ডগা ছিদ্র করে ভেতরের শাস খায়। ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয়। থায়ামিথক্সাম+ ক্লোরানট্রানিলিপ্রলি জাতীয় কীটনাশক যেমন-ভলিয়ম ফ্লেক্সি ০.৫ মিলিলিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক যেমন-ওস্তাদ ২ মিলিলিটার বা ম্যাজিক ১ মিলিলিটার বা কট ১ মিলিলিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বা স্প্রে করতে হবে।
জনাব আরাফাত, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ
প্রশ্ন : তিল গাছের কা-ে খয়েরি রঙের দাগ পড়েছে। কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানতে চাই।
উত্তর : এটি তিলের কা- পচা রোগের লক্ষণ। ম্যাক্রোফোমিনা ফ্যাসিওলিনা নামক ছত্রাকের কারণে এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে কা-ে পানিভেজা, ছোট, লম্বা ও আঁকাবাঁকা খয়েরি ও কালচে পড়া দাগ দেখা যায়। পড়ে দাগগুলো বড় হয় ও পুরোগাছে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক সময় গাছ মারা যায়। কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক চ্যাম্পিয়ন ২ গ্রাম/লিটার পানিতে বা বিটক্স ৪ গ্রাম/ লিটার পানিতে অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ব্যাভিস্টিন ১ গ্রাম/লিটার পানিতে অথবা ম্যানকোজেব গ্রুপের ডাইথেন এম ৪৫ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
উত্তম কুমার, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া
প্রশ্ন : কাঁঠালের মুচি কালো হয়ে ঝরে পড়ছে। করণীয় কী?
উত্তর : এটি কাঁঠালের মুচি পচা রোগ। ৎযরুড়ঢ়ঁং ংঢ়. নামক ছত্রাক ধারা এ রোগ হয়। এ ছত্রাকের আক্রমণের ফলে বাদামি দাগ পড়ে দাগগুলো কালচে হয় ও মুচি পচে যায়। পচা অংশে অনেক সময় সাদা মাইসেলিয়াম দেখা যায়। ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক ডাইথেন এম-৪৫ বা ইন্সেফিল এম- ৪ ২ গ্রাম অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক এমকোজিম ২ গ্রাম অথবা প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে দশ (১০) দিন পর পর ২-৩ বার শেষ বিকেলে স্প্রে করতে হবে।
জনাব সজল, উপজেলা : মঠবাড়িয়া, জেলা : পিরোজপুর
প্রশ্ন : শসার পাতা ও ফলে কালো কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। করণীয় কী?
উত্তর : এটি শসার এনথ্রাকনোজ রোগ। পড়ষষবঃড়ঃৎরপযঁস ংঢ়. নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগে আক্রান্ত পাতা ও ফলে ছোট ছোট কালো পচা দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে দাগগুলো একত্র হয়ে গাছ ও ফল পচে যায়। কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের নোইন ১ গ্রাম অথবা প্রোপিকোনাজল গ্রুপের টিল্ট ০.৫ মিলিলিটার বা কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ২ গ্রাম হারে স্প্রে করতে হবে ৭ দিন পরপর ৩ বার।
শরিফ, উপজেলা : নড়িয়া, জেলা : শরীয়তপুর
প্রশ্ন : আদা পাতার মাঝে ডিম্বাকৃতির দাগ দেখা যাচ্ছে। দাগগুলোর মাঝে সাদা বা ধূসর রং দেখা যায়। এই সমস্যা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি?
উত্তর : আদার পাতায় দাগ পড়া একটি ছত্রাকবাহিত রোগ। পড়ষষবঃড়ঃৎরপযঁস ংঢ়. নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগের বিস্তার ঘটে। এ রোগের আক্রমণ দেখা দিলে ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক ডাইথেন এম ৪৫ ২ গ্রাম বা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাক নাশক ব্যাভিস্টিন বা নোইন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ ছাড়া রোগ প্রতিরোধক জাত ও রোগমুক্ত গাছ থেকে কন্দ ব্যবহার করতে হবে।
আব্দুর রহিম, উপজেলা : আত্রাই, জেলা : নওগাঁ
প্রশ্ন : বরবটি গাছে এক ধরনের পোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলেছে। এই পোকা কিভাবে দমন করতে পারি?
উত্তর : বরবটি গাছে বিছা পোকার আক্রমণ হয়েছে। এ পোকার আক্রমণ দেখা দিলে সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের রিপকর্ড ১ মিলি অথবা ফেনিট্রোথিয়ন গ্রুপের সুমিথিয়ন ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ৩ বার। এ ছাড়া পোকার ডিম ও বাচ্চা হাত দিয়ে বাছাই করতে হবে।
হুমায়ুন শেখ, উপজেলা : শ্রীপুর, জেলা : গাজীপুর
প্রশ্ন : কলাগাছের পাতায় ছোট ছোট হলুদ দাগ দেখা যাচ্ছে। দাগগুলো ক্রমশ বড় হয়ে বাদামি রং ধারণ করে এবং পাতা পুড়ে যাচ্ছে। কিভাবে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি?
উত্তর : এটি কলাগাছের সিগাটোকা রোগ নামে পরিচিত। পবৎপড়ংঢ়ড়ৎধ সঁংধব নামক ছত্রাক দ্বারা ও রোগের বিস্তার ঘটে। প্রতিকার হিসেবে প্রোপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলি অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ব্যাভিস্টিন ১ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে ৩ বার। এ ছাড়া আক্রান্ত গাছের পাতা পুড়ে ফেলতে হবে।
লেখক : তথ্য অফিসার (উদ্ভিদ সংরক্ষণ), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। মোবাইল : ০১৯১৬৫৬৬২৬২; ই-মেইল : aklimadae@gmail.com
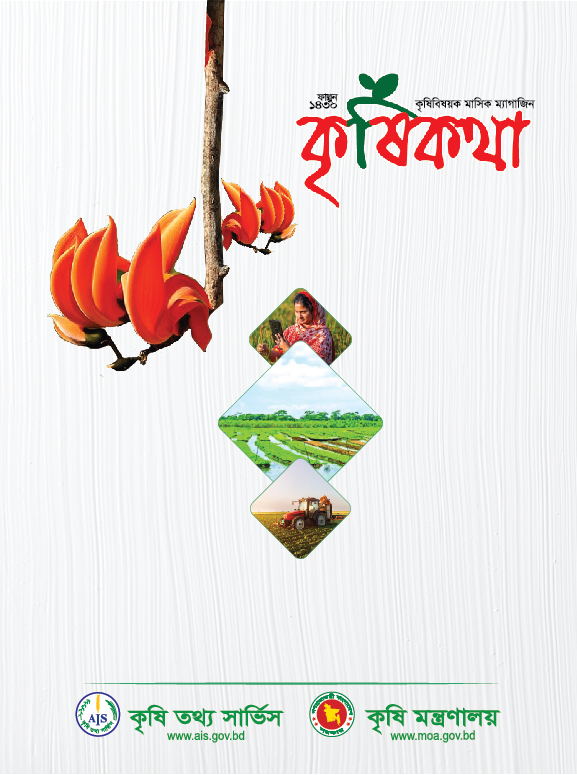 সিঙ্গারা-ফল-(পানি-ফল)-চাষের-সাফল্য
সিঙ্গারা-ফল-(পানি-ফল)-চাষের-সাফল্য
সিঙ্গারা ফল (পানি ফল) চাষের সাফল্য
ড. এস.এম. আতিকুল্লাহ১, ড. বরুন পাল২
কৃষিতে ‘স্মার্ট এগ্রিকালচার’ বৈশি^ক পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবেলায় খাপখাইয়ে নেয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঝুঁকি মোকাবিলায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাতক্ষীরা জেলা বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এখানে লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা কৃষি উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করছে। এই অবস্থা উত্তরণে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রচেষ্টায় জেলায় ‘স্মার্ট এগ্রিকালচার’ পদ্ধতি অনুসরণ করে একই জমিতে পর্যায়ক্রমে ধান ও সিঙ্গারা ফল চাষে সাফল্য অর্জন সম্ভব হচ্ছে। যে জমি ও জল কৃষকের কাছে জঞ্জাল ছিল তা এখন আর্থিক সুফল এবং পুষ্টি জোগানে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। চাষের জমি যা বর্ষায় জলাবদ্ধ থাকে এমন জমিতে মৌসুমি সিঙ্গারা ফল চাষে সাফল্য আসছে। বিগত ৮-১০ বছর ধরে এই অঞ্চলে সিঙ্গারা চাষ সম্প্রসারণ হচ্ছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এই ফল সামান্য যত্ন ও ন্যূনতম খরচে চাষ করা যায়। বিশেষ করে কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধিতে সিঙ্গারা ফল চাষ বেশ অবদান রাখছে। তথ্য মতে, সুজলা-সুফলা সাতক্ষীরা জেলায় সিঙ্গারা ফল চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ সালে ১০৬ হেক্টর জমিতে ২৭৫৫ মেট্রিক টন সিঙ্গারা উৎপাদিত হয়েছে।
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি মাড়িয়ে প্লাবিত জমিতে ফসল উৎপাদন সহনশীল কৃষির বাস্তব উদাহরণ। জমিতে জল আসতেই হালকা চাষ দিয়ে বীজ বপন করা হয়। ক্রমান্বয়ে পানি বাড়ে সাথে সিঙ্গারা গাছও বৃদ্ধি পেতে থাকে। গাছের পাতা জলে ভাসতে থাকে। বাড়তি জল ফসলের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। দো-আঁশ মাটিতে এ উদ্ভিদ ভাল জন্মে। মূলত সাতক্ষীরার জলবায়ু সিঙ্গারা চাষের জন্য উপযোগী, উদ্ভিদ জন্মানোর অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে।
তাজা ফল আহারে কচকচে এবং নরম যা তৃষ্ণানিবারক। অভাব-অনটনে রান্না করে ডাল বা জাউ খাওয়া হয়। খাবার টেবিলে বিকল্প পরিবেশনায় রসনা তৈরি করে। এই ফল ডায়াবেটিক রোগ নিরাময়ক। পানাসক্ত ব্যক্তির মাতলামো নিবারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। চীনদেশে পানিফল জ্বর নিরাময়ক। ফল শুকিয়ে গুঁড়া করে আটা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই সামাজিক অনুষ্ঠান পূজা তথা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের মাধ্যম হিসেবে এই ফলকে বিবেচনা করা হয়। হিন্দু সমাজে এই ফলের চূর্ণ বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় উৎসবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে এই চূর্ণকে “সিঙ্গারা-কা-আটা” নামে অবহিত করে। এই ফল সকালের নাশতায়, দুপুরের পিপাসা নিবারণ তথা টেবিলে অন্যান্য ফলের সাথে পরিবেশন করা যেতে পারে।
শিশুর প্রিয় পানিফল : কচকচা ফল শিশুরা খেতে খুব পছন্দ করে। কালিগঞ্জ উপজেলার শিশু-কিশোরের মধ্যে মৌসুমে বেশ আমোদ-ফুর্তি লক্ষ করা যায়। শিশুরা কাটি-কুটি করে ফল ত¦ক খোটাখুটিতে বেশ আনন্দ পায়। তাই এই ফলকে গ্রামীণ পুষ্টির সহজ যোগানদার বলা যায়। সাধারণ গ্রামীণ শিশু-কিশোররা দামি ফল খেতে পারে না। তাদের বিকল্প পুষ্টির সুযোগ সৃষ্টি করে। খাদ্যোউপযোগী প্রতি-১০০ গ্রাম পানিফলে ৮৪.৯ গ্রাম জলীয় অংশ, মোট খনিজ পদার্থ ০.৯ গ্রাম, ০.৬ গ্রাম আঁশ, ৬৫ কিলো ক্যালরি খাদ্যশক্তি, ২.৫ গ্রাম আমিষ, ০.৯ গ্রাম চর্বি , ১১.৭ গ্রাম শর্করা, ১০ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৮ মিলিগ্রাম লৌহ, ০.১৮ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.০৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-২ এবং ১৫ মিলি গ্রাম ভিটামিন সি বিদ্যমান থাকে।
জাত পরিচিতি ও বাজারমূল্য : ভারত ও চীন দেশে এই ফল তিন হাজার বছর পূর্বে জন্মানোর ইতিহাস রয়েছে। এটি দ্বিবীজপত্রী, আবৃতবীজী, বর্র্ষজীবী বীরুৎ প্রকৃতির উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম ঞৎধঢ়ধ নরংঢ়রহড়ংধ জড়ীন.। এই জলজ উদ্ভিদ ঞৎধঢ়ধপবধব বা ওয়াটার চেষ্টনাট গোত্রের সদস্য। ইংরেজিতে ডধঃবৎ পযবংঃহঁঃ শব্দের চয়ন দেশীয় নাম পানিফল। জলজ পরিবেশে পানির নিচে চাষ হয় বিধায় পানিফল বলা হয়। আবার এ ফলের আকার সিংগারার ন্যায় তাই সিঙ্গারা (ঝরহমযৎধ) নাম দেয়া হয়। ফলের আকৃতির কারণে লজেন্স বা হিরার টুকরো ফলও বলে থাকে। এ বছর এরই মধ্যে স্থানীয় বাজারে কেজি প্রতি ২৫-৩০ টাকা দরে বেচাকেনা শুরু হয়েছে। সাতক্ষীরার সিঙ্গারা ঢাকা, নওগাঁ, খুলনা এবং রাজশাহী অঞ্চলে বাজারজাত করা হয়। এই ফল শুকিয়ে গুঁড়া করে আটা হিসেবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা যায়। ভারতসহ পার্শ্ববর্তী দেশে গুঁড়ার চাহিদা তৈরি হচ্ছে। তাই ফল উৎপাদন লাভবান করতে উন্নত চাষ পদ্বতি, আধুনিক জাত ও ফল সংরক্ষণের প্রযুক্তি আবিষ্কার করা দরকার।
এমন নয় যে সিঙ্গারা সাতক্ষীরা জেলার নিজস্ব ফসল। কৃষি বিজ্ঞানীদের সৃজনশীল চিন্তা এবং সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষকের প্রচেষ্টায় সাতক্ষীরা জেলায় সিঙ্গারা চাষের অনেক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামীর কথা বললে সাতক্ষীরা অঞ্চলকে নিয়ে যুতসই “ক্লাইমেট স্মার্ট” কৃষির পরিকল্পনা করতে হবে। তাই আগামীর কৃষির জন্য অঞ্চলভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। বলা হয় এই সাতক্ষীরা অঞ্চলের কৃষক জলাভূমিতে সিঙ্গারা আর প্রান্তিক অফলা জমিতে স্থায়ী ফল বাগান তৈরি করছে। এতে জমি, জল এবং স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে। কৃষিতে ঝুঁকি মোকাবিলার প্রবণতা, জমির বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকের হাতে নগদ অর্থের জোগান হচ্ছে; মুখে ফুটছে হাসি।
লেখক : ১এগ্রিকালচার স্পেশালিস্ট, জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প; ২আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, দিল্লি। মোবাইল : ০১৭১২৮৮৯৯২৭, ই-মেইল : mdatikullah@yahoo.com
 সয়াবিনের সাতকাহন
সয়াবিনের সাতকাহন
সয়াবিনের সাতকাহন
ড. এম এ মান্নান
সয়াবিন প্রকৃতির এক অপূর্ব উপহার বা আশ্চর্য ফসল। কম গ্লাইসেমিক সূচক, কম স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং কোলেস্টেরল মুক্ত এবং পুষ্টিগত সুবিধার কারণে এটাকে “গোল্ডেন বিন” ও বলা হয়। এটি একটি বহুমুখী এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ ফসল যা বাংলাদেশের মানুষের মাঝে এর গুরুত্ব বাড়ছে। এটি ডাল বা শিমজাতীয় উদ্ভিদ বিধায় এর শিকড়ে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া বাতাসের নাইট্রোজেন সংযোজন করে মাটিতে উদ্ভিদের মুখ্য পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।
ব্যবহার ও পুষ্টি
উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবারের (গরুর দুধ এবং মাংস, মাছ এবং হাঁস-মুরগি) মতোই সয়াবিনের অনন্য পুষ্টি গুণ রয়েছে এবং এটি মানুষের দৈনন্দিন প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। এর প্রোটিনের ৮৫% জুড়ে রয়েছে বিটা-কনগ্লাইসিনিন এবং গ্লাইসিনিন। সয়াবিনের দানায় বিদ্যমান কোলিন নামক রাসায়নিক পদার্থ মেধাশক্তি বাড়ায়। সয়াবিনে কার্বোহাইড্রেট কম থাকায় ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য ভালো। সয়াবিনে মানবদেহের প্রয়োজনীয় প্রায় সব এমাইনো এসিড আছে। সব মাছ, মাংস, ডালসহ সব খাদ্যের চেয়ে আমিষ অনেক বেশি থাকে। ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সব ডালের চেয়ে ২-৭ গুণ বেশি আছে। প্রতি ১০০ গ্রাম সয়াবিনে থাকে আমিষ ৪০ গ্রাম, তেল ২০ গ্রাম, শ্বেতসার ১৩ গ্রাম, আঁশ ৪ গ্রাম, খনিজলবণ ৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৫০ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৭০০ মিলিগ্রাম, আয়রন ৭ মিলিগ্রাম ও পটাশিয়াম ১৫৩৩ মিলিগ্রাম। প্রতিদিন ৫০-৬০ গ্রাম সয়াবিনজাত খাদ্য খেলে আমিষের চাহিদা পূরণ হয়। সয়াবিনে অসম্পৃক্ত ফ্যাট এসিড থাকায় হৃদরোগীদের জন্য উপকারী। এটি মানুষ এবং হাঁস-মুরগির জন্য কম খরচে প্রোটিন এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের একটি ভালো উৎস হিসেবে কাজ করায় উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের জন্য সয়াবিন একটি অন্যতম মূল্যবান ফসল। অন্য দিকে এটি ফসফরাস এবং ক্যালসিয়াম এ ভরপুর। এ ছাড়াও এর তেলে ভিটামিন-এ, ডি, লেসিথিন এবং মূল্যবান ফ্যাটি এসিড রয়েছে।
জমি স্বল্পতার জন্য ও সয়াবিনে মাত্র ২০-২২% তেল থাকায় এখনো প্রচলিত পদ্ধতিতে সয়াবিনের বীজ থেকে বাংলাদেশে তেল উৎপাদন সম্ভব হয়নি। তাই দেশে উৎপাদিত সয়াবিনের বেশির ভাগই প্রধানত পশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং বাজারের সব সয়াবিন তেলই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। অধিকাংশ মানুষের ধারণা সয়াবিন থেকে শুধু তেল উৎপাদন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে সয়াবিনের অন্যান্য শস্যের মতো উপযোগিতা আছে। তেলের পাশাপাশি সয়াবিন থেকে টফু, পরোটা, সয়া জিলাপি, মসলাযুক্ত সয়াবাদাম বা নাট, সয়াপেঁয়াজু, সিঙ্গারা, সয়াচটপটি, সয়াময়দা, সয়াশিশুখাদ্য, সয়াডাল, সয়াহালুয়া, সয়াখিঁচুরি, সয়াপাতরা, সয়াভর্তা, সয়াবিন মিশ্রিত মিষ্টি কুমড়ার তরকারি, সয়াবিন মিশ্রিত আলুর তরকারি, সয়াবিন মিশ্রিত শাক, সয়াদুধ, সয়াদই, সয়াভাঁপা পিঠাসহ ৩৬ রকমের খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। সয়ার আটা থেকে নাগেট বা বড়ি তৈরি করা হয়। এটি খেতে অনেকটা মাংসের মতো। মাংসে যে পরিমাণ পুষ্টি থাকে, সেই পরিমাণে পুষ্টি সয়াবড়িতেও পাওয়া যায়। তাই একে সবজিভোজীদের মাংসও বলা হয়। এটি বেশ মজাদার খাবার। সয়া নাগেট মাংসের মতো রান্না করা হয়। এ ছাড়া নিরামিষ, সবজি ও তরকারি যেভাবে রান্না করা হয়, সেভাবেও রান্না করা যায়। সয়াবিনের স্বাস্থ্য উপকারিতার মধ্যে রয়েছে সয়াবিনে চর্বি কম এবং এতে কোলেস্টেরল নেই সয়াবিন ফাইবারের একটি চমৎকার উৎস এটি ভিটামিন বি১২ এর একটি ভাল উৎস হিসেবেও বিবেচিত হয় সয়াবিন অ্যামিনো অ্যাসিড ধারণকারী প্রোটিন খাদ্য যা মানুষের শরীরের জন্য অপরিহার্য সয়াবিন সেবনে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়, হৃদরোগ এবং অস্টিওপরোসিস থেকেও রক্ষা করে।
সয়াবিন গাছ বাতাস থেকে প্রতি হেক্টর জমিতে ৭৫-১২০ পাউন্ড নাইট্রোজেন জমা করে বলে ইউরিয়া সার লাগে না এবং পরের ফসলে ইউরিয়া সার কম লাগে। সয়াবিনের পর গম চাষ করলে ৩৬% ফলন বেশি হয়। সয়াবিন সারা বছর চাষ করা যায় অর্থাৎ রবি ও খরিফ মৌসুমে চাষ করা যায়। সয়াবিন চাষে সার, সেচ, কীটনাশক, পরিচর্যা কম লাগে বলে উৎপাদন খরচ খুব কম। সয়াবিনের পাতা ফসল পাকার সময় ঝরে পড়ে ফলে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করে বিধায় মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। রোপা আমন ধান কাটার পর বিনা চাষে বিনা খরচে সয়াবিন চাষ করা যায়। বিভিন্ন ফসলের সাথে আন্তঃফসল ও সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। এজন্য অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন হয় না।
চাষপদ্ধতি
সয়াবিন চাষ করা খুব সহজ। দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ মাটি সয়াবিন চাষের জন্য ভালো। ৪-৫টি চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। রবি মৌসুমে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে এবং খরিফ মৌসুমে জুলাই-আগস্ট মাসে বীজ বপন করতে হয়। সারি থেকে সারি ১ ফুট এবং বীজ থেকে বীজ ৫-১০সেমি. দূরে দূরে বপন করলে ফলন বেশি হয়। তবে ছিটিয়েও বীজ বপন করা যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সয়াবিনের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে এবং কৃষকপর্যায়ে চাষ হচ্ছে । প্রতি হেক্টরে গোবর ২০ টন, ইউরিয়া ৪০ কেজি, টিএসপি ১৫০ কেজি ও এমওপি ১০০ কেজি দিয়ে চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। তবে জীবাণু সার প্রয়োগ করলে ইউরিয়া সার লাগে না। আগাছা হলে দমন করতে হবে। খরা হলে সেচ দিতে হবে। পোকামাকড়ের মধ্যে বিছাপোকা দ্বারা সয়াবিন গাছ আক্রান্ত হলে আক্রমণের প্রথম অবস্থায় পোকাসহ পাতাটি তুলে পায়ে মাড়িয়ে বা গর্তে চাপা দিয়ে মারতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক যেমন- সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক যেমন-কট ১০ ইসি ১ মিলি বা সিমবুশ ১০ ইসি ০.৫ মিলি./লি. পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। ছাই ছিটিয়ে বা নগস স্প্রে করেও দমন করা যায়। কা-ের মাছি ও পাতা মোড়ানো পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণত রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় না। ৯০ থেকে ১২০ দিনে সয়াবিন পরিপক্ব হয়। প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৫০০ থেকে ২০০০ কেজি ফলন হয়। সয়াবিনের বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজের আর্দ্রতা ১০-১২% হতে হবে। পাত্রের মুখ ভালো করে বন্ধ রাখতে হবে। বীজের পাত্র ঠা-া স্থানে রাখতে হবে।
সয়াবিন নিয়ে গবেষণা
বাংলাদেশে সয়াবিনে প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও এ নিয়ে গবেষণা বেশি হয়নি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯০ সালে সোহাগ (পিবি-২), ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সয়াবিন-৪ (জি-২), ২০০৬ সালে বারি সয়াবিন-৫, ২০০৯ সালে বারি-সয়াবিন-৬ এবং ২০২০ সালে বারি সয়াবিন-৭ নামে সয়াবিনের জাত উদ্ভাবন করে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত সয়াবিনের ৭টি (বিনা সয়াবিন-১, বিনা সয়াবিন-২, বিনা সয়াবিন-৩, বিনা সয়াবিন-৪, বিনা সয়াবিন-৫, বিনা সয়াবিন-৬, বিনা সয়াবিন-৭) জাত উদ্ভাবন করেছে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগ ২০০৭ সালে তাইওয়ান এর এশিয়ান ভেজিটেবল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে দুই শতাধিক সয়াবিনের জেনেটিক লাইন সংগ্রহ করে সয়াবিন নিয়ে গবেষণা শুরু করে । বর্তমানে এ বিভাগ সয়াবিন নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে গবেষণা করে যাচ্ছে । এ পর্যন্ত এ বিভাগ বিইউ সয়াবিন-১, বিইউ সয়াবিন-২, বিইউ সয়াবিন-৩, বিইউ সয়াবিন-৪ নামে ৪টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। যার মধ্যে বিইউ সয়াবিন-১ মাত্র ৬৫ থেকে ৭০ দিনে ফসল কাটা যায় এবং বিইউ সয়াবিন-৩ লবণ সহনশীল যা উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতে চাষ করার জন্য উপযোগী। এ বিভাগ খরা ও জলাবদ্ধতাসহনশীল সয়াবিনের জাত উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বালাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ২৮.৬০ লাখ হেক্টর জমির মধ্যে প্রায় ১০.৫৬ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা আক্রান্ত। এই লবণাক্ত জমিতে লবণ সহনশীল সয়াবিন এবং বাংলাদেশের চরাঞ্চলে উচ্চফলনশীল সয়াবিনের চাষ করলে আমাদের দেশের পোল্ট্রি ও মাছের খাবারের জন্য সয়াবিনের চাহিদার অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব হবে।
প্রায় ৫০০০ বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর প্রথম চাষ শুরু হয়। যখন চীনারা এর পুষ্টিকর মূল্যের জন্য একে ‘হলুদ গহনা’ এবং ‘মহান ধন’ হিসেবে উল্লেখ করেছিল। ১৮৯৪-৯৫ সালে কোরিয়ার উপর চীনা-জাপানি যুদ্ধ এবং চীনের বিপর্যস্ত পরাজয়ের পর ফসলটি জাপান এবং এশিয়ার অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ট্রেডিং ইকোনমিক্স অনুসারে, বতমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং প্যারাগুয়ে সয়াবিনের প্রধান উৎপাদক। রপ্তানিকারক হচ্ছে চীন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মেক্সিকো এবং জাপান প্রধান আমদানিকারক। বিশ্বব্যাপী তেলজাতীয় ফসলের ৫০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে সয়াবিন।
বাংলাদেশে সয়াবিন চাষের সূচনা হয়েছিল ১৯৪২ সালে যদিও ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত এটির জনপ্রিয়তা বাড়ানো বা কোন গবেষণা করা হয়নি। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-র ডাল এবং তেলবীজ বিভাগ খরিফ-২ মৌসুমে পতিত জমিতে আবাদের লক্ষ্যে সয়াবিনের দুটি জাত (পলিকান এবং বর্ণালী) বাছাই করেছিল। পরবর্তীতে হলুদ মোজাইক ভাইরাস এর প্রতি সংবেদনশীল হওয়ায় জাত দুটির উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি (এমসিসি) পুণরায় বাংলাদেশে সয়াবিন চাষ শুরু করে। ১৯৮২ সালে লক্ষ¥ীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় মাত্র ১ হেক্টর জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে সয়াবিনের চাষ করা হয়। এরপর ১৯৯২ সালে এমসিসি ও ডর্প নামক দুটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সয়াবিন চাষে কৃষকদেরকে ব্যাপক উদ্বুদ্ধ করে। তখন থেকেই ধীরে ধীরে অন্য রবি ফসলের সাথে সয়াবিনের আবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বতমানে বাংলাদেশে ৬২,৮৭০ হেক্টর আবাদি জমি থেকে বছরে মোট ৯৬,৯২১ টন সয়াবিন উৎপাদিত হয়, যার প্রায় ৭০ ভাগ লক্ষ¥ীপুর জেলায় উৎপাদিত হচ্ছে যদিও দেশে ডেইরি ও পোল্ট্রি সেক্টরে চাহিদা মেটাতে বছরে প্রায় ১৫ লাখ মেট্রিক টন সয়াবিন প্রয়োজন। কয়েক বছর আগে উপেক্ষিত থাকলেও, ক্রমান্বয়ে অর্থকরী ফসল হিসেবে এর জনপ্রিয়তা বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নোয়াখালী, লক্ষ¥ীপুর এবং ভোলা জেলায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডারে ভেতরের জমিতে এবং চরাঞ্চলে সয়াবিন চাষ করা যায় এবং ভালো ফলন দেয় ।
আমাদের দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় সয়া খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারি ।
লেখক: অধ্যাপক ও সয়াবিন গবেষক, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর। মোবাইল : ০১৭১২০৮৫৭৬৭, ই-মেইল : mannanagr@bsmaru.edu.bd
 চৈত্র-মাসের-কৃষি-(১৫-মার্চ-১৩-এপ্রিল)
চৈত্র-মাসের-কৃষি-(১৫-মার্চ-১৩-এপ্রিল)
চৈত্র মাসের কৃষি
(১৫ মার্চ-১৩ এপ্রিল)
ফেরদৌসী ইয়াসমিন
আমরা ১৪৩০ বঙ্গাব্দের শেষ মাসে চলে এসেছি। চৈত্র মাসে বসন্ত ঋতু নতুন করে সাজিয়ে দেয় প্রকৃতিকে। চৈতালী হাওয়ায় জানান দেয় গ্রীষ্মের আগমন। এ মাসে রবি ফসল ও গ্রীষ্মকালীন ফসলের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম একসাথে করতে হয় বলে কৃষকের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন আসুন আমরা জেনে নেই এ মাসের কৃষিতে আমাদের করণীয় কাজগুলো।
বোরো ধান যারা শীতের কারণে দেরিতে চারা রোপণ করেছেন তাদের ধানের চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। সার দেয়ার আগে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। এলাকার জমিতে যদি সালফার ও দস্তা সারের অভাব থাকে এবং জমি তৈরির সময় এ সারগুলো না দেয়া হয়ে থাকে তবে ফসলে পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ পরীক্ষা করে শতাংশপ্রতি ২৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৪০ গ্রাম দস্তা সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ধানের কাইচ থোড় আসা থেকে শুরু করে ধানের দুধ আসা পর্যন্ত ক্ষেতে ৩-৪ ইঞ্চি পানি ধরে রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে ধান উৎপাদনে সেচের পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি (অডউ) ব্যবহার করা যেতে পারে। পোকা দমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আলোর ফাঁদ পেতে, পোকা ধরার জাল ব্যবহার করে, ক্ষতিকর পোকার ডিমের গাদা নষ্ট করে, উপকারী পোকা সংরক্ষণ করে, ক্ষেতে ডাল-পালা পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ধানক্ষেত বালাইমুক্ত করতে পারেন।
এসব পন্থায় রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা না গেলে শেষ উপায় হিসেবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া নিচু এলাকায় আউশ ও বোনা আমন চাষের এটি উপযুক্ত সময়। ভুট্টা (রবি) জমিতে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ গাছের মোচা খড়ের রঙ ধারণ করলে ও বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে শুকনো আবহাওয়ায় মোচা সংগ্রহ করে ফেলতে হবে।
ভুট্টা (খরিফ) গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা চাষ করতে চাইলে এ মাসে বীজ বপন করতে হবে। খরিফ মৌসুমের জন্য ভুট্টার উন্নত জাতগুলো হলো বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৭ প্রভৃতি। শতাংশপ্রতি বীজ লাগবে ১০০-১২০ গ্রাম। উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটি দেশী জাতের পাট চাষের জন্য উপযুক্ত। দেশী পাটের অত্যন্ত জনপ্রিয় জাত হচ্ছে ডি-১৫৪। এ জাতটি ছাড়াও সিভিএল-১, সিভিই-৩ এবং সিসি-৪৫ জাতের চাষ করা যেতে পারে।
অন্যান্য মাঠ ফসল রবি ফসলের মধ্যে চিনা, কাউন, আলু, মিষ্টিআলু, চীনাবাদাম, পেঁয়াজ, রসুন যদি এখনো মাঠে থাকে তবে দেরি না করে সাবধানে তুলে ফেলতে হবে।
খেয়াল রাখতে হবে এ সময়ে বা সামান্য পরে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য পচনশীল ফসল তাড়াতাড়ি কেটে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।
শাকসবজি গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজ বপন বা চারা রোপণ শুরু করা প্রয়োজন। সবজি চাষে পর্যাপ্ত জৈবসার ব্যবহার করতে হবে। এ সময় গ্রীষ্মকালীন টমেটো, ঢেঁড়স, বেগুন, করলা, ঝিঙা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা, শসা, ওলকচু, পটোল, কাঁকরোল, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, লালশাক, পুঁইশাক এসব সবজি চাষ করতে পারেন। ধৈঞ্চা, শন, বরবটি, মাষকলাই, অড়হর, ছোলা এসবের গাছ দিয়ে সবুজ সার তৈরি করা যেতে পারে। গাছপালা এ সময় বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের পরিমাণ কমে আসে। আম গাছে হপার পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত কীটনাশক যেমন- সিমবুস/ফেনম/ ডেসিস/ফাইটার ২.৫ ইসি প্রভৃতি প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে হবে। আম গাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে কিন্তু ফুল ফোটার আগেই একবার এবং এর একমাস পর আর একবার প্রতি লিটার পানির সাথে ১.০ মিলি সিমবুস/ফেনম/ডেসিস /ফাইটার ২.৫ ইসি মিশিয়ে গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপাল ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করা প্রয়োজন। এ সময় আমে পাউডারি মিলডিউ ও এ্যান্থ্রাকনোজ রোগ দেখা দিতে পারে। টিল্ট, রিডোমিল গোল্ড, কানজা বা ডায়থেন এম ৪৫ অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। কলা বাগানের পার্শ্ব চারা, মরা পাতা কেটে দিতে হবে। পেঁপের চারা রোপণ করতে পারেন এ মাসে। এসময় থেকে ফলগাছে নিয়মিত কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও মাকড়নাশক স্প্রে করতে হবে। বাঁশঝাড়ে এ সময় নতুন চারা গজাবে। তাই বাঁশঝাড়ের গোড়ায় মাটি এবং গোবর বা আবর্জনা পচা সার দেওয়া প্রয়োজন।
লেখক: উপপরিচালক (গণযোগাযোগ), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা, টেলিফোন: ০২৫৫০২৮২২৭, মেইল: ddmc@ais.gov.bd














