কৃষি কথা
 করোনা অতিমারিতে খাদ্য নিরাপত্তায় ইঁদুর নিধন
করোনা অতিমারিতে খাদ্য নিরাপত্তায় ইঁদুর নিধন
করোনা অতিমারিতে খাদ্য নিরাপত্তায় ইঁদুর নিধন
মোঃ মেসবাহুল ইসলাম
করোনা অতিমারিতে খাদ্য নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশনা ‘এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে’- বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর সংস্থা ও কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সবার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় খাদ্যশস্যের নিবিড়তা বেড়েই চলেছে। স্বাধীনতার পর সর্বাধিক উন্নতি হয়েছে কৃষি সেক্টরে। দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান জিডিপির ১৩.০২ শতাংশ। করোনা সংক্রমণের কারণে যখন দেশের সবকিছু স্থবির, তখনও সচল কৃষির চাকা। দুঃসময়ে কৃষিই দেখাচ্ছে সম্ভাবনার পথ। এ বছর বোরো মৌসুমে বিগত বছরের সকল রেকর্ডকে ভেঙে ২ কোটি ৭ লাখ মেট্রিক টনের অধিক ফলন হয়েছে যার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকা। এমন কি কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্ব বাজার মন্দাভাব থাকলেও এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত কৃষিপণ্য রপ্তানি আয় ৯.১% বেড়ে ৮২৪ দশমিক ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। শুধু করোনাই নয় গত ৫০ বছরে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, শীত, খরা, তাপদাহসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা সামলিয়ে কৃষি বার বার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এসেছে বিস্ময়কর সাফল্য ও অভাবনীয় উন্নতি। কৃষি খাতে অন্তত দশটির অধিক ক্ষেত্রে বিশ্বে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। কৃষিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান পাট রপ্তানিতে ১ম, পাট ও কাঁঠাল উৎপাদনে ২য়, ধান ও সবজি উৎপাদনে ৩য়, আম ও আলু উৎপাদনে ৭ম, পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম, সামগ্রিক ফল উৎপাদনে বিশ্বে ২৮তম স্থানে বাংলাদেশ। দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণের পাশাপাশি পুষ্টিতেও বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত হচ্ছে ও পরিচিতি লাভ করছে। মুজিববর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের জোগান ও চাহিদা মিটিয়ে খাদ্য নিরাপত্তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখা।
বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতি থেকে উদ্বৃত্তে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দানাদার ফসল উৎপাদন ও রক্ষার যাবতীয় কৌশল সুচারুভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ফসল উৎপাদন ও রক্ষায় অন্যান্য বালাইয়ের সাথে ইঁদুরকেও গুরুত্ব দিয়ে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষা করতে ইঁদুরের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তবে এশিয়ার ধান উৎপাদনকারী প্রতিটি দেশে কৃষক, চালকল মালিক ও ব্যবসায়ীরা ইঁদুরকে গুরুত্বপূর্ণ বালাই হিসেবে বিবেচনা করে। শুধু ধান কর্তন থেকে গুদামে রাখা অবস্থায় ২-২৫ ভাগ পর্যন্ত ইঁদুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একটি ইঁদুর প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৭ গ্রাম খাদ্য খেয়ে থাকে। আর যা খায় তার ৪-৫ গুণ নষ্ট করে। সব ধরনের ইঁদুর বা ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের ছেদন (সদা বর্ধিষ্ণু) দাঁত রয়েছে। ক্ষয়ের মাধ্যমে দাঁতের এই বৃদ্ধিরোধ তথা আকার ও আকৃতি সঠিক রাখার জন্য সারা জীবন কিছু না কিছু কাটাকুটি করে থাকে। কাটাকুটি করে ইঁদুর যে শুধুমাত্র দানাদার ফসলের ক্ষতি করে তা নয়, অন্যান্য ফসল ও ফলমূল, আসবাবপত্রের ক্ষতি সাধন করে। বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতি এর হাত থেকে রেহাই পায় না। এরা মানুষ ও পশুপাখির প্রায় ৬০টিরও বেশি বিভিন্ন রোগজীবাণুর বাহক ও বিস্তারকারী। তাছাড়া ইঁদুর বিভিন্ন ধরনের স্থাপনাও কেটে নষ্ট করে। ক্ষতির দিক বিবেচনায় রেখে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৯৮৩ সাল থেকে জাতীয়ভাবে ইঁদুর নিধন অভিযান পরিচালনা করে আসছে। সে ধারাবাহিকতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ বছরেও ইঁদুর কর্তৃক ফসল ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস করার লক্ষ্যে ‘ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২১’ শুরু করতে যাচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থে, ইঁদুর মারি একসাথে।’ আশা করি সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ অভিযান সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে।
ইঁদুর বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্যের একটি প্রাণী। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ বাদে পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশে ইঁদুরের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিশ্বের অন্যতম ইঁদুর উপদ্রুত এবং বংশ বিস্তারকারী এলাকা হচ্ছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা। যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এখানকার উপকূলীয় লোনা ও মিঠাপানির এলাকাগুলো ইঁদুরের বংশ বিস্তারের জন্য বেশ অনুকূল। বাংলাদেশে ইঁদুরের প্রায় ২২টিরও অধিক ক্ষতিকর প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। এরা সব ধরনের পরিবেশে খাপখাওয়াতে পারে। উপযুক্ত এবং অনুকূল পরিবেশে একজোড়া প্রাপ্ত বয়স্ক ইঁদুর বছরে প্রায় ২০০০টি বাচ্চা জন্ম দিতে পারে। প্রতি ধানের মৌসুমে একটি স্ত্রী ইঁদুর অনুকূল পরিবেশে প্রায় ২৪টি বাচ্চা দিতে পারে। প্রতি বছর ইঁদুর ফসল ও কৃষকের শত্রু হিসেবে হানা দেয়। বাংলাদেশের অর্ধেক জমির ফসল ইঁদুরের আক্রমণের শিকার হয়। বাংলাদেশের প্রায় ১০ শতাংশ ধান, গম ইঁদুর খেয়ে ফেলে ও নষ্ট করে। গবেষণা থেকে জানা যায় তিন মাসের জন্য ধান গুদামে রাখা হলে ৫ থেকে ১০ ভাগ ইঁদুরের দ্বারা ক্ষতি হতে পারে। বাংলাদেশে গড়ে প্রতি কৃষক পরিবারে প্রতি বছরে ২০০ কেজি ধান ইঁদুরের দ্বারা নষ্ট হয়। বৃষ্টিনির্ভর ও সেচ সুবিধাযুক্ত ধানের জমিতে ফসল কাটার পূর্বে শতকরা ৫-১৭ ভাগ ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে ইঁদুরের আক্রমণে বছরে আমন ধান শতকরা ৫-৭ ভাগ, গম ৪-১২ ভাগ, গোলআলু ৫-৭ ভাগ, আনারস ৬-৯ ভাগ নষ্ট হয়। গড়ে মাঠ ফসলের ৫-৭% এবং গুদামজাত শস্য ৩-৫% ক্ষতি করে। ইঁদুর শতকরা ৭ থেকে ১০ ভাগ সেচ নালাও নষ্ট করে থাকে। সেটা ফসলের উৎপাদনের উপর প্রভাব ফেলে। ইঁদুর মুরগির খামারে গর্ত করে মুরগির ডিম ও ছোট বাচ্চা খেয়ে ফেলে। ইঁদুর বেড়িবাঁধ ও বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে গর্ত করে এবং মাটি সরিয়ে বাঁধ দুর্বল করে ফেলে। ফলে বাঁধ ভেঙে পানি দ্বারা প্লাবিত হয়ে বাড়িঘর, ফসলাদি ও গবাদিপশুর ক্ষতি সাধন করে, যার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক।
ইঁদুর দ্বারা ফসল ও সম্পদের যে ক্ষতি হয় তা নিয়ন্ত্রণ করা গেলে একদিকে যেমন- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে আবার অন্যদিকে আয়ও বাড়বে। সাধারণত ইঁদুর সবসময় দমন করা যায়। তবে ইঁদুর দমনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক। সে লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ইঁদুর নিধন অভিযান এসময় বাস্তবায়ন করে থাকে। এ অভিযানের মাধ্যমে গত ৫ বছরে (২০১৬-২০২০) গড়ে প্রায় ১০০৯৬২.৮ মেট্রিক টন আমন ফসল রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ২০২০ সালে প্রায় ১,১৯,৩৪,৪৬৩টি ইঁদুর নিধনের মাধ্যমে প্রায় ৮৯,৫০৮ মেট্রিক টন আমন ফসল রক্ষা করা হয়েছে। ইঁদুর দমন পদ্ধতি ফসলের রোগ ও পোকামাকড় দমন পদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্নতর। এরা সুকৌশলে দমনের ক্ষেত্র যেমন- বিষটোপ ও ফাঁদ এড়িয়ে চলে। এজন্য একক দমনের চেয়ে সমন্বিত দমন ব্যবস্থা অধিক কার্যকরী। মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর ইঁদুরের ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করেই উপযুক্ত দমন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে। সঠিক জ্ঞান এবং কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এর সংখ্যা লাগসইভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব।
করোনা সংকট দীর্ঘায়িত হলে করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হবে তা অনুমান করা কঠিন। তবে এখনই সতর্ক না হলে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে চলমান খাদ্য নিরাপত্তা বলয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে করোনা সংকটের সময় চলমান খাদ্য নিরাপত্তাকে ধরে রাখতে কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইঁদুর একক প্রচেষ্টায় নিধন করা একেবারেই সম্ভব নয়। বৈশ্বিক অতিমারি মোকাবিলার ন্যায় ইঁদুর নিধনেও সবার সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরিশেষে বলতে চাই, ‘সবাই সম্মিলিতভাবে ইঁদুর মারি, দেশের মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করি’।
সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। www.moa.gov.bd
 আখের জমিতে ইঁদুরের প্রতিবন্ধকতা
আখের জমিতে ইঁদুরের প্রতিবন্ধকতা
আখের জমিতে ইঁদুরের প্রতিবন্ধকতা
ড. মো. আমজাদ হোসেন১ ড. সমজিৎ কুমার পাল২ ড. মো. আতাউর রহমান৩
বাংলাদেশের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পোকামাকড়ের পাশাপাশি অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী দমন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাঠের ফসল উৎপাদন ও গুদামজাত শস্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইঁদুর এক বড় সমস্যা। ইঁদুর মাঠের শস্য খায়, কেটে নষ্ট করে এবং গর্তে জমা করে। আখ ফসলও অনিষ্টকারী ইঁদুরের আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না।
আখ বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলসমূহের মধ্যে অন্যতম, যা চিনি ও গুড় উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল। প্রতি বছর মিল এবং মিল বহির্ভূত এলাকায় প্রায় এক লক্ষ হেক্টর জমিতে আখের চাষ হয়ে থাকে। শুধু চিনি বা গুড় উৎপাদনই নয়, চিবিয়ে খাওয়ার জন্যও আখের ব্যাপক চাহিদা বিদ্যমান। আখ ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যার মধ্যে হেক্টরপ্রতি মাড়াইযোগ্য আখের স্বল্পতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সুষম সার প্রয়োগ না করা এবং রোগ ও পোকামাকড় অন্যতম। শুধু পোকামাকড়ের কারণেই প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২০% উৎপাদন এবং প্রায় ১৫% চিনি আহরণ হ্রাস পায়। আখ রোপণ থেকে শুরু করে কর্তন পর্যন্ত ১২-১৪ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। এই দীর্ঘ সময়ে অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী ইঁদুর আখের জমিতে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে কোন কোন বছর ইঁদুরের ব্যাপক আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় এবং আখের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়।
ইঁদুর Rodentia বর্গের Muridae পরিবারের অন্তর্গত যার বৈজ্ঞানিক নাম Bandicota bengalensis। বাংলাদেশে আখ উৎপাদনকারী সকল জেলায় মাঠের কালো ইঁদুরের ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে আখ ফসলে যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার শ্রীলংকা, ভারত, নেপাল, ভুটান, বার্মা, পাকিস্তান, থাইল্যান্ডসহ বহুদেশে ইঁদুরের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মাঠের বড় কালো ইঁদুর ধরা পড়লে উচ্চঃস্বরে ফোঁস এবং কর্কশ শব্দের মাঝামাঝি অদ্ভুত ধরনের শব্দ করে এবং একই সময়ে লোম বা পশম খাঁড়া করে হুমকি প্রদর্শন করে। এরা সার্বক্ষণিক কৌতূহলী এবং অনুসন্ধানকারী স্বভাবের। এরা সবাইকে শত্রুভাবে। ইঁদুরের স্মরণ শক্তি (৬০ দিন), ঘ্রাণ শক্তিও প্রখর, জিহ্বার স্বাদ মানুষের ন্যায় (তিতা, মিষ্টি) অনুভব করতে পারে কিন্তু রং শনাক্ত করতে পারে না। পৃষ্ঠদেশের পশম স্পষ্ট ঝাঁকড়া এবং পিঠ ও পাঁজর কালচে-বাদামি হয়। পেটের লোম ক্রিম অথবা হালকা হলুদ রঙের আভা থাকে। সামনের পা এবং পিছনের পা কালো লোম দ্বারা আবৃত থাকে। আখের মাঠে বয়স্ক ইঁদুরের ওজন পুরুষ ৩১০-৯১০ গ্রাম এবং স্ত্রী ৩৭৫-৭৫০ গ্রাম পাওয়া যায়।
আখের মাঠে ইঁদুরের উপস্থিতির লক্ষণসমূহ
আখ কেটে খাওয়া, নখ দিয়ে আখ আঁচড়ানো, আখ বেয়ে উপরে উঠা বা নামাসহ ক্ষণস্থায়ী চিচি শব্দ শোনা যায়। আখের ক্ষেতে চলাচলের রাস্তায় ইঁদুরের মল, নোংরা দাগ, পায়ের ছাপ, ইঁদুর যাতায়াতে পথ ইত্যাদি দ্বারা ইঁদুরের উপস্থিতি চিহ্নিত করা যায়। তাছাড়া ইঁদুরের বাসা বা গর্ত, আশেপাশে ছড়ানো ছিটানো খাবার, ইঁদুরের গন্ধ ইত্যাদি থেকেও ইঁদুরের উপস্থিতি বোঝা যায়। সারা বছরই আখক্ষেতের ইঁদুর দেখা যায় তবে মার্চ-আগস্ট মাসে এদের প্রকোপ বেড়ে যায়।
আখক্ষেতে ইঁদুরের ক্ষতির প্রকৃতি
আখ মাঠে লাগানোর পরে কিংবা চারা গজানো শুরু হলেই ইঁদুরের উপদ্রব লক্ষ করা যায়। আখের ক্ষেতে গর্ত, নালা ও প্রচুর পরিমাণে মাটি তুলে আখের চারার ব্যাপক ক্ষতি করে। মাটির নিচ থেকে আখের চারার গোড়া কেটে দেয় (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল)। মাটির নিচে ইঁদুরে কাটা আখ একটু এবড়ো-থেবড়ো হয় কিন্তু উইপোকা কাটা আখ দেখতে একেবারেই মসৃণ দেখা যায়। জুন-আগস্ট মাসে বৃষ্টি হলেই ইঁদুর আখের মাঠে কোন গর্ত না করেই মাটির ঠিক উপর থেকে আখ খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। গোড়ার দিক থেকে কোন আখের সম্পূর্ণ বা অর্ধেক গিরা খেয়ে ফেলে। ইঁদুরে ক্ষতিগ্রস্ত এসব আখ একটু বাতাস হলেই ভেঙে পড়ে। আখ হেলে পড়া রোধে বেঁধে দেওয়া হয়। বাঁধা অংশে ইঁদুর আশ্রয় নিয়ে মনের আনন্দে আখ খেয়ে প্রচুর ক্ষতি করে। মাঠের কালো ইঁদুর জমিতে গর্ত করে তাতে চারা গাছ কেটে জমা করে। আখের চারা একটু বড় হলেই তা কেটে দেয়। অর্ধপরিপক্ব আখ খেয়ে ক্ষত সৃষ্টি করেও প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। আখ ফসলে ইঁদুর প্রায় ৮-১০% ক্ষতি করে থাকে।
সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা
ইঁদুরের মৌলিক চাহিদা যেমন-খাদ্য, পানি ও বাসস্থান সীমিত করে এদের সংখ্যা কমানো যায়। এতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি, ইঁদুর বাহিত রোগ ও পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমানো সম্ভব। ইঁদুর দমনের উপযুক্ত সময় হলো আখের জমিতে সেচ দেওয়ার দিন। আখের জমির চারপাশের আইল উঠায়ে দিয়ে প্লাস্টিকের পাইপ বা রড দ্বারা আইল তৈরি করলে ইঁদুর বাসা বাঁধার জায়গা পাবে না। এভাবে সবাই মিলে আখের জমিতে ইঁদুর আসা নিরুৎসাহিত করলে একরপ্রতি আখের উৎপাদন খরচ ৩,৫০০ টাকা কমানো সম্ভব হবে। এ ছাড়াও সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইঁদুর নিধন করা সম্ভব।
১মহাপরিচালক, বিএসআরআই, ২পরিচালক (গবেষণা), বিএসআরআই, ৩ সিএসও এবং প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএসআরআই।
ফোন : ০৭৩২৫৬৫৩৬২৮, ই-মেইল : dg-bsri.gov.bd
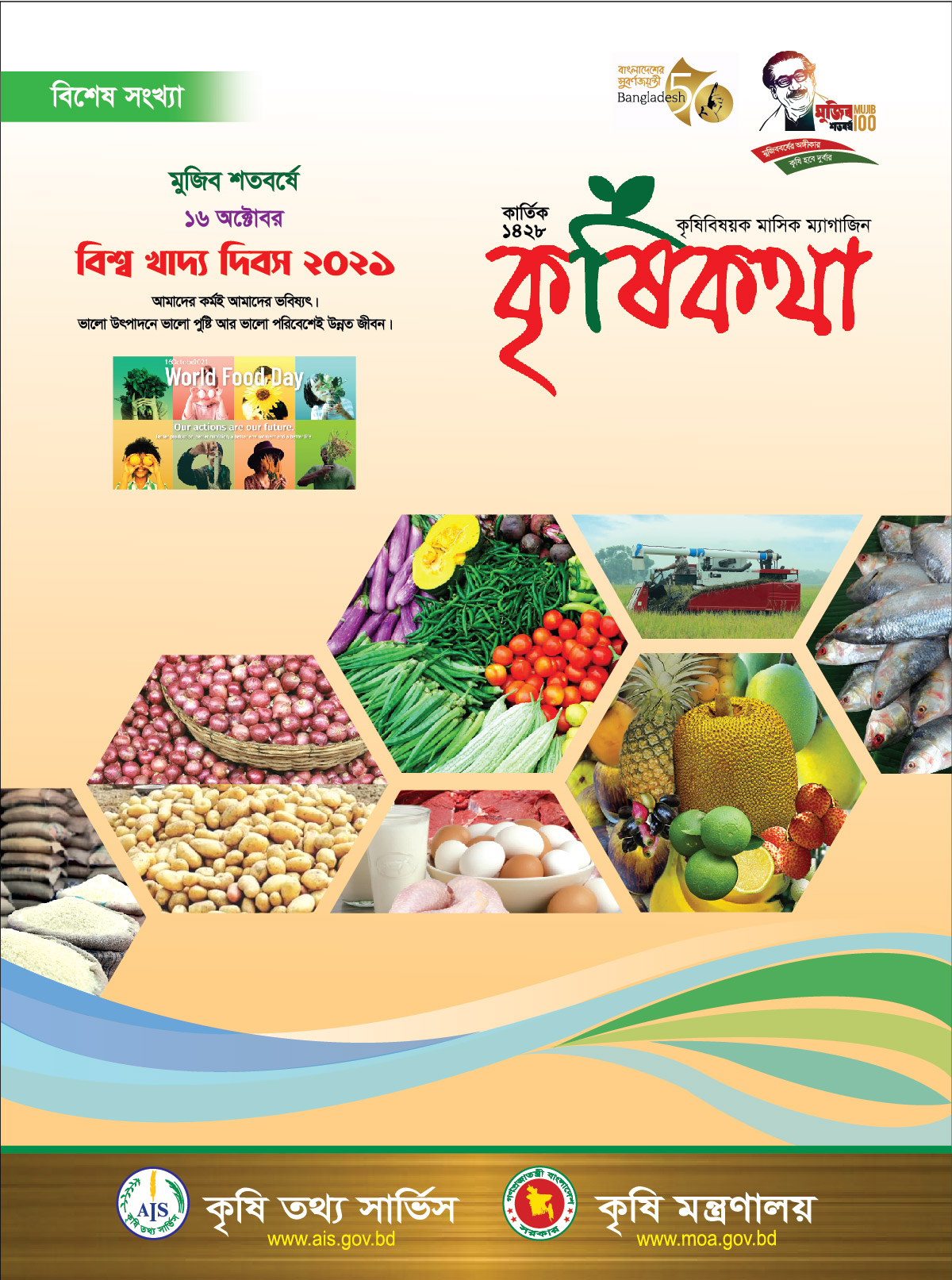 ভাতের মাধ্যমে জিঙ্কের জোগান
ভাতের মাধ্যমে জিঙ্কের জোগান
ভাতের মাধ্যমে জিঙ্কের জোগান
ড. সুরজিত সাহা রায়
বাংলাদেশ একটি ঘনবসতি দেশ। ছোট এ দেশটির জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি। ২০১৮ সালের জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ২১.৮ শতাংশ এবং হতদরিদ্রের হার ১২.৯ শতাংশ। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার ৩১ শতাংশ (বিডিএইচএস, ২০১৯)। দানাদার শস্যে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও অপুষ্টি জনিত অদৃশ্য ক্ষুধায় (ঐরফফবহ ঐঁহমবৎ) ভুগছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী। শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি জনসংখ্যার সুষম খাবারের ঘাটতি রয়েছে। ভিটামিন ‘এ’, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক এবং আয়রনের অভাব উল্লেখযোগ্য। পাঁচ বছরের কম বয়সি শতকরা ৪১ ভাগ শিশু জিঙ্কের অভাবে ভুগছে, শতকরা প্রায় ৩৬.৪ ভাগ শিশু খর্বকায়। ১৫-১৯ বছর বয়সি মেয়েদের শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ অপুষ্টির কারণে বেটে বা লম্বায় কম। অপুষ্টির ঘাটতি মেটাতে না পারলে স্থূলতা এবং অসংক্রামক রোগের প্রবণতা বাড়তে পারে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহের সাথে মিল রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবসান, ক্ষুধার অবসান ও উন্নত পুষ্টিঅর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। এ দেশের মানুষের ৭৭ শতাংশ ক্যালরি ও ৫০ শতাংশ প্রোটিন আসে ভাত থেকে। প্রতিদিন গড়ে মাথাপিছু ৩৬৭ গ্রাম চালের ভাত আমরা খেয়ে থাকি। ভাত বা দানাদার খাদ্য মোট খাদ্যশক্তির ৬০ শতাংশের বেশি দখল করে আছে। অর্থাৎ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির অধিকাংশ ক্যালরি, প্রোটিন ও খনিজ উপাদান আসে ভাত থেকে। চালে মোটামুটি ৮০% শর্করা, ৭.১% প্রোটিন, ০.৬৬% চর্বি, ০.১২% চিনি, ১.৩% আঁশ থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম চালে ১১৫ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম, ১১৫ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ২৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ২৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৪.৩১ মিলিগ্রাম আয়রন পাওয়া যায় (ইউএসডিএ, ২০১২)।
মানবদেহের জন্য জিঙ্ক খুব প্রয়োজনীয় একটি খনিজ উপাদান। মানবদেহের ৩০০টি এনজাইমের সাথে জিঙ্ক সরাসরি অংশগ্রহণ করে যেগুলো দেহের অনেক বিপাকীয় কাজে অংশ নেয়। জিঙ্কের অভাবে মুখের রুচি নষ্ট হয়, স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয়, ওজন কমে যায় অথবা মুটিয়ে যায়, চুল পড়ে যায়, হজমে সমস্যা হয়, জটিল ধরনের অবসাদগ্রস্ততা দেখা দেয়, বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়, হরমোনের সমস্যা হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, মনোযোগ ও স্মরণশক্তি কমে যায়, ত্বকের ক্ষত সারতে দেরি হয় এবং স্নায়ুবিক দুর্বলতা দেখা দেয়। মানব শরীর জিঙ্ক সংরক্ষণ করে রাখতে পারে না বিধায় প্রতিদিনই একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের ১১ মিলিগ্রাম এবং নারীদের ৮ মিলিগ্রাম জিঙ্ক গ্রহণ করতে হয়। গর্ভবতী মায়েদের দৈনিক ১১ মিলিগ্রাম, দুগ্ধদানকারী মায়েদের ১২ মিলিগ্রাম জিঙ্ক প্রয়োজন এবং শিশুদের দৈনিক চাহিদা ৩-৫ মিলিগ্রাম জিঙ্ক।
লাল মাংস জিঙ্কের ভালো উৎস। ১০০ গ্রাম গরুর মাংসে ৪.৮ মিলিগ্রাম জিঙ্ক থাকে, যা দৈনিক চাহিদার শতকরা ৪৪ ভাগ মেটায়। ১০০ গ্রাম ছোট চিংড়ি দৈনিক চাহিদার শতকরা ১৪ ভাগ মেটায়। ১০০ গ্রাম রান্না করা ডাল মেটাতে পারে চাহিদার মাত্র ১২%। বাদামে প্রচুর জিঙ্ক আছে। ২৮ গ্রাম বাদাম চাহিদার ১৫%, পনির ২৮%, এক কাপ দুধ ৯% এবং একটি ডিম শতকরা ৫ ভাগ জিঙ্কের চাহিদা মেটাতে পারে। মাংস, ডিম, দুধ, পনির, বাদাম, চিংড়ি দামি খাবার হওয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে। লাল মাংস ও চিংড়িতে কোলেস্টেরল বেশি থাকায় বয়স্ক জনগণ সাধারণত ডাক্তারের পরামর্শে এসব খাবার এড়িয়ে চলেন।
বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার “খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্টির জোগান” স্লোগানকে সামনে রেখে আমাদের বিজ্ঞানীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। যার ফলে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ৬টি জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধানের জাত, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১টি ধানের জাত এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১টি জিঙ্কসমৃদ্ধ গমের জাত উদ্ভাবন করেছেন। উদ্ভাবিত জিঙ্কসমৃদ্ধ জাতগুলোতে প্রতি কেজি চালে ২২ থেকে ২৭ মিলিগ্রাম জিঙ্ক থাকে যেখানে সাধারণ চালে থাকে মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম জিঙ্ক। প্রতিদিন ৪০০ গ্রাম জিঙ্কসমৃদ্ধ চালের ভাত খেলে একজন ভোক্তা প্রতিদিন ৯-১০ মিলিগ্রাম জিঙ্ক পেতে পারে, যা দৈনিক চাহিদার প্রায় সমান।
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৩ সালে বিশ্বের সর্বপ্রথম জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত ব্রি ধান৬২ উদ্ভাবন করে। এরপর একে একে ব্রি ধান৬৪, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮৪ এবং সর্বশেষ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে উচ্চ জিঙ্কসমৃদ্ধ ব্রি ধান১০০ অবমুক্ত করে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জিঙ্কসমৃদ্ধ বিনাধান-২০ নামের ধানের জাত এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৭ সনে বারি গম৩৩ উদ্ভাবন করেছে।
আমন মৌসুমে আবাদের জন্য তিনটি জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। ব্রি ধান৬২ জিংক এর পরিমাণ প্রতি কেজি চালে ১৯ মিলিগ্রাম। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৩.৫-৪.৫ টন। ব্রি ধান ৭২ জিঙ্কের পরিমাণ প্রতি কেজিতে ২২.৮ মিলিগ্রাম। গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৫.৭ টন হলেও উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৭.৫ মেট্রিক টন হতে পারে। বিনাধান-২০ জিঙ্কের পরিমাণ প্রতি কেজিতে ২৬ মিলিগ্রাম। গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৬.১ টন হলেও ৬.৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।
বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য জিঙ্কসমৃদ্ধ চারটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রতি কেজিতে ২৪ মিলিগ্রাম জিঙ্কসমৃদ্ধ ব্রি ধান৬৪ হেক্টরপ্রতি ৬.০ থেকে ৬.৫ টন ফলন দিতে পারে। ব্রি ধান৭৪ জাতটির প্রতি কেজিতে জিঙ্কের পরিমাণ ২৪.২ মিলিগ্রাম আছে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৭.১ টন হলেও উপযুক্ত পরিচর্যায় ৮.৩ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। ব্রি ধান৮৪ জাতটি প্রতি কেজি চালে জিঙ্ক আছে ২৭.৬ মিলিগ্রাম, ১০.১ মিলিগ্রাম আয়রন ও শতকরা ৯.৭ ভাগ প্রোটিন আছে। হেক্টরপ্রতি ফলন ৬.০-৬.৫ টন হলেও উপযুক্ত পরিবেশে ৮ টন ফলন দিতে সক্ষম। নাজিরশাইল চালের ন্যায় দানাবিশিষ্ট ব্রি ধান ১০০ জাতটির প্রতি কেজি চালে জিঙ্কের পরিমাণ ২৫.৭ মিলিগ্রাম। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৭.৭ টন হলেও উপযুক্ত পরিবেশে ৮.৮ টন ফলন দিতে সক্ষম।
বারি গম৩৩ গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩.৯৫ টন। ধানের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি জিংকসমৃদ্ধ অর্থাৎ, প্রতি কেজি গমে ৫০-৫৫ মিলিগ্রাম জিঙ্ক আছে।
বাংলাদেশে গত বছর অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৭৪ ও ব্রি ধান৮৪ এর আবাদ হয়েছে যথাক্রমে ৫৭,২৪৫ ও ২,৮২৯ হেক্টর জমিতে। এ বছর এ জাত দুটির আবাদ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহত্তর বরিশাল জেলার লোকেরা মোটা চাল পছন্দ করে বিধায় ঐ অঞ্চলে ব্রি ধান৭৪ এর আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যান্য জেলায় অধিক ফলন, রোগবালাই কম ও জীবনকাল তুলনামূলক কম হওয়ায় কৃষকদের মাঝে এ জাতটি আবাদে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিঙ্কসমৃদ্ধ হওয়ায় এ জাতের চালের ভাত খাওয়ার ব্যাপারে কুমিল্লাসহ বিভিন্ন জেলার কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে। কৃষক তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ধান সিদ্ধ করে ভ্যানচালিত কলে চাল করে নিজেরা খায় এবং অতিরিক্ত চাল স্থানীয় বাজারে চাল বিক্রি করে। কিন্তু বাজারে জিঙ্কসমৃদ্ধ কোন জাতের চাল পাওয়া যায় না।
চালের বাজার মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে চালকলের মালিকগণ। চালকল বলতে বুঝানো হচ্ছে অটো রাইস মিলকে। কৃষকের উৎপাদিত ধানকে মোটা ও চিকন দুটো গ্রেড করে তারা চাল করে। শহরের বাজারে যেসব চাল পাওয়া যায় তা মিনিকেট, নাজির, আটাশ মিনিকেট, চিনিগুঁড়া, বাসমতি, জিরা, স্বর্ণা, ইত্যাদি নামে পরিচিত। মিনিকেট ও নাজির চালের বাজারমূল্য বেশি। চিনিগুঁড়া চাল পোলাওয়ের চাল। প্রকৃতপক্ষে, মিনিকেট নামের কোনো ধানের জাত নেই। নাজিরশাইল আমন মৌসুমে খুব সামান্য চাষ হয় এর ফলন কম হওয়ার কারণে ব্রি ধান২৮ বা মাঝারি মোটা জাতের চালকে পলিশ করে তথা ছেঁটে মিনিকেট করা হয়। ব্রি ধান৪৯ জাতের চালকে পলিশ করে নাজির নামে বিক্রি করা হয়। একইভাবে ব্রি ধান৩৪ কে চিনিগুঁড়া এবং ব্রি ধান৫০ কে বাসমতি চাল নামে বাজারে বিক্রি করা হয়।
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ^বিদ্যালয় এ পর্যন্ত শতাধিক উচ্চফলনশীল ধানের জাত ও বেশ কয়েকটি হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)সহ বিভিন্ন বেসরকারি বীজ কোম্পানি বেশ কয়েকটি হাইব্রিড ধানের জাত বাজারজাত করে এবং কিছু হাইব্রিড জাতের বীজ এদেশেই উৎপাদন করে। কৃষকগণ বিভিন্ন নামের স্থানীয় জাত এবং ভারত থেকে আসা বিভিন্ন জাত চাষ করে থাকে। সবমিলিয়ে এদেশে কয়েক শত জাতের ধানের আবাদ হয়ে থাকে। একেকটা জাতের একেক রকম স্বাদ, বর্ণ ও বৈশিষ্ট্য। উৎপাদনকারী কৃষক নিজেরা এসব আবাদ করে এবং নিজের পছন্দের জাতের চাল খেতে পারলেও বাজারের সাধারণ ভোক্তারা এ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
যখন ঢেঁকিছাঁটা চাল এবং ছোট ছোট বয়লারের চাল বাজারে আসতো তখন চালের জাতের বৈচিত্র্য ছিল। এখন অটো রাইস মিল হওয়ায় সেটা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ একটা বড় অটো রাইস মিলে প্রতিদিন প্রায় ৯৬ মেট্রিক টন ধান প্রয়োজন। চক্র পূরণের জন্য কমপক্ষে ৭০০ মেট্রিক টন ধান না হলে মিলারদের পক্ষে সেই জাতের চাল করা সম্ভব না। মিলারগণ ফড়িয়া বা সরবরাহকারী ব্যবসায়ীদের থেকে ধান সংগ্রহ করেন। ফড়িয়াদের দ্রুত ধান সংগ্রহ করে মিলারদের সরবরাহ করতে হয় বলে তারা এতো জাত না বেছে সহজভাবে মোটা, মাঝারি মোটা, চিকন, ইত্যাদিতে গ্রেড করে মিলারদের সরবরাহ করে। এরপর এসব জাত পলিশ করা, সাদা করা, সর্টিং করা ইত্যাদি করে মিনিকেট বা নাজির নামে বাজারে বিক্রি করা হয়। ভোক্তারাও এসব জাতের চাল বেশি দামে কিনে দুইভাবে প্রতারিত হচ্ছেন। প্রথমত বেশি দাম ও দ্বিতীয়ত ভিটামিন ও খনিজহীন শর্করা বিশিষ্ট চাল। চাল ছাটাই ও পলিশ করলে এর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে যায়। মিলাররা ছাঁটাইকৃত চাল বেশি দামে বিক্রি করতে পারে এবং উপজাত হিসেবে যে কুঁড়া পায় সেটাও মাছের খাদ্য হিসেবে বাজারে ভালো দামে বিক্রি হয়। ভোক্তারা না বুঝে বা নিরুপায় হয়ে অধিক দামে এসব চালের নামে আবর্জনা কিনে খাচ্ছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের জাতের চাল বাজারে ভিন্ন নামে বিক্রি হওয়ায় তাদের পরিশ্রমের স্বীকৃতিও পাচ্ছে না। সচেতন ভোক্তারা বাজারে তাদের চাহিদা মতো পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ চাল খেতে পারছে না।
এ সব সমস্যার আশু সমাধান দরকার। মিলার ও ভোক্তা উভয়ের এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। তাই সবার আগে ভোক্তাদের ধানের জাত ও খাদ্যপুষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। এ ছাড়াও, ভিন্ন নামে চাল বাজারে বিক্রি করাকে প্রতারণার দায়ে দোষী করে অসাধু ব্যবসায়ীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। ফড়িয়াদের সততার সাথে নির্দিষ্ট জাতের ধান ক্রয় করে মিলারদের সরবরাহ করতে হবে। কৃষকদেরও যেসব জাতের ফলন ও বাজারমূল্য বেশি সেসব জাতের আবাদ বাড়াতে হবে অর্থাৎ বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করতে হবে। কৃষি শ্রমিকের খরচ সাশ্রয় ও দ্রুততার সাথে কম সময়ে আবাদ ও কর্তন কাজে কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। সমকালীন চাষাবাদ ও সমবায়ের মাধ্যমে আবাদ করতে হবে। এর ফলে, ধানের ফলন বৃদ্ধি, সফলতার সাথে রোগবালাই-পোকামাকড় দমন, কৃষকের প্রযুক্তি জ্ঞান বৃদ্ধি, বাজারমূল্য প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে কৃষক লাভবান হতে পারবে। যেমন : কোন উপজেলায় ৫০০ হেক্টর জমিতে ব্রি ধান৭৪ এর আবাদ হলে ৩০০০ টন ধান উৎপাদন হবে; ফড়িয়া বা মিলারগণ এসব কৃষক থেকে খুব সহজেই ২০০০ টন ব্রি ধান৭৪ ধান সংগ্রহ করতে পারবে এবং সেই চালটা ব্রি ধান৭৪ নামে বাজারে বিক্রি করতে পারবে। সেক্ষেত্রে, ফড়িয়াকে ধানের জাত ও ঐ আবাদকারী কৃষককে চিনতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত উপসহকারী কৃষি অফিসারগণ এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে। সাধারণ ভোক্তারা জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের চাল খেয়ে জিঙ্কের অপুষ্টি দূর করতে পারবে। বরিশাল বিভাগের জনগণ মোটা চাল খেতে পছন্দ করে, তারা ব্রি ধান৭৪ এর চাল খেতে পারবে এবং যারা চিকন ও লাল চালের ভাত খেতে পছন্দ করে তারা ব্রি ধান৮৪ অথবা ব্রি ধান১০০ জাতের চাল খেয়ে দেহের জিঙ্কের চাহিদা অনেকটাই মেটাতে পারবে।
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। মোবাইল : ০১৭১১৯৬৯৩১৮, ই-মেইল :surajit@dae.gov.bd
 জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২১
জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২১
জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২১
ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা
বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত। গ্রামের উন্নয়নের কথা বলতে গেলে প্রথমে আসে কৃষি উন্নয়ন। পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাতের উন্নয়ন। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জমি হ্রাসের প্রেক্ষাপটে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানের জন্য এবং কৃষি ও কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান কৃষক ও কৃষিবান্ধব সরকার গ্রহণ করেছে বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর ফলে দেশ আজ দানাজাতীয় শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সে সাথে খাদ্যশস্য রপ্তানিও করা হচ্ছে। ‘এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টায় শস্যের নিবিড়তা বেড়েই চলেছে বিধায় জমিতে প্রায় সবসময় ফসল বিদ্যমান থাকে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রয়োজন কৃষি উৎপাদনে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ অধিক ফলন নিশ্চিত করা আর উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বালাইজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা। বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত বিভিন্ন রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ এবং ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে ফসল ঘরে তোলাই কৃষকের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দেখা যায় কৃষকের উৎপাদিত ফসলের একটা বড় অংশ ইঁদুর দ্বারা নষ্ট হয়। ইঁদুর যে পরিমাণ খাবার খায় তার চেয়ে বেশি কেটেকুটে নষ্ট করে। এক জোড়া ইঁদুর গর্তে ২০ কেজির বেশি খাদ্য জমা করে, ৫০ কেজি গোলাজাত শস্য নষ্ট করে। ইঁদুর মাঠ থেকে শুরু করে ফসল কর্তনের পরেও গুদামজাত অবস্থায় বা গোলায় তোলার পরও ক্ষতি করে। সুতরাং ইঁদুর সর্বাবস্থায় আমাদের ক্ষতি করতে সক্ষম। ইঁদুরের বিচরণ ক্ষেত্র বাড়ির শোবার ঘর পর্যন্ত বিস্তৃত। এরা মাঠের ফসল, গুদামজাত শস্য, ফল, শাকসবজি, সংরক্ষিত বীজ ছাড়াও আমাদের বাসাবাড়ির আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র, কাগজ, লেপ-তোষক ইত্যাদি কাটাকুটি করে আমাদের প্রচুর ক্ষতি করে। এর পাশাপাশি বাঁধ, রেললাইন, জাহাজ, বন্দর, অফিস, মাতৃসদন, সেচের নালাসহ সর্বত্র ইঁদুরের বিচরণ রয়েছে। এরা মানুষ ও পশুপাখির মধ্যে প্লেগ, জন্ডিস, টাইফয়েড, চর্মরোগ, আমাশয়, জ্বর, কৃমিসহ প্রায় ৬০ প্রকার রোগজীবাণুর বাহক ও বিস্তারকারী। বাংলাদেশে ইঁদুরের আক্রমণে বছরে আমন ধানের শতকরা ৫-৭ ভাগ, গম ৪-১২ ভাগ, গোলআলু ৫-৭ ভাগ, আনারস ৬-৯ ভাগ নষ্ট করে। গড়ে মাঠ ফসলের ৫-৭% এবং গুদামজাত শস্য ৩-৫% ক্ষতি করে। ইঁদুর বছরে প্রায় ৭ লক্ষ মে.টন খাদ্যশস্য নষ্ট করে।
ইঁদুর স্তন্যপায়ী, সর্বভুক ও নিশাচর প্রাণী। ফসলের জন্য ক্ষতিকর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে ইঁদুর মানুষের প্রধান শত্রু। বাংলাদেশে প্রায় ১১ প্রজাতির ইঁদুর আছে। ইঁদুরের সামনের দাঁত জন্ম থেকে বাড়তে থাকে। ছেদন দন্তের বৃদ্ধি রোধ করার জন্যে এরা কাটাকাটি করে। ইঁদুর বছরে ৬-৮ বার এবং প্রত্যেক বার ৩-১৩টি বাচ্চা জন্ম দেয়। বাচ্চা জন্ম দেয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইঁদুর পুনরায় গর্ভধারণ করতে পারে। জন্ম গ্রহণের পর তিন মাস বয়সে গর্ভধারণ করতে পারে। একজোড়া ইঁদুর বছরে প্রায় ২০০০টি বংশধর সৃষ্টি করতে পারে।
ইঁদুরের বিভিন্ন প্রজাতি : মাঠের বড় কালো ইঁদুর, মাঠের কালো ইঁদুর, বাঁশের ইঁদুর, গেছো ইঁদুুর, হিমালয়ান ইঁদুুর, ঘরের বাত্তি ইঁদুুর, মাঠের ছোট নেংটি ইঁদুুর, সাদা দাঁত বিশিষ্ট ইঁদুুর। ইঁদুরের সমস্যা গ্রামের লোকজন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না, সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় কোন পদ্ধতিও পর্যাপ্ত নয়। গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর ইঁদুর যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা সঠিকভাবে বুঝে উপযুক্ত দমন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে পারাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৯৮৩ সাল থেকে ইঁদুর নিধন অভিযান পরিচালনা করে আসছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ৫ বছরে ইঁদুর নিধন অভিযান কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ইঁদুরের আক্রমণ থেকে রক্ষাকৃত আমন ফসলের পরিমাণ সারণি দ্রষ্টব্য।
বর্তমানে সারাবিশ্বে পোলট্রি শিল্প ইঁদুর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এবং পোলট্রি উৎপাদনকারীদের অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। ইঁদুর মুরগির খামারে গর্ত করে মুরগির ডিম ও ছোট বাচ্চা খেয়ে ফেলে। পোলট্রি শিল্পে ইঁদুর দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষতির দিকে লক্ষ্য রেখে খামারিদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে যাতে সমন্বিতভাবে ইঁদুর দমনে অংশগ্রহণ করে এবং খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
সারণি : ইঁদুর নিধন অভিযান কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলাফল॥
| বছর | প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | নিধনকৃত ইঁদুরের সংখ্যা | ইঁদুরের আক্রমণ থেকে রক্ষাকৃত আমন ফসলের পরিমাণ (মে. টন) |
| ২০১৬ | ৬০,২৬,৬৯১ | ১,১৮,৪৫,৯০৪ | ৮৮,৮৪৪ |
| ২০১৭ | ৬৪,০০,০১২ | ১,২০,৫১,৪১৬ | ৯০,৩৮৫ |
| ২০১৮ | ৫৬,৮৩,৩৬৫ | ১,৬৬,৮৭,২৩৪ | ১,২৫,১৫৪ |
| ২০১৯ | ৫৫,১৩,৪৪৫ | ১,৪৭,৮৯,৭৮৫ | ১,১০,৯২৩ |
| ২০২০ | ৩১,৪৮,৪৮৫ | ১,১৯,৩৪,৪৬৩ | ৮৯,৫০৮ |
ইঁদুুর নিধন অভিযান ২০২১ এর উদ্দেশ্য
ইঁদুর খুব চালাক প্রাণী। ইঁদুরের শ্রবণ ও ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত প্রকট। ইঁদুর ব্যবস্থাপনা একার পক্ষে সম্ভব নয়। সকলের সমন্বয়ে সমন্বিতভাবে দমন ব্যবস্থা করতে হবে। ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২১ উদ্যাপনের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে (১) কৃষক-কৃষানি, ছাত্রছাত্রী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আইপিএম/আইসিএম এসব ক্লাবের সদস্য, সিআইজি, ডিএই এর বিভিন্ন কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোসহ সর্বস্তরের জনগণকে ইঁদুর দমনে উদ্বুদ্ধ করা; (২) ইঁদুর দমনের জৈবিক ব্যবস্থাপনাসহ লাগসই প্রযুক্তি কৃষি কর্মীদের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো; (৩) ঘরবাড়ি, দোকানপাট, শিল্পকারখানা ও হাঁস-মুরগির খামার ইঁদুরমুক্ত রাখার জন্য সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা; (৪) আমন ফসল ও অন্যান্য মাঠ ফসলে ইঁদুরের ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে রাখা; (৫) গভীর ও অগভীর নলকূপের সেচের নালার ইঁদুর মেরে পানির অপচয় রোধ করা; (৬) রাস্তাঘাট ও বাঁধের ইঁদুর নিধনের জন্য সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা; (৭) ইঁদুরবাহিত রোগের বিস্তার রোধ করা এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা; (৮) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে গণযোগাযোগ বিশেষ করে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যাপারে জোর দেয়া।
ইঁদুঁর নিধন অভিযান ২০২১ এর উদ্বোধন এবং পুরস্কার প্রদান
জাতীয় পর্যায়ে ইঁদুর নিধন অভিযানের উদ্বোধন অক্টোবর মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিচালিত হতে যাচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য ‘জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থে, ইঁদুর মারি একসাথে।’ বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে এবং ইঁদুর নিধনে পুরস্কার প্রদান সম্পর্কে পরবর্তী নির্দেশনা মোতাবেক অনুসরণ করা হবে। জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার, লিফলেট, পুস্তিকা প্রস্তুত করে অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় প্রেরণ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
ইঁদুর একটি নীরব ধ্বংসকারী স্তন্যপায়ী প্রাণী। ইঁদুর প্রাণীটি ছোট হলেও ক্ষতির ব্যাপকতা অনেক। এরা যে কোনো খাদ্য খেয়ে বাঁচতে পারে। যে কোনো পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে। অল্প বয়সে বাচ্চা দিতে পারে। ইঁদুর একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রাণী। একটি মাত্র পদ্ধতি দ্বারা ইঁদুর দমন করা বাস্তবে সম্ভব নয়। ইঁদুর দমন পদ্ধতি সঠিক স্থানে, সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ইঁদুর মারা বিষ খুবই মারাত্মক। বিষ প্রয়োগের সময় পানাহার বা ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে। কাজের শেষে হাত মুখ এবং শরীরের অনাবৃত অংশ ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। মানুষ বা পশু খাদ্যের সাথে ইঁদুরের বিষ পরিবহন বা গুদামজাত করা এবং বিষের খালি প্যাকেট অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বাংলাদেশের কৃষকগণ ১০-১২ ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করে ইঁদুর ধরে থাকেন। যেমন- বাঁশের তৈরি ফাঁদ, কাঠের তৈরি ফাঁদ, ইঁদুর ধরার লোহার তৈরি কল ইত্যাদি। এ ছাড়া বাসাবাড়িতে ইঁদুর ধরার জন্য গ্লুবোর্ড ব্যবহার করে ছোট বড় ৫-১০টি ইঁদুর মারা যায়। জুম ফসল রক্ষার জন্য বাঁশের বেড়া দিয়ে বাঁশের ফাঁদ পাতা হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে জোয়ারের সময় টেঁটা দিয়ে ইঁদুর মারা যায়। জোয়ারে ধান ফসল ডুবে গেলে ইঁদুর কচুরিপানা, হোগলা গাছে ও মাঠে আশ্রয় নিলে তখন সম্মিলিতভাবে ইঁদুর দমন করা উচিত। ইঁদুর মারার প্রকৃত বিষ হচ্ছে জিংক ফসফাইড। কৃষক এ বিষ বিভিন্ন খাদ্যের সাথে মিশিয়ে বিষটোপ তৈরি করেন। খাদ্য হিসেবে শুঁটকি, চিংড়ি, শামুক, কাঁকড়া ভালো কাজ করে। বাজারে ল্যানির্যাট ও ব্রমাপয়েন্ট পাওয়া যায়, যা ভালো কাজ করে। ৩ গ্রাম ওজনের অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইডের গ্যাসবড়ি ইঁদুরের গর্তে দিয়ে ভালোভাবেই ইঁদুর দমন করা যায়। নিজের বাড়ির ইঁদুর নিজেকেই মারতে হবে এটি বাস্তব কথা কিন্তু একা ইঁদুর দমন করা সম্ভব নয়। ইঁদুর সমস্যা একটি সামাজিক সমস্যা। সমাজের সবার সহযোগিতা ছাড়া ইঁদুর দমন সম্ভব নয়। ইঁদুর দমন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ দিয়ে সহায়তা ও ইঁদুর দমন কর্মসূচির জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন।
পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। ফোন : ৯১৩১২৯৫, ই-মেইল: dppw@dae.gov.bd
 সমন্বিত ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা (আশ্বিন ১৪২৮)
সমন্বিত ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা (আশ্বিন ১৪২৮)
সমন্বিত ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা
মো: মোসাদ্দেক হোসেন১, ড. শেখ শামিউল হক২
ইঁদুর সবার পরিচিত স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী প্রাণী, যা প্রতিনিয়তই মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করছে। ইহা মাঠে ও গুদামে আমাদের বিভিন্ন ফসল যেমন- ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, বিভিন্ন ফল ও শাকসবজির ক্ষতি করছে, গুদামজাত শস্যে মলমূত্র ও লোম সংমিশ্রণ করছে, বিভিন্ন অবকাঠামোর ক্ষতিসাধন করছে। পোকামাকড়ের তুলনায় ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করা আপাতত খুব কঠিন মনে হলেও অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় সঠিক জ্ঞান এবং কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ইহার সংখ্যা লাগসইভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর ইঁদুর কি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা সঠিকভাবে বুঝে উপযুক্ত দমন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে পারাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা
যে কোন সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (IPM) মূলনীতি হলো বালাই বা শত্রুকে জানা। সব ইঁদুর এক প্রজাতিভুক্ত নয়। প্রতিটি প্রজাতির জন্মহার, বাসস্থান এবং আচরণ ভিন্ন হয়। এই ভিন্নতার কারণগুলো ক্ষতির মাত্রা এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। যেমন- কিছু ইঁদুর গাছ বা বাসাবাড়ির ছাদের উঁচুস্থানে বাস করে, অন্যরা জমির গর্তে বা মাটির দেয়ালের গর্তে বাস করে। ইঁদুর দমন কার্যক্রমকে কার্যকরী করতে হলে ইঁদুর কোথায় বাস করে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ । ইঁদুর সহজেই যে কোনো পরিবেশে নিজকে খাপখাইয়ে নিতে পারে। কোন একটি ইঁদুর প্রজাতি প্রতিকূল পরিবেশে ভিন্ন খাদ্য বা বাসস্থানে বেঁচে থাকতে পারে। তাই ইঁদুর কখন, কোথায়, কোন ফসল, গোলাজাত খাদ্য এবং স্বাস্থ্যের কি ক্ষতি করে তা জানা থাকলে সমন্বিত উপায়ে স্বল্প খরচে এ সমস্ত সৃষ্ট সমস্যার সমাধান সম্ভব। ইঁদুরের ক্ষয়ক্ষতির ধরন, এর ব্যাপকতা ও দমন প্রক্রিয়া অন্যান্য বালাই থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও কৌশলগত। তাই স্থান কাল পাত্রভেদে কৌশলের সঠিক ও সমন্বিত দমন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ইঁদুর দমন করতে হবে। তবে ইঁদুরকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন। এককভাবে ইঁদুর দমন ফলত খুব বেশি কার্যকরী হয় না। সবাই মিলে একযোগে বেশি জায়গার ইঁদুর মারলে ফসল রক্ষা পায় ও ইঁদুরের সংখ্যা পরবর্তীতে বাড়তে পারে না। এজন্যই প্রতি বছর সরকারিভাবে ইঁদুর নিধন অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সচেতনতা বাড়িয়ে এটাকে সামাজিকভাবে আরো অংশগ্রহণমূলক করতে হবে। গ্রামে, শহরে, জমিতে সর্বত্রই একযোগে ইঁদুর নিধন করতে হবে। সমন্বিত ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা দু’ভাবে কার্যকরী করা যায়। প্রথমটি হলো ইঁদুরের বাসস্থান ও চলাচলস্থল পরিবর্তন করা এবং দ্বিতীয়টি হলো বিভিন্ন কৌশলে ইঁদুরের সংখ্যা কমিয়ে আনা। ইঁদুর যেহেতু নোংরা স্থান পছন্দ করে, সেহেতু ফসলের মাঠ, বাধ, বাড়িঘরসহ ইঁদুরের বংশবিস্তারের সব স্থান পরিষ্কার পরিছন্ন রাখলে বংশবৃদ্ধি কমে আসে। তাছাড়া ফাঁদ ও অন্যান্য কৌশল প্রয়োগ করে ইঁদুরের সংখ্যা কমিয়ে আনা যায়। ইঁদুর দমনের পদ্ধতিসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. অরাসায়নিক পদ্ধতিতে দমন ২. রাসায়নিক পদ্ধতিতে দমন এবং ৩. জৈবিক পদ্ধতিতে দমন।
অরাসায়নিক পদ্ধতিতে দমন
অরাসায়নিক পদ্ধতি হলো ভৌত ও যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা। যেমন- (১) গর্ত খুঁড়ে ইঁদুর বের করে মেরে ফেলা। (২) ইঁদুরের গর্তে পানি ঢেলে এবং মরিচ/খড়/সালফারের ধোঁয়া দিয়ে ইঁদুর বের করে মেরে ফেলা। (৩) জমির আইল চিকন (৬ থেকে ৮ ইঞ্চি), আগাছা এবং আবর্জনা ময়লা মুক্ত রাখা, রোপণ দূরত্ব বাড়ানো, ধানক্ষেতে মাছ চাষ। (৪) বাঁশের, কাঠের, লোহার ও মাটির তৈরি বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করা। যেমন- কেচিকল (Kill trap), বাঁশের কল, বাঁশের ফাঁদ, জীবন্ত ইঁদুর ধরার ফাঁদ, মাটির ফাঁদ, মাটির চিটাগুড়ের ফাঁদ, তারের ফাঁদ। উক্ত ফাঁদগুলো আবার দুই ধরনের-জীবিত ও মৃত (স্ন্যাপ) ফাঁদ। জীবন্ত ফাঁদে আবার একক ইঁদুর বা বহু ইঁদুর জীবন্ত ধরার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জীবন্ত ফাঁদে খাবার দিতে হয়। খাবার হিসাবে ধান বা চালের সাথে নারিকেল তেলের মিশ্রণ তৈরি করে নাইলন বা মসারির কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে টোপ হিসাবে দিতে হয়। এ ছাড়াও শুঁটকি মাছ, শামুকের মাংসল অংশ, পাকা কলা ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাপকভাবে ফাঁদ ব্যবহার কষ্টসাধ্য হলেও ইহার মাধ্যমে ইঁদুরের সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব। বন্যাপ্রবণ এলাকায় কলাগাছের ভেলার উপর ফাঁদ স্থাপন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। যখন দলগত বা সামাজিকভাবে বৃহৎ এলাকায় ফাঁদ ব্যবহার করা হয় তখন ইহা খুবই কার্যকরী হয়। কেচিকল দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায় এবং রাসায়নিক ইঁদুরনাশক ব্যবহরের তুলনায় সাশ্রয়ী।
(৫) গাছে ধাতব পাত ব্যবহার করা। গাছের কাণ্ডে পিচ্ছিল ধাতব পাত পেঁচিয়ে রাখলে ইঁদুর গাছে উঠতে পারে না বিধায় ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। (৬) গ্লুবোর্ড ব্যবহার করা। বোর্ডে বা মেঝেতে ইঁদুরের খাবার রেখে চতুর্দিকে গ্লু বা আঠা লাগিয়ে রাখা। এক্ষেত্রে ইঁদুর খাওয়ার জন্য গ্লু-এর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় আটকে যায়, আটকে পড়া বাত্তি ইঁদুরকে সহজেই মেরে মেলা যায়। (৭) খাদ্য ও তার অবশিষ্টাংশ ঢেকে রাখা। (৮) একই এলাকার ধান ফসল একই সময়ে লাগানো ও কর্তন করা। ২৫ হেক্টরের একটি করে দল গঠন করে এ কাজ করা যেতে পারে। (৯) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে ইঁদুরের প্রকোপ কমানো যায়। বাড়িঘর ও ক্ষেতের আশেপাশের ঝোপঝাড়, জলাশয়ের কচুরিপানা পরিষ্কার রাখা। (১০) প্রতিরোধক জাল ব্যবহার করা। (১১) ধানক্ষেতের চারদিকে এক মিটার উচ্চতায় পলিথিন দ্বারা ঘিরে দিয়ে ইঁদুরের আক্রমণ প্রতিরোধ করা। (১২) আগে পাকে এমন স্বল্প জীবনকালের ধান (যেমন ব্রি ধান৬২) চাষ করে ইহাকে ফাঁদ ফসল (Trap crop) হিসেবে ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করা।
(১৩) বিভিন্ন যান্ত্রিক উৎপীড়ক (রিপেলেন্ট) যেমন-ভিডিও ফ্লিম টানিয়ে, মানুষের প্রতিকৃতি অথবা আলট্রা শব্দ সৃষ্টি করে জমি থেকে ইঁদুরকে সাময়িক সরিয়ে রাখা যায়। এর কার্যকারিতা তেমন নয় কারণ এতে ইঁদুরের সংখ্যা কমে না বরং দীর্ঘদিন ব্যবহারে এই সমস্ত ডিভাইসের প্রতি ইঁদুর অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।
ট্র্যাপ ব্যারিয়ার সিস্টেম (Trap Barrier System)
কৃষিক্ষেত্রে অল্প এলাকায় এটি ব্যবহার করা যায়। একটি টোপ (ষঁৎব) ফাঁদ ফসল (আগাম পাকে) চাষ করে ইঁদুর ঢুকতে না পারে এ রকম বেড়া দিয়ে এটাকে ঘিরে দিয়ে বেড়ার মাঝে মাঝে ফাঁক তৈরি করে ফাঁকের ভেতরের দিকে একসাথে অনেক ইঁদুর ধরা পড়ে এরকম জীবন্ত ফাঁদ পেতে রাখতে হবে। ইঁদুর খাবারের আকর্ষণে ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে ধরা পড়বে। এই পদ্ধতির সফলতা পেতে হলে কাছাকাছি সময়ে (১৫ দিনের মধ্যে) আশেপাশের সকল কৃষক জমি লাগাতে হবে এবং বেড়ার টোপ ফসল আগাম পাকতে হবে। এই টোপ ফাঁদ বেড়া পদ্ধতি তৈরি করতে যে খরচ হবে তা সব কৃষক ভাগ করে নেবে। কোন এলাকায় প্রতি বছর ইঁদুরের দ্বারা ১০ ভাগের বেশি ক্ষতি হলে ট্র্যাপ ব্যারিয়ার সিস্টেম গ্রহণ করা দরকার।
রাসায়নিক পদ্ধতিতে দমন
রাসায়নিক পদ্ধতিতে ইঁদুর দমনে তিন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- ১) একমাত্রা বিষটোপ ২) দীর্ঘমেয়াদি বিষটোপ এবং ৩) বিষ গ্যাসবড়ি ব্যবহার করা হয়।
একমাত্রা বিষটোপ : এ ধরনের বিষটোপ ইঁদুর একবার খেলেই সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। এরূপ সর্বাধিক পরিচিত বিষটোপ হচ্ছে গমে মিশ্রিত জিংক ফসফাইড (<২%)। এটি ব্যবহারের কৌশল হলো জিংক ফসফাইড ছাড়া শুধু গম কয়েক দিন দিয়ে অভ্যাস করে হঠাৎ একদিন জিংক ফসফাইড মিশ্রিত গম প্রদান করা।
দীর্ঘমেয়াদি বিষটোপ (Anticoagulant) : এ ধরনের বিষটোপ ইঁদুর খেলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় না। ইঁদুরের শরীরে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয় এবং কিছুদিন অর্থাৎ ২ থেকে ১৪ দিন পর মারা যায়। যেমন- ল্যানির্যাট, স্টর্ম, ব্রমাপয়েন্ট, ক্লের্যাট ইত্যাদি। যে সমস্ত দীর্ঘমেয়াদি বিষটোপ রক্ত জমাট প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার মাধ্যমে ইঁদুর দমন করে, সেগুলো শহরাঞ্চল এবং কৃষিক্ষেত্রে ইঁদুর দমনে খুবই কার্যকরী হলেও আর্থিক মূল্য এবং পরিবেশের বিষয় বিবেচনা করলে দীর্ঘ দিন এগুলো ব্যবহার করা ঠিক নয়।
গ্যাসবড়ি
গ্যাসবড়ি বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন করার মাধ্যমে ইঁদুর মেরে ফেলে। ইঁদুরের গর্তে বিষাক্ত অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড বড়ি দিয়ে গর্তের মুখ ভাল করে বন্ধ করে দিলে ইঁদুর মারা যায়। অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট ছাড়াও ফসটক্সিন ট্যাবলেট, হাইড্রোজেন/রাসায়নিক ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।
রাসায়নিক রিপলেন্ট
গুদামজাত বীজে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করলে তা রিপলেন্ট হিসাবে কাজ করে। যেমন-গেছো ইঁদুর/ঘরের ইঁদুর ম্যালাথিয়ন ব্যবহারিত স্থান এড়িয়ে চলে। এছাড়া দেখা গিয়েছে যে, সাইক্লোহেক্সামাইড ব্যবহৃত এলাকায় ইঁদুরের উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য।
জৈবিক পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন
জৈবিক পদ্ধতি হলো ইঁদুর দমনে অন্য জীবের সাহায্য নেয়া। ইঁদুরভোজী প্রাণীদের রক্ষা এবং বংশবিস্তারের যথাযথ ব্যবস্থা করলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ ইঁদুর সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে। পেঁচা, শিয়াল, বেজি, বন বিড়াল, সাপ, গুইসাপ, বিড়াল জাতীয় প্রাণীর প্রধান খাদ্য হচ্ছে ইঁদুর। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইসরাইল, জর্ডান, মালয়েশিয়া ও হাঙ্গেরি মাঠ ফসলের ইঁদুর দমনে পেঁচার ব্যবহার করছে। এজন্য তারা পেঁচার প্রাকৃতিক পরিবেশকে সংরক্ষণের পাশাপাশি এর প্রজনন ও প্রতিপালন কার্যক্রমকে কৃষক পর্যায়ে উৎসাহিত করছে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে যে, একজোড়া পেঁচা চার মাসের একটি প্রজনন চক্রে ৪ থেকে ৬টি বাচ্চার লালন-পালনে ৫০-৭০ গ্রাম ওজনের প্রায় ৩০০০ থেকে ৫০০০ পর্যন্ত ইঁদুর ভক্ষণ করতে পারে। বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি পেঁচার প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে কোন এলাকায় কোন প্রজাতির পেঁচা বেশি তার সঠিক তথ্য জানা নেই। অনেকে পেঁচাকে অলক্ষণের প্রতীক মনে করে। কিন্তু পেঁচা মানুষের কোন ক্ষতি করে না বরং নিরবে-নিভৃতে ইঁদুর দমন করে মাঠের ফসলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করছে। তাই জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এদের সংরক্ষণ ও বংশ বিস্তারের সুযোগ করে দিতে হবে।
সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার ধারণার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত পরিবেশসম্মত ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা (Ecologically-based Rodent Management, EBRM) বর্তমান সময়ে এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এখানে নিরাপত্তা, আর্থিক লাভ এবং স্থায়ী দমন ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। আমাদের দেশে ইঁদুর দমনের জন্য মূলত বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ ও রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সঠিকভাবে প্রয়োগ না করার কারণে ইঁদুর দমন কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয় না। প্রাথমিকভাবে রাসায়নিক বিষকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। রাসায়নিক বিষ ব্যবহারের ফলাফল প্রায়শই ব্যর্থ হয়। ইহার কারণ হলো সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার না করা এবং রাসায়নিক বিষে ইঁদুর প্রতিরোধী হয়ে যাওয়া। ফাঁদ ও রাসায়নিক বিষের সাথে সাথে অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারলে আর্থিক ও পরিবেশগত দিক থেকে ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা টেকসই হবে। জৈবিক পদ্ধতিকে ইঁদুর দমনকে বর্তমান সময়ে ইবিআরএম এর একটি আকর্ষণীয় এবং ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পরিবেশসম্মত ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনায় জৈবিক দমন পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করলে দীর্ঘমেয়াদে ইঁদুর দমনের ক্ষেত্রে ইহা মূল্যবান কৌশল হিসাবে কাজ করবে।
১প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ২মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিআরআরআই, গাজীপুর-১৭০১। মোবাইল : ০১৭১৫০১১৩৫১
ইমেইল : shamiulent@gmail.com
 ইঁদুরের মাধ্যমে বসতবাড়ি, গুদামজাত শস্যের ক্ষতি ও জনস্বাস্থ্যে করণীয়
ইঁদুরের মাধ্যমে বসতবাড়ি, গুদামজাত শস্যের ক্ষতি ও জনস্বাস্থ্যে করণীয়
ইঁদুরের মাধ্যমে বসতবাড়ি, গুদামজাত শস্যের ক্ষতি ও জনস্বাস্থ্যে করণীয়
কৃষিবিদ ড. মোঃ শাহ আলম
ইঁদুর জাতীয় প্রাণী হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিকারক প্রাণী যা ফসল বপন থেকে শুরু করে ফসল কাটা ও সংগ্রহ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে ক্ষতি করে থাকে। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য গুদামে সংরক্ষণ করা হয় যেখানে ইঁদুরের ক্ষতির পরিমান অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। ইঁদুর স্তন্যপায়ী, সর্বভুক, নিশাচর প্রাণী। এদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হলেও স্পর্শ, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্বাদেন্দ্রিয় বেশ প্রখর। ইঁদুর যে কোনো পরিবেশে নিজেকে খাপখাইয়ে খুব দ্রুত বংশবিস্তার করতে সক্ষম। একজোড়া ইঁদুর হতে বছরে চক্রবৃদ্ধি হারে গড়ে প্রায় ২০০০টি পর্যন্ত ইঁদুর জন্মলাভ করতে পারে। ইঁদুর সাধারণত গর্তে বাস করে, তবে কোন কোনো প্রজাতি ঘরে বা গাছেও বাসা তৈরি করতে পারদর্শী। যে কোনো স্থানে একটিমাত্র ইঁদুরের উপস্থিতিও এতটাই ক্ষতিকর যে, এর অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রান্তসীমা হচ্ছে শূন্য। তাছাড়া ইঁদুর জাতীয় প্রাণী বিভিন্ন রোগের বাহক/সংরক্ষক হিসাবেও কাজ করে, যেমন- প্লেগ, মিউরিন টাইফাস, লেপটোস্পারোসিস, ইঁদুর কামড়ানো জ¦র সালমোনেলোসিস ইত্যাদি। আমাদের বসতবাড়ি ও গুদামে যে কয়টি ইঁদুরের প্রজাতি বেশি ক্ষতি করে সেগুলো হলো- মাঠের বড় কালো ইঁদুর বা ধেড়ে ইঁদুর, ঘরের ইঁদুর বা গেছো ইঁদুর গোষ্ঠী, বাত্তি বা সোলই বা ঘরের নেংটি ইঁদুর, বাদামি ইঁদুর অন্যতম।
বসতবাড়ি, ল্যাবরেটরি ও গুদামে ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির ধরন
যে সমস্ত প্রাণী বসত বাড়ীতে ও গুদামজাত শস্যের ক্ষতি করে থাকে তাদের মধ্যে ইঁদুর অন্যতম। আমাদের দেশে যে পরিমান খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়, গোলাজাত করার পরে তার থেকে শতকরা প্রায় ৩ থেকে ৫ ভাগ শস্য এই সম্মিলিত ইঁদুর বাহিনী দ্বারা নষ্ট হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা গিয়েছে ইঁদুর দ্বারা সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ ২.৫-৩০ শতাংশ। একটি ইঁদুর প্রতিদিন ২৫ গ্রাম এবং একটি নেংটি ইঁদুর ৩-৪ গ্রাম খাবার খায়। ইঁদুর যে পরিমাণ শস্য খায়, তার চেয়ে ৪ থেকে ৫ গুণ পর্যন্ত বেশি নষ্ট করে মলমূত্র, পশম ও মাটির সাথে মিশিয়ে যা মানুষের খাবারের অনুপযোগী। একটি ইঁদুর প্রতিদিন ২৫-১৫০টি মল ত্যাগ, ১৫- ২৫ মিলি. প্রস্রাব করে এবং প্রায় ১০০০টি পশম ঝরে যায় যা খাদ্যশস্যের সাথে মিশে শস্য নষ্ট করে। ইঁদুর গুদামে বীজের ভ্রƒণের অংশ খেয়ে ফেলে ফলে বীজের খাদ্যগুন ও অংকুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। গোলা ও বস্তা কেটেও ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রিক তার আসবাবপত্র ইত্যাদি কেটে ক্ষতি করে। নেংটি ইঁদুর বাসা বাড়ী ও ল্যাবরেটরিতে লেপতোষক, বই পুস্তক, কাগজ, ফাইল ইত্যাদি কেটে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। ঢাকা জেলার সাভারের নামা বাজারের বিভিন্ন মুদির দোকানে জরিপ করে দেখা গেছে ইঁদুর চাল, ডাল, আটা, গম, তরিতরকারি, বস্তাসহ আসবাসপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র কেটে ও খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। যার পরিমাণ বছরে প্রায় ১৬ কোটি টাকা। গুদামে প্রতি পরিবারে ৪০-৫০ কেজি ধান বৎসরে ক্ষতি করে থাকে এবং এ ক্ষতির পরিমাণ ৭৫,০০০-১,০০,০০০ মেট্রিকটন। গুদাম ঘর কাঁচা হলে এরা গর্ত করে ঘরের দেয়াল ও মেঝে নষ্ট করে।
ইঁদুরে কাটা দানাশস্য বা জিনিসপত্র, মেঝেতে ইঁদুরের পায়ের ছাপ, খোবলানো মেঝের ঝুরঝুরে মাটি, পড়ে থাকা ইঁদুরের মল, কাঠের তাকে বা দেয়ালে তেলতেলে দাগ প্রভৃতি দেখে ইঁদুরের আক্রমণ ও উপস্থিতি বুঝা যায়।
ইঁদুর দমনের জন্য বিভিন্ন কার্যকরী দমন ব্যবস্থা রয়েছে। মূলত দমন পদ্ধতি নির্ভর করে উপস্থিত প্রজাতির ধরন, ক্ষতির মাত্রা ও পরিমাণ, ফসলের অর্থনৈতিক মূল্য, দমনপদ্ধতির সহজপ্রাপ্যতা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা সাপেক্ষে। অধিকন্তু, কোন একক পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেয়ে যৌথভাবে সমন্বিত বা সুসংহত দমন ব্যবস্থা নিলে অধিক কার্যকরী হয়। স্মর্তব্য যে, আহার, বাসস্থান ও পানি এ তিনের যে কোন একটির অভাব হলে ইঁদুর স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। ইঁদুর খাবার না খেয়ে এক সপ্তাহ বাঁচতে পারে কিন্তু পানি ছাড়া তিন দিনের বেশি বাঁচতে পারে না কিন্তু নেংটি ইঁদুর পানি ছাড়া অনেকদিন বাঁচতে পারে।
বসতবাড়ি ও গুদাম ঘরেও ইঁদুর দমন ব্যবস্থাকে প্রধানত দু’ভাবে ভাগ করা যায় অরাসায়নিক বা পরিবেশসম্মত দমন এবং বিষ প্রয়োগ বা রাসায়নিক দমন পদ্ধতি।
ক) অরাসায়নিক পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন (Non-chemical control)
আদিকাল থেকে কোন প্রকার বিষ বা বিষটোপ ছাড়া ইঁদুর দমন প্রচেষ্টা চলে আসছে। যথাসম্ভব পরিবেশসম্মত পদ্ধতিতে দমনব্যবস্থা নেওয়া শ্রেয়।
১। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা (Ecological management)
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (ঈষবধহষরহবংং/ঐুমরবহব) বজায় রেখে বসতবাড়ি, রান্নাঘর, ভাণ্ডার, খাদ্য গুদাম, বাড়ির আঙিনা উচ্ছিষ্ট খাবার-দাবার, অবাঞ্ছিত আগাছা ও ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নির্মূল করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইঁদুরের দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনা যায়। খড়ের গাদা ও গোলাঘর মাটি হতে ১৮-২৪ ইঞ্চি উঁচুতে মাচা তৈরি করে স্থাপন করলে ইঁদুরের আক্রমণের মাত্রা হ্রাস পায়।
দালানকোঠা, ঘরবাড়ি ও খাদ্যগুদামে দরজা-জানালা, গ্রিল, পাইপের খোলা মুখ ও অন্যান্য ইঁদুর প্রবেশ স্থানের ফাঁক-ফোকরে ধাতব পাত বা তারজালি লাগিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ইঁদুরের অনুপ্রবেশ বন্ধ এবং চলাচল প্রতিহত করা সম্ভব। পানির ট্যাপের ছিদ্র, ভাঙা ড্রেন সর্বদা মেরামত করতে হবে যাতে ইঁদুরের জন্য পানি সহজলভ্য না হয়। ঘরে ড্রাম, মটকা, টিনের পাত্র ইত্যাদিতে ধান, গম ও অন্যান্য শস্যসামগ্রী সংরক্ষণ করলে ইঁদুরের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সম্ভব হলে শস্যাধারের মেঝে পাকা হওয়া বাঞ্ছনীয়।
২। ভৌত ও যান্ত্রিক দমন (Physical and Mechanical Control)
বসতবাড়িতে ফাঁদ পেতে ইঁদুর ধরা একটি চিরায়ত আদি দমন পদ্ধতি। ফাঁদ ব্যবহার কৌশল ও তা স্থাপনের স্থান নির্ধারণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, অন্যথায় ফাঁদ লাজুকতার (Trap shyness) সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইঁদুরের আকার আকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ফাঁদ ব্যবহার করা সমীচীন। যেমন ঘরের নেংটি ইঁদুর ধরার ফাঁদ দিয়ে বড় আকৃতির মাঠের ধেড়ে কালো ইঁদুর ধরা সম্ভব নয়। এসব ফাঁদ ইঁদুরের চলাচলের পথ বা আনাগোনাবহুল স্থান যথাঃ ঘরের কিনারায়, দেয়ালের পার্শ্বে, মাচায়, চালের উপর বা গর্তের কাছাকাছি স্থাপন করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ফাঁদে ধৃত ইঁদুর যথাশীঘ্রই সম্ভব সরানো হয় এবং পুরাতন, খারাপ ও মোল্ডযুক্ত টোপ সরিয়ে নতুন টোপ দেওয়া হয়। প্রয়োজনানুযায়ী ফাঁদের সংখ্যা কম হলে সাফল্য হ্রাস পায়। কোন কোন ফাঁদে ইঁদুর ধরা পড়ার সময়ই যাঁতাকলে আটকে মারা যায়। ইঁদুরের ফাঁদ ভীতি কাটানোর জন্য প্রথম ২-৩ দিন এ ফাঁদের মুখ খোলা রেখে স্থাপন করা হয়। ধৃত জীবন্ত ইঁদুর পানিতে ডুবিয়ে মেরে এবং মৃত ইঁদুরসমূহ মাটির গভীরে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।
৩। জৈবিক দমন (Biological control) : কেবল পরিবেশ বিধ্বংসী রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ইঁদুর নিধনযজ্ঞ চালানো সম্ভব নয়। তাই আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে পরিবেশবান্ধব জৈবিক দমনের দিকে। পরভোজী প্রাণীর মধ্যে দিবাচর শিকারি পাখি স্তন্যপায়ী প্রাণী সরীসৃপ দৈনিক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইঁদুর শিকার করে ইঁদুরের আধিক্য কমায়। আমাদের নিজেদের স্বার্থে এসব ইঁদুরভুক উপকারি প্রাণিকুলের নির্বিচার নিধন বন্ধে ও সংরক্ষণে যথাযথ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(খ) রাসায়নিক দমন বা ইঁদুরনাশক দিয়ে দমন
রাসায়নিক পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বহু যুগ ধরে রাসায়নিক পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন চলে আসছে। বিষ ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক পদ্ধতিকে মূলত দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) তীব্র বা তাৎক্ষণিক বিষ (খ) বহুমাত্রা বা দীর্ঘমেয়াদী বিষ। অরাসায়নিক পদ্ধতিতে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হলে, ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাধিক্য ঘটলে বিষ বা বিষটোপ ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিভিন্ন রকমের ইঁদুর নাশক যেমন : জিংক ফসফাইড, ল্যানির্যাট, ক্লের্যাট, ব্রমাপয়েন্ট প্রভৃতি বাজারে বিভিন্ন কীটনাশকের দোকানে পাওয়া যায়।
বিষ ব্যবহারের নিয়ম
যে সব ঘরে ইঁদুর আছে বলে মনে করেন অথবা নতুন মাটি তোলা গর্তের মুখে, ইঁদুর চলাচলের রাস্তার উপর বিষটো রেখে দিতে হবে। ছোট ঘর হলে ৪/৫ স্থানে এবং বড় ঘর হলে ১৫/২০ স্থানে বিষ রাখা প্রয়োজন। বিষটোপ প্রস্তুত ও ব্যবহারের পর হাত সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে। বিষটোপ ছোট ছেলে মেয়েদের ও গৃহপালিত পশুর নাগালের বাইরে রাখতে হবে। কখনো বিষ মুখে বা পেটে গেলে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ডাক্তার আসতে দেরী হলে রোগীকে বমি করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সন্ধ্যার সময় বিষটোপ দিতে হবে এবং পরদিন সকালে সেগুলো আবার তুলে রাখতে হবে। ইঁদুর সম্পূর্ণভাবে দমন বা নির্মূল করা সম্ভব হয় না। তাই এদের সংখ্যা কমিয়ে মূল্যবান খাদ্যশস্য রক্ষা করে খাদ্যাভাব দূর করার চেষ্টা করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট একক পদ্ধতি ইঁদুর দমনের জন্য যথেষ্ট নয়। ইঁদুর দমনের সফলতা নির্ভর করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন সময়োপযোগী পদ্ধতি ব্যবহারের উপর। অতএব সম্মিলিত এবং সময়োপযোগী দমন পদ্ধতি প্রয়োগ করলেই বসতবাড়ি ও গুদামে ইঁদুরের উপদ্রব কমানো সম্ভব।
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর। মোবাইল : ০১৯১১৮৫৭৫৮৬,
ই-মেইল : atamvpd@gmail.com
 ভাইরাস প্রতিরোধী গাছপালা
ভাইরাস প্রতিরোধী গাছপালা
ভাইরাস প্রতিরোধী গাছপালা
মৃত্যুঞ্জয় রায়
ব্রাজিলীয় বংশোদ্ভূত নোবেলজয়ী বৃটিশ প্রাণিবিজ্ঞানী স্যার পিটার মিডাওয়ার ভাইরাস সম্পর্কে এক মজার কথা বলেছেন। তিনি ভাইরাসকে বলেছেন, ‘ওটা প্রোটিন আবৃত এক টুকরো দুঃসংবাদ...’। আসলেই ভাইরাস যে কতবড় দুঃসংবাদ হয়ে আবির্ভূত হতে পারে তা এখন বিশ্ববাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ভাইরাস শব্দটি এখন আর বিশ্বের কারো কাছে অপরিচিত নয়। ভাইরাস কত সহজে মানুষ মেরে ফেলছে, কিন্তু মানুষের হাতে ভাইরাসকে মারা অস্ত্র তেমন কিছুই নেই। এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের ঘুম হারাম। শুধু করোনা ভাইরাসই নয়। বিশ্বে মানুষ ও প্রাণীর বহু মারাত্মক ব্যাধির কারণ নানা ধরনের ভাইরাস। এর মধ্যে বেশ কিছু ভাইরাস রোগের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিছু ভাইরাসের চিকিৎসার জন্য মানুষ লোক চিকিৎসার দ্বারস্থ হচ্ছে। এসব লোক চিকিৎসার মূল প্রাকৃতিক উৎস হলো গাছপালা।
বিশ্বজুড়ে ভাইরাসের রাজত্ব
আমাদের এই গ্রহে কত ভাইরাস আছে? সে হিসেবও বিজ্ঞানীরা করে ফেলেছেন, তবে তার হিসেব আমাদের সাদামাটা হিসেবে কুলাবে না। পৃথিবীতে প্রায় ১০৩১ রকমের ভাইরাস আছে। তার মানে সংখ্যাটি হলো ১০ এর পরে একত্রিশটা শূন্য। এর একটি হলো করোনা ভাইরাস। বিশেষজ্ঞদের মতে মাত্র ২০০ লিটার সাধারণ পানির মধ্যেই নাকি ৫০০০ জেনোটাইপের ভাইরাস থাকে। পৃথিবীর এমন কোন স্থান বা পরিবেশ নেই যেখানে ভাইরাস না আছে। গাছে, পানিতে, মাছে, প্রাণীতে, গভীর সাগরে, মেরুর বরফে, গরম-ঠাণ্ডা সব পরিবেশেই ভাইরাস রয়েছে। সাগরের ২০০০ মিটার গভীরেও মিলেছে ভাইরাসের সন্ধান। তার মানে গোটা গ্রহ জুড়ে রয়েছে ভাইরাসদের এক দাপুটে রাজত্ব। অদৃশ্য সেই রাজত্বের মহাশক্তির কাছে মানুষ যেন অসহায়। এসব ভাইরাসের মধ্যে কিছু ভাইরাস মানুষ ও প্রাণীদের রোগ সৃষ্টি করে থাকে, গাছেও রোগ সৃষ্টি করে। স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশে মৃত্যুর প্রধান দশটি কারণের একটি হলো ভাইরাস জীবাণু। হার্পস, এইচআইভি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জন্ডিস বা হেপাটাইটিস, ডেঙ্গু, পোলিও প্রভৃতি ভাইরাসজনিত অন্যতম প্রধান রোগ। সাথে সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯। এসব রোগের চিকিৎসা বা নিরাময় আধুনিক ঔষধের দ্বারা করা খুব কঠিন।
ফিরে যাই প্রকৃতির কাছে
প্রকৃতি আমাদের জীবনের মূলসূত্র। তাই সেখানেই রয়েছে আমাদের জীয়নকাঠি। গবেষকরা যুগ যুগ ধরে প্রকৃতি থেকে এমন কিছু গাছপালা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছেন যেগুলোর ভাইরাস প্রতিরোধী বা বিনাশী গুণ আছে। এসব গাছপালা হয় দেহে ভাইরাসকে অনুপ্রবেশে বাধা দেয় অথবা অনুপ্রবেশের পর তার কার্যকারিতাকে বাধা দেয়। কিছু গাছপালায় এমন কিছু প্রাণরাসায়নিক উপাদান আছে যা ভাইরাস দেহে ঢুকলেও আশ্রয়দাতার দেহকোষের ভেতরে সেসব ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধিকে বন্ধ করে দেয়। ফলে ভাইরাস আর আশ্রয়দাতার দেহে সহজে রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। পাকিস্তানের একদল গবেষক মুহাম্মদ নোমান সোহেল ও তার সাথীরা Allium sativum (রসুন), Daucus maritimus (বন্য গাজর), Helichrysum aureonitens (সোনামুখী), Pterocaulon sphcelatum, Quillaja saponaria ইত্যাদি গাছের মধ্যে ভাইরাস বিরোধী বেশ কিছু সক্রিয় উপাদানের সন্ধান পেয়েছেন যা দিয়ে ভাইরাস রোগের চিকিৎসার জন্য ঔষধ শিল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেই গবেষণাপত্রটি ২০১১ সালে এশিয়ান জার্নাল অব এনিম্যাল এন্ড ভেটেরিনারি এ্যাডভান্সেস এর ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গবেষকবৃন্দ বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানকৃত ভাইরাস বিরোধী গাছপালার একটি পর্যালোচনাও করেছেন। পর্যালোচনা করে বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন যে, ৫৭টি উদ্ভিদ হার্পস ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর ও এইচআই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর ২৬ প্রজাতির উদ্ভিদ।
ইনফ্লয়ঞ্জা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে পারে Camelia sinensis (চা), Cistus incanus, Echinacea purpurea, Geranium sanguineum, Narcissus tazetta, Pandanus amaryllifolius (পোলাও পাতা), Scutellaria baicalens রঙ ইত্যাদি। সিস্টাস ইনকানাস গাছ ইবোলা ও এইচআই ভাইরাস প্রতিরোধ করতে পারে। জন্ডিস বা হেপাটাইটিস সি রোগের ভাইরাস জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর হিসেবে গবেষকরা ৬টি গাছের সন্ধান পেয়েছেন। এসব উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহ হলো Trachyspermum ammi (রাঙা জিরা), Embelia schimper, Solanum nigrum (ফুটিবেগুন বা তিতবেগুন), Canabis sativa (গাঁজা বা ভাং), Acacia nilotica (বাবলা), Daucus maritimus (বন্য গাজর)। পরবর্তীতে তিউনিসিয়ার গবেষক এস.মিলাদি ও তাঁর সাথীরা ২০১২ সালে জার্নাল অব ন্যাচারাল প্রোডাক্ট জার্নালের ২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে দাবি করেন, ডকাস ম্যারিটিমাস প্রজাতির বন্যগাজরের বীজ এইআইভি টাইপ১, ডেঙ্গু, ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস, হেপাটাইটিস সি ইত্যাদি রোগের বিরুদ্ধে মধ্যম কার্যকর।
গবেষকবৃন্দ বিশ্ব গবেষণার প্রেক্ষিতে মোট ১১৫ প্রজাতির উদ্ভিদের খোঁজ পেয়েছেন যেগুলো কোনো না কোনো ভাইরাস জীবাণুর বিরুদ্ধে কম বেশি কার্যকর। এগুলোর মধ্য থেকে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন যে, ২৪ প্রজাতির গাছ দুই বা ততোধিক ভাইরাস জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে (সারণি দ্রষ্টব্য)। এমনকি গবেষকরা জানতে পেরেছেন যে, এই ২৪ প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে ২ প্রজাতির উদ্ভিদ ৪ রকমের ভাইরাস জীবাণুকে দুর্বল করতে পারে। এ দুটি প্রজাতির উদ্ভিদ হলো রসুন ও বন্য গাজর। রসুন হার্পস ভাইরাস, প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস-৩, রাইনোভাইরাস ও ভেসিকুলার স্টোমাটাইটস ভাইরাস প্রতিরোধী। এই ২৪টি গাছের সব গাছই হার্পস ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর। এসব উদ্ভিদের মধ্যে কিছু উদ্ভিদের দেখা আমরা এদেশেও পাই। যেমন- রসুন, চা, রাধাচূড়া, ছোলা, ডায়ান্থাস, বাবলা, ঘোড়ানিম, পোলাওপাতা ইত্যাদি। শুধু ভাইরাস বিরোধী উদ্ভিদের তালিকা তৈরিই নয়, গবেষকরা সেসব উদ্ভিদের কোন কোন রাসায়নিক উপাদান ভাইরাস বিরোধী ভূমিকা পালন করে তাও উল্লেখ করেছেন।
ভাইরাস বিরোধী পঞ্চরত্ন
সেজ ও পুদিনা : পুদিনাজাতীয় এক ধরনের বিরুৎ জাতীয় মসলা গাছ। অন্তত ছয়টি সূত্র থেকে জানা গেছে এ গাছ ভাইরাসজনিত রোগ নিরাময়ে লোক চিকিৎসায় বহুকাল আগে থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেজ গাছের ডাল-পাতায় রয়েছে স্যাফিসিনোলাইড নামক এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ যা মানুষের এইডস রোগের জীবাণু এইচআইভি-১ এর বিরুদ্ধে কার্যকর। এই রাসায়নিক উপাদান এইডস রোগের ভাইরাস জীবাণুকে মানুষের দেহকোষে অনুপ্রবেশে বাধা দেয়। পুদিনা বা চা ভাইরাস সংক্রমণ সারাতে লোক চিকিৎসায় প্রাকৃতিক ঔষধ হিসেবে অনেক নৃগোষ্ঠীর লোকেরা ব্যবহার করে আসছে। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও এর সত্যতা পাওয়া গেছে। পুদিনা পাতায় থাকা এক ধরনের অ্যাসেনসিয়াল অয়েল বা তেল মেনথল ও রোসম্যারিনিক এসিড এন্টিভাইরাল এজেন্ট হিসেবে কাজ করে বলে ২৪ জন গবেষকের গবেষণা ফলাফল থেকে জানা গেছে। বিশেষ করে এই পাতার রস আরএসভি বা শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণকারী ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে পারে। করোনাভাইরাসের জন্য এ গাছ নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।
তুলসী : একটি টেস্ট টিউব পরীক্ষায় দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের তুলসী হার্পস ও হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের বিরুদ্ধে বেশ ভাল কাজ করে। তুলসী পাতায় থাকা বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ বিশেষত এপিজেনিন ও ইউরোসোলিক এসিড এসব ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে পারে। তুলসী রস সেবনে দেহে ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। প্রায় ৪ সপ্তাহ ধরে ২৪ জন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের ওপর পরিচালিত বারোটি গবেষণা সূত্রের ফলাফলে দেখা গেছে, ওসব মানুষেরা ৩০০ মিলিগ্রাম পরিমাণ তুলসী রস সেবনের ফলে তাদের দেহে রোগ প্রতিরোধী হেল্পার টি কোষ ও ন্যাচারাল কিলার কোষের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পেরেছে। এই উভয় ধরনের কোষই মানুষের দেহে এসব ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে।
মৌরী বা পানমৌরী : টেস্ট টিউব পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে মৌরীর রস হার্পস ও প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ-৩ ভাইরাসের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভালো কাজ করতে পারে। প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা গবাদিপশুর রোগ। মৌরীর ট্রান্স-এনথিওল হলো প্রধান রাসায়নিক উপাদান যার এই শক্তি রয়েছে।
রসুন : মোট ২৩ জন মানুষের ওপর রসুনের কার্যকারিতা নিয়ে এক গবেষণা চালানো হয় যেসব মানুষদের ভাইরাসজনিত আঁচিল ছিল। রসুনের রস সেসব আঁচিলে প্রয়োগের ফলে ২ সপ্তাহের মধ্যেই তাদের সেসব আঁচিল দূর হয়। এ ছাড়া টেস্ট টিউব পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রসুন ইনফ্লুয়েঞ্জা এ এবং বি, এইচআইভি, এইচএসভি-১, ভাইরাল নিউমোনিয়া ও রাইনোভাইরাসের বিরুদ্ধেও কার্যকর। রসুন দেহে ভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।
আদা : নানাভাবে আদা খাওয়া যায়। চা বা লজেন্স যেভাবেই খাওয়া হোক না কেন তা উপকার করে। টেস্টটিউব পরীক্ষায় দেখা গেছে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, আরএসভি, ফেলিন ক্যালিসিভাইরাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে আদা বেশ ভালো কাজ করে। আদায় থাকা জিনজারোলস ও জিঞ্জারোন এসব ভাইরাস জীবাণুকে দেহকোষে অনুপ্রবেশে বাধা দেয়। জ্বর ও ব্যথা সারাতে বিশ্বব্যাপী আদার ব্যবহার রয়েছে। দ্য জার্নাল অব প্লান্ট মেডিসিনে ২০১৭ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটায় এক গবেষণায় দেখা গেছে, আদা মানুষের শ্বাসতন্ত্রের সাইনিসাটিয়াল ভাইরাস (আরএসভি) প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে।
দরকার আরও গবেষণা
সুপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন গাছপালা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। বহু গাছপালার মধ্যে এন্টিভাইরাল কম্পাউন্ড বা এমন কিছু রাসায়নিক উপাদান আছে যা ভাইরাস সংক্রমণকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এখন সময় এসেছে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন গাছের সন্ধান করার। গাছের যেহেতু ভাইরাস বিরোধী ক্ষমতা আছে, সেহেতু এই গ্রহে এমন গাছপালা নিশ্চয়ই আছে যা দিয়ে আমরা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারি। যেসব গাছ অন্য আরও অনেক ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে, সেসব গাছ করোনাভাইরাসকেও ঠেকাতে পারে কিনা তা দেখা যেতে পারে। দরকার এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা ও খুঁজে দেখা।
অতিরিক্ত পরিচালক (এলআর), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৮২০৯১০৭, ই- মেইল : kbdmrityun@yahoo.com
 কৃষিতে নারী (আশ্বিন ১৪২৮)
কৃষিতে নারী (আশ্বিন ১৪২৮)
কৃষিতে নারী
উদ্যোক্তা
কাজী আবুল কালাম
বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের প্রায় ৪১% মানুষ কৃষিকাজে সম্পৃক্ত। কৃষিকাজে নারী পুরুষ নির্বিশেষে কাজ করছেন। কৃষকেরা কৃষিপণ্য উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য দেখালেও তারা কৃষিপণ্যের যথাযথ মূল্য প্রাপ্তি হতে প্রায় ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছেন। কৃষকও যেন তাঁর উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান এবং অপরদিকে ভোক্তাও যেন যৌক্তিক মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারেন- বিপণন ব্যবস্থাপনায় এ বিষয়টিই হলো সবচেয়ে কঠিন কাজ।
পণ্য উৎপাদন হতে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানোর মধ্যবর্তী পথে একাধিক স্তরে একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদেরকে ‘অ্যাক্টর’ বা ক্রিয়াশীল বলা হয়। পণ্যের বাজারে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যতজন ‘অ্যাক্টর’ সম্পৃক্ত থাকেন সকলের ভূমিকাই কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে যত সংখ্যক ‘অ্যাক্টর’ সম্পৃক্ত হবেন তত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী উৎপাদক বা বিপণন শৃংখলের যেকোনো ‘অ্যাক্টর’-ই পুরুষ হবেন, এমন একটি ভাবনা সকলের মাঝে বিরাজমান। কিন্তু সেই ধারণা ক্রমান্বয়ে বদল হতে শুরু হয়েছে। আজকাল যেকোনো ব্যবসাতেই নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছেন। কৃষি ব্যবসাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। নারীরাও এখন এ ব্যবসায় কখনও উৎপাদক, কখনও মধ্যবর্তী ‘অ্যাক্টর’, আবার কখনও বা নিজেই উদ্যোক্তা।
যেকোনো উদ্যেক্তাকে তার পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান বজায় রেখে ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। যেকোনো পণ্য বিপণনের জন্য বিক্রেতাকে কতগুলো বিষয়ে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। সেগুলো হলো : ক্রেতার আচরণ, ক্রেতার বিভাজন বিপণন ব্যবস্থাপনা, বিপণন সম্পর্কিত তথ্য আহরণ, বিপণন কৌশল, বিপণন মিশ্রণ এবং পণ্যের মূল্য। এ বিষয়গুলো আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ক্রেতার পছন্দ, তার সন্তুষ্টি, ক্রয় সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয়ে একজন বিক্রেতা বা উদোক্তাকে বিবেচনা করতে হবে। ব্যবসা করার জন্য তাকে অনুসরণীয় নীতি মেনে চলতে হবে। বিপণনের ক্ষেত্রে যে সকল সম্ভাব্য সুযোগ রয়েছে তা শনাক্ত ও গ্রহণ করতে হবে। পণ্য বিপণনে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। বিপণনের অন্যতম শর্ত হলো যথাযথ স্থানে সঠিক সময়ে উপযুক্ত মূল্যে সঠিক পণ্য থাকতে হবে। এ বিষয়টিকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। সর্বোপরি একজন বিক্রেতা বা উদ্যোক্তাকে পণ্যের গুণগতমান, উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয়, বাজারের স্থান ও অবস্থা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করে তার পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।
কৃষিপণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তাকে সংশ্লিষ্ট কৃষিপণ্য বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে। বিশেষ করে কৃষিপণ্যটি কোথায় ও কোন সময়ে উৎপাদিত হয়, পণ্যের উৎপাদনের কলাকৌশল, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, সার, বালাইনাশক ব্যবস্থাপনা, ফসলের রোগ প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা, পণ্য উত্তোলনের সময়, সংগ্রহোত্তর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা থাকা আবশ্যক। পচনশীল কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা করা জরুরি। এ কারণে একজন উদ্যোক্তাকে প্রতিটি পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। একই সঙ্গে তাকে পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পণ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উদ্যোক্তাকে আরও একটি বিষয়ে নজর দিতে হবে। সে বিষয়টি হলো মূল্য সংযোজন। মূল্য সংযোজন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনাসহ এর বিভিন্ন ধাপে যেমন- বাছাই, গ্রেডিং, প্যাকেজিং বা অন্য কোনো উপায়ে গুণগতমান বৃদ্ধি করে সে পণ্যের উচ্চমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর জন্মলগ্ন থেকেই কৃষিপণ্য বিপণনের বিষয়ে কৃষককে তার উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে কাজ করছে। বিশেষ করে উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর অন্যতম কাজ হলো কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ। সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদি।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম হলো কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও কৃষিপণ্যের বাজারসংযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। ‘বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভলপমেন্ট’ প্রকল্পের অধীনে সারাদেশে এ পর্যন্ত ৩৩,৪৩২ জনকে উদ্যোক্তা সৃজনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; তন্মধ্যে নারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১২,০৩৫ জন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ঋণ সুবিধা দেয়া হয়। ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৫,০০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ৩,৫০,০০০/- টাকা। এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে গৃহীত প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণ করে অনেক নারী উদ্যোক্তা হয়েছেন।
কৃষকের বাজার
‘ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি’ -এর মাধ্যমে ব্যাপকসংখ্যক পুরুষ ও নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কর্মসূচিটি দেশের ৫টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, নরসিংদী, খুলনা, রংপুর ও কুমিল্লা জেলায় পরিচালিত হয়েছে। আধুনিক যুগে প্রচণ্ড ব্যস্ত জীবনে রান্নার জন্য সময় বের করা বেশ কঠিন বিষয়। এজন্য ফ্রেশকাট শাকসবজি অনেকের জন্যই স্বস্তিদায়ক। ‘রেডি টু কুক ও রেডি টু ফুড’ উন্নত বিশ্বে প্রচলিত একটি বিষয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাক সবজি বিশেষ করে মিশ্র সবজি ও সালাদ, বিভিন্ন ধরনের পাতাযুক্ত শাকসবজি, কচুর লতি ইত্যাদি ও ফলমূল (কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, আম, তরমুজ, ইত্যাদি) স্থানীয় ও ঢাকার বাজারের সুপারশপে বাজারসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
এ কর্মসূচির অধীনে যে সকল নারীরা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে উদ্যোক্তা হয়েছেন। উদ্যোক্তা নারীরা ইতোমধ্যে ব্যবসার পাশাপাশি নিজেরাও আগ্রহী নারীদের নিয়মিতভাবে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূলের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। অপরদিকে তারা উৎপাদিত পণ্য ‘কৃষকের বাজার’ এ বিক্রি করেন।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে কৃষিপণ্য বিপণনের বিষয়ে ২৩ জুন ২০২১ নারী উদ্যোক্তা রেখা রাণি অধিকারী জানান, পরামর্শ মোতাবেক আচার তৈরির উপর প্রশিক্ষণ নেন। এখন প্রায় ২৪ ধরনের আচার তৈরি করতে পারেন। ৭-৮ বছর যাবৎ তিনি আচার তৈরি করে বিক্রি করছেন। বর্তমানে তিনি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ‘কৃষকের বাজার’ এ আচার বিক্রি করেন। তৈরিকৃত আচার ‘মেসার্স মা ফুড প্রোডাক্টস’ নামে বিক্রি হয়। কৃষি দপ্তর বা অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেলাতে তিনি নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। করোনার সময়ে তার আচার বিক্রি অনেক কমে গিয়েছিল। ‘কৃষকের বাজার’ এ আচার বিক্রয়ের সুযোগ পেয়ে তিনি খুব খুশি।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জেলা মার্কেটিং অফিসারদের সহায়তায় ইতোমধ্যে কৃষিপণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ১৮ জেলার ৩৯টি উপজেলা হতে নির্বাচিত ৯৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর (কৃষক/ উদ্যোক্তা/ প্রক্রিয়াজাতকারী) একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। এ তালিকার মধ্যে ৭৫% নারী। পরবর্তীতে এ তালিকাটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত ‘বাংলাদেশ কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন কার্যক্রম’ এ প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে প্রেরণ করা হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীরা কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছেন।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জনবল, যন্ত্রপাতি, উপকরণাদির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কৃষি বিপণন কাজে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছে। আগামীতেও বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি বিপণন তথা ভ্যালু চেইনের বিভিন্ন স্তরে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের কাজে সহায়তার জন্য এসেম্বল সেন্টার স্থাপন, বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ, কুল চেম্বার নির্মাণ, রিফার ভ্যানের মাধ্যমে কৃষিপণ্য সরবরাহ ইত্যাদি কাজে উদ্যোক্তাদের সর্বদাই প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। এ ছাড়া সকল কার্যক্রমেই নারীদেরকে সর্বদাই প্রাধান্য প্রদান করা হয়ে থাকে। আশা করা যায় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের কৃষিবান্ধব কার্যক্রম এবং সর্বোপরি কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা আগামীতে কৃষিপণ্য বিপণনে আরও অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তা এগিয়ে আসবেন এবং সফল হবেন।
পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। মোবাইল : ০১৭২৭৫৩১১০০, ই-মেইল : kaziabulkalam@gmail.com
 আমদানি নির্ভরতা কমাতে দেশি জাতের মাল্টার সম্প্রসারণ
আমদানি নির্ভরতা কমাতে দেশি জাতের মাল্টার সম্প্রসারণ
আমদানি নির্ভরতা কমাতে দেশি জাতের মাল্টার সম্প্রসারণ
কৃষিবিদ মো. রাসেল সরকার
মাল্টা অত্যন্ত সুস্বাদু, রসালো ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন একটি ফল। ভিটামিন ‘সি’ সম্মৃদ্ধ ফলগুলোর মধ্যে মাল্টা অন্যতম। শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সী মানুষের কাছে এটি সমান জনপ্রিয়। কথায় বলে, ‘ফল খাই, বল পাই’। ফল যত তাজা খাওয়া যায় ততই ভালো, এতে ফলের পুষ্টিমান অটুট থাকে। তাজা ফল ভক্ষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন ফলের পরিপূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করা যায়, অন্যদিকে সঠিক পুষ্টিগুণও পাওয়া সম্ভব হয়। বর্তমানে দেশে আমদানিকৃত বিদেশি ফলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাল্টা। বিদেশি মাল্টা আমদানিতে প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে, অধিকন্তু দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকায় এসব ফলের স্বাদ ও পুষ্টিমান ধীরে ধীরে কমতে থাকে। বিগত কয়েকবছরে সারাদেশে বাণিজ্যিকভাবে মাল্টা চাষ বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে।
আমদানি বাণিজ্য
বাংলাদেশে সাধারণত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল তথা মধ্য মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত মধুমাস ধরা হয় এবং এসময়ই নানান দেশীয় ফলের প্রাচুর্য থাকে। বছরের অন্যান্য সময়ে এত বেশি দেশীয় ফল পাওয়া যায় না। বিশেষ করে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে জানুয়ারি পর্যন্ত কুল ও পেয়ারা বাদে অন্য দেশীয় ফল বাজারে তেমন থাকে না, এসময় ফলের চাহিদা পূরণে বিদেশি ফলই একমাত্র ভরসা। একটি হিসেব মতে, দেশি জাতের ফলের মাধ্যমে দেশের মোট ফলের চাহিদার মাত্র ৩৫ শতাংশ পূরণ হয়। বাকি ৬৫ শতাংশ ফল বাহিরে থেকে আমদানি করতে হয়। মূলত ৬ ধরনের বিদেশি ফল (আপেল, কমলা, মাল্টা, আঙ্গুর, বেদানা, নাশপাতি) সবচেয়ে বেশি আমদানি করা হয়। দেশে কিছু কিছু বিদেশি ফলের উৎপাদন শুরু হয়েছে তবু এখনো বিদেশি জাতের ফল আমদানি নির্ভরতা প্রায় ৯০ শতাংশের অধিক। দেশে আমদানিকৃত ফলের ৮৫% আপেল, কমলা, মাল্টা ও আঙ্গুর-এই ৪ ধরনের ফল। পণ্যের বাজার পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান ইনডেক্সমুন্ডি (ওহফবী গঁহফর) এর তথ্য অনুযায়ী মাল্টা ফল আমদানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে আপেল, কমলা, মাল্টা ও আঙ্গুর ফলের শুল্ককরসহ আমদানি ব্যয় ৯৪৬ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৮০২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। কাস্টমস এর তথ্যানুযায়ী দেশে ২০১৭-১৮ সালে শুধু মাল্টা ও কমলা আমদানি করা হয় ১,১৭,১৭০ মেট্রিক টন যাতে প্রায় ১ হাজার ৮৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়। মূলত ৪৬টি দেশ থেকে উল্লিখিত ৬ ধরনের বিদেশি ফল আমদানি করা হয়। আমদানিকৃত বিদেশি ফলের সিংহভাগই চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে দেশে আসে। অল্পকিছু স্থলবন্দরের মাধ্যমে ভারত ও ভুটান থেকে আমদানি করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দর এর হিসাব অনুযায়ী, বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে বন্দর দিয়ে মোট ৪.৫৮ লাখ মেট্রিক টন বিদেশি বিভিন্ন জাতের ফল আমদানি হয়েছে। শুল্ককরসহ যার বাজারমূল্য প্রায় ৩৪২২ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট বিদেশি ফল আমদানি হয়েছে ৪.৬১ লক্ষ টন। পাঁচ বছরে আমদানি বেড়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ১৬ হাজার টন এবং মোট আমদানির প্রায় ৭৭ শতাংশই হচ্ছে আপেল ও মাল্টা। আশার কথা হচ্ছে, দেশে মাল্টা চাষ সম্প্রসারণের সাথে সাথে বিদেশি মাল্টা আমদানির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমছে।
দেশে মাল্টা চাষের হালচাল
২০০৪ সালে খাগড়াছড়ির পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে বারি মাল্টা-১ নামে দেশীয় মাল্টার একটি জাত উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলো (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) ও সিলেট অঞ্চল ছাড়াও বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা, বরেন্দ্রভূমি, উত্তরাঞ্চলসহ প্রায় সমগ্র দেশে মাল্টার চাষাবাদ হচ্ছে। চারা রোপণের ১-২ বছরের মধ্যেই মাল্টা গাছে ফুল ও ফল আসে এবং সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে একাধারে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত একেকটি গাছ থেকে পূর্ণমাত্রায় ফল সংগ্রহ করা সম্ভব। এ দেশের প্রায় সকল অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া বারি মাল্টা-১ চাষের অনুকূল এবং খুব অল্প সময়ের মাঝেই ফল সংগ্রহ করা যায়। এর ফলে দেশের বিভিন্ন জেলায় ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছোট বড় নানা আকারের মাল্টা বাগান গড়ে উঠেছে। এসব ফলবাগান আগামী ২-৩ বছরের মাঝেই পূর্ণ উৎপাদনে যেতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিদেশি মাল্টা ও কমলার আমদানি নির্ভরতা কমাতে এবং দেশের মাটি ও জলবায়ু উপযোগী নতুন উদ্ভাবিত মাল্টার জাতের অধিক ফলনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) সারাদেশে লেবুজাতীয় ফসলের (মাল্টা, কমলা, লেবু প্রভৃতি) চাষ সম্প্রসারণের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ২০২৩ সালে শেষ হতে যাওয়া ৫ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩০ টি জেলার ১২৩টি উপজেলায় ৫৯১০০টি বিভিন্ন আয়তনের বাগান স্থাপিত হবে এবং প্রায় ৫০০০ পুরাতন মাল্টাবাগানের ব্যবস্থাপনা হবে। প্রকল্প শেষে দেশে মাল্টা ও কমলার উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। অতিরিক্ত প্রায় ৪০ হাজার মেট্রিক টন মাল্টা ও কমলা উৎপাদিত হবে যাতে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার অধিক বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। এ ছাড়াও, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রকল্পের মাধ্যমেও সাইট্রাস জাতীয় ফলের চাষাবাদ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ডিএইর তথ্য মতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে কমলা ও মাল্টার উৎপাদন হয়েছে যথাক্রমে ৪০,৩১৭ টন ও ২৮,০৪১ টন। দেশে চাষকৃত কমলার বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ যেখানে মাল্টার ক্ষেত্রে প্রায় ১০-১৫ শতাংশের অধিক।
দেশীয় মাল্টায় অনীহার কারণ
যদিও বিগত কয়েকবছরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সারাদেশে বাণিজ্যিকভাবে মাল্টা চাষ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে তথাপি দেশীয় জাতের মাল্টার ক্ষেত্রে সিংহভাগ ভোক্তার অনীহা লক্ষ করা যায়। দেশীয় মাল্টার প্রতি অনীহার প্রধান কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা হলো। ১. কথায় বলে, “আগে দর্শনধারী, তারপর গুণ বিচারী”, একথা দেশি জাতের মাল্টার ক্ষেত্রে প্রায় পুরোপুরি খাটে। দেশি জাতের মাল্টা পরিপক্ব অবস্থায়ও সাধারণত হলুদাভ সবুজ থাকে। ২. সাধারণভাবে মনে করা হয় বিদেশি ফলের পুষ্টিমান অধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এজন্য বিদেশি ফলের প্রতি অতিমাত্রায় দুর্বলতা এবং দেশীয় ফলের ক্ষেত্রে অজ্ঞতাজনিত অনীহা কাজ করে। ৩. মাল্টা নন-ক্লাইমেকটেরিক ফল বিধায় গাছ থেকে সংগ্রহ করার পর তা আর পাকে না। অসাধু অনেক ব্যবসায়ী ও চাষি মাল্টা পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই উচ্চমূল্য পাওয়ার জন্য গাছ থেকে সংগ্রহ করে বাজারজাত করে। এর ফলে মাল্টার পরিপূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায় না এবং ভোক্তার মনে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। ৪. দেশীয় মাল্টার পুষ্টিগুণ ও স্বাদ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় ভোক্তাদের দেশি জাতের মাল্টার প্রতি অনীহা দেখা যায়।
গৃহীত ব্যবস্থা/উদ্যোগ
বিদেশি মাল্টার আমদানি নির্ভরতা কমাতে দেশি জাতের মাল্টার বাজার সৃষ্টির বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোক্তার নিকট একে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। এই যুগপৎ বিষয়ের সম্মিলন ঘটিয়ে ভোক্তা এবং নতুন মাল্টা চাষি ও কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো। ১. গবেষণার মাধ্যমে ফল দীর্ঘদিন সংরক্ষণের নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং উজ্জ্বল কমলা বর্ণের উচ্চফলনশীল আগাম ও নাবী জাত উদ্ভাবন করা। ২. সরকারি হর্টিকালচার সেন্টার ও বেসরকারি নার্সারিগুলোতে অধিক পরিমাণে চারা উৎপাদনের মাধ্যমে চারার সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করা। ৩. বসতবাড়িতে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচুসহ অন্যান্য ফলের সাথে মাল্টার চারা রোপণের জন্য জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ৪. বিদেশি মাল্টা আমদানিতে শুল্কহার বাড়িয়ে দেশীয় জাতের মাল্টার বাজারজাতকরণের সুযোগ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। ৫. জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের ফল, সবজি কিংবা কৃষি প্রযুক্তি মেলা, প্রদর্শনী, মাঠ দিবসসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে দেশি জাতের মাল্টা ও এর পুষ্টিগুণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা ও লিফলেট বিতরণ করা। ৬. প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ অন্যান্য সকল অন্তর্জাতিক মাধ্যমে দেশীয় মাল্টার পরিচিতি, পুষ্টিগুণ ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে তথ্যনির্ভর প্রতিবেদন/ভিডিওচিত্র প্রকাশ করা। ৭. দেশের বিভিন্ন উপজেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ও কৃষকের নিজস্ব উদ্যোগে বিগত কয়েক বছরে ছোট বড় যেসব মাল্টাবাগান গড়ে উঠেছে সেসব কৃষি উদ্যোক্তার সফলতার গল্প তুলে ধরা। ৮. জেলা, অঞ্চল বা জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ফল চাষিকে পুরস্কৃত করা। ৯. উৎপাদিত ফলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণের পাশাপাশি উন্নত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করা। ফল উৎপাদন ও বিপণনের সাথে জড়িত কৃষক ও ব্যবসায়ীদের রপ্তানিযোগ্য ও মানসম্মত আধুনিক ফল উৎপাদন প্রযুক্তি, সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
বর্তমানে বাংলাদেশে দেশীয় জাতের মাল্টা (বারি মাল্টা-১) চাষে নীরব বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)। দেশীয় জাতের মাল্টাকে যথাযথ ব্রান্ডিং করতে পারলে একদিকে ফল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ অন্যদিকে বিদেশি মাল্টার আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা, ব্যাপক প্রচার প্রচারণা এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ বাংলাদেশকে মাল্টা আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশের কাতারে উন্নীত করতে পারে। য়
কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, তারাগঞ্জ, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১৭-৪৫২৫৩৩, ই-মেইল: russelsarker06@gmail.com
 শহর ও গ্রামের ইঁদুর দমনের কলাকৌশল
শহর ও গ্রামের ইঁদুর দমনের কলাকৌশল
শহর ও গ্রামের ইঁদুর দমনের কলাকৌশল
ড. সন্তোষ কুমার সরকার
ইঁদুরকে মানুষ পছন্দ করে না, কিন্তু ইঁদুর মানুষকে পছন্দ করে। মানুষ এবং ইঁদুর একই ছাদের নিচে বাস করে। একই টেবিলে আহার করে। মানুষ ইঁদুরের বাসস্থান বনভূমি নষ্ট করে ইঁদুরকে তাদের সাথে থাকতে বাধ্য করেছে। মানুষ ইঁদুরের খাদ্য, বাসস্থান ও পানির জোগানদার। ইঁদুর যখন বনে থাকে তখন এরা ক্ষতিকারক প্রাণী নহে। মানুষ ফসলি জমিতে বিল্ডিং তৈরি করে শহর গড়ছে। ইঁদুরও দিনে দিনে শহর বাসি হচ্ছে। বর্ষাকালের আরম্ভে মাঠের ইঁদুর গ্রামের বসতবাড়িতে এবং শহরে আগমন ঘটে। এজন্য বর্ষাকালে গ্রামের বসতবাড়িতে ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইঁদুরের সংখ্যা শহরে না গ্রামে বেশি? আমার মতে শহরে বেশি। কারণ শহরে মানুষের সংখ্যা বেশি, ইঁদুরও বেশি। শহরে সারা বছর ইঁদুরের খাদ্য, বাসস্থান ও পানির নিশ্চয়তা আছে। সারা বছরই ইঁদুরের বংশবিস্তার করার পরিবেশ বিদ্যমান। শহর বলতে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা শহরকে বিবেচনা করা হয়েছে। গ্রাম বলতে ফসলের মাঠ বাদে মানুষের বসবাসের ইঁদুরের স্থানকে বিবেচনা করা হয়েছে।
শহরের ইঁদুরের উপস্থিতির স্থান
যেখানে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশ করার সুযোগ নেই, সেখানে বিপুল সংখ্যক ইঁদুরের উপস্তিতি পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে, ভবিষতেও থাকবে। বড় বড় শহরে বড় বড় দালানের একটিও ইঁদুর মুক্ত বিল্ডিং খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রতিটি বাসাবাড়িতে ও আঙ্গিনায় ইঁদুরের উপস্থিতি রয়েছে। এ ছাড়াও কাঁচাবাজারের মাছ-মাংস, চাল-ডাল ও সবজি, ফলমূল বিক্রয় এলাকাতে এবং খাদ্যশস্য পাইকারী বাজারে মাঠের কালো ইঁদুরের উপস্থিতি রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত ক্ষতি করছে। মুরগির খামারে ও বাজারের বিক্রয় স্থানে মাঠের কালো ইঁদুরের উপস্থিতি রয়েছে। বিমান বন্দর ইঁদুরের অভয়াশ্রয় বলা যায়। সমুদ্র ও নদী বন্দরগুলোতে ইঁদুর দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।
ইঁদুর মুক্ত কোনো স্থান কোনো শহরে নেই। শহরে বছরে ইঁদুর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পদ ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যানগত বা গবেষণার কোনো তথ্য নেই। তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি প্রতিবছর প্রত্যেকটি শহরে কোটি কোটি টাকার সম্পদ ইঁদুর দ্বারা ক্ষতি হয়ে থাকে।
শহরে ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা
সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা মশা নিধনের প্রোগ্রামের মতো ইঁদুর দমনের কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। ইঁদুরের কারণে পানির অপচয় ও রোগবিস্তার এবং ড্রেনের ক্ষয়ক্ষতি এসব নিয়ন্ত্রণে সবাইকে গুরুত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। জনস্বাস্থ্যের গুরুত্বে বিবেচনায় ইঁদুর দমন প্রোগ্রাম অন্যান্য দেশের মতো সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা হতে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান পেস্টকন্ট্রোল সার্ভিসের মাধ্যমে তেলাপোকা ও ইঁদুর দমন করে থাকে। সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে বাসাবাড়ির ইঁদুর দমন করে থাকে। এ ছাড়াও অফিসে বা বাসাবাড়িতে ইঁদুরের ক্ষয়ক্ষতি না হলে কেউ ইঁদুর দমনের উদ্যোগ গ্রহণ করে না। সিঙ্গাপুরের অফিস বা বাসাবাড়ির আঙ্গিনায় ইঁদুরের উপস্থিতি পেলে শাস্তি প্রদানের আইন করা হয়েছে। এ আইনের উদ্দেশ্য প্লেগের মতো ছোঁয়াছে রোগের বিস্তার রোদ করা। আমাদের দেশেও অনুরূপ আইন করা প্রয়োজন।
শহরের ড্রেনের পাশে, ডাস্টবিনের গর্তের ইঁদুর ফসটক্সিন গ্যাস বড়ি প্রয়োগ করে দমন করা যাবে। প্রতি গর্তে একটি করে গ্যাসবড়ি প্রয়োগ করতে হবে। সিটিকর্পোরেশন ও পৌরসভা ওয়ার্ডভিত্তিক বছরের দুইবার ইঁদুর নিধন করতে হবে। বাসাবাড়ি, অফিসের ভিতর ইঁদুর দমনের গ্লুবোর্ড ব্যবহার করতে হবে। কারণ বিষটোপ ব্যবহার করলে তা খেয়ে এসির বা যন্ত্রপাতির ভিতর মরে থাকতে পারে এবং গন্ধ বাহির হবে। কেচিকল, তারের জীবন্ত ইঁদুর ধরার ফাঁদ ব্যবহার করেও ইঁদুর এবং চিকা মারা যায়। এক কক্ষে কম পক্ষে ৫-৬টি ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। ইঁদুরের উপস্থিতি যেমন- মলমূত্র বা পায়ের ছাপ, ক্ষতির চিহ্ন দেখামাত্র ইঁদুর মারার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। রান্না ঘরের খাবার ঢেকে রাখতে হবে। খাবার না পেলে ইঁদুর থাকবে না। নিচতলার বাহিরে দেওয়ালে ছোট বাক্সে ইঁদুরের বিষটোপ রাখলে ইঁদুর বিষটোপ খেয়ে মারা যাবে এবং বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করবে না বা উপদ্রব থাকবে না।
গ্রামে ইঁদুরের উপস্থিতির স্থান
গ্রামের প্রতিটি বসতবাড়িতে ইঁদুরের কমবেশি উপস্থিতি আছে। কত ইঁদুর আছে তার কোনো পরিসংখ্যানগত তথ্য নেই। আমাকে একজন কৃষক প্রশ্ন করেছিল যে, তাদের গ্রামে কতটি ইঁদুর আছে? আমি বলেছিলাম যতলোক বাস করে তার চেয়ে বেশি আছে। যদি কোথাও ইঁদুর চোখে পড়ে তবে ঐ স্থানে কমপক্ষে ৫টি ইঁদুর আছে। যতটি গর্ত আছে ততটি মাঠের কালো ইঁদুর রয়েছে। মাঠে পানি আসলে বিপুল সংখ্যক মাঠের কালো ইঁদুর গ্রামের উঁচু ভূমি, বসতবাড়িতে আসে এবং পানি চলে গেলে কিছু সংখ্যক ইঁদুর বসতবাড়িতে থেকে যায়। তাই বর্ষাকাল গ্রামের ইঁদুর দমনের উপযুক্ত সময়। এতে দুইটি উপকার হয় যথা : বসতবাড়িতে ইঁদুরের ক্ষয়ক্ষতি কম হয় এবং গ্রামের পাশে আমন ফসলের ক্ষতি কম হবে। বসতবাড়িতে মাঠের কালো ইঁদুর, গেছো ইঁদুর ও সলই ইঁদুরের উপস্থিতি বেশি রয়েছে। কৃষকের গোলাজাত শস্যের প্রায় ১০-১২% ক্ষতি করে। মাঠে কালো ইঁদুর মাটির ঘরে, উঠানে, খড়ের গাদায়, গরুর খাবার স্থানে বেশি গর্ত করে থাকে। এরা গরিবদের পছন্দ করে তাদের কাঁচা ঘরের জন্য আর ধনীদের পচ্ছন্দ করে খাদ্য শস্য বেশি থাকার কারণে। বসতবাড়ির সবজি যেমন- লাউ, চালকুমড়া, শসা এবং ফলমূলের বেশি ক্ষতি করে গেছো ইঁদুর ও মাঠের কালো ইঁদুর। ঘরের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিসপত্রের ক্ষতি করে সলই ইঁদুর, গেছো ইঁদুর ও মাঠের কালো ইঁদুর।
গ্রামের ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা
কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ : সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে ইঁদুর দমন অথবা মেরে থাকে। এতে সফলতার পরিমাণ অত্যন্ত কম। দমন ব্যবস্থা অল্প সময়ের জন্য কার্যকর থাকে। কারণ ইঁদুর খাদ্য,পানি ও বাসস্থানের জন্য সবসময় স্থান পরিবর্তন করে থাকে। তাই পাড়া অথবা গ্রামের সবাই একযোগে ইঁদুর দমন করা প্রয়োজন। এতে প্রতিবেশির বাড়িতে ইঁদুরের আগমনের সম্ভাবনা কমে যায়। উপদ্রব ও ক্ষয়ক্ষতি কম রাখতে এবং সফলভাবে ইঁদুর দমন করতে হলে কমিউনিটির সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন।
সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ একটি পাড়ার কৃষকদের সাথে বসে উঠান সভার মাধ্যমে ইঁদুর দমনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ঐপাড়ায় প্রতিটি বাড়িতে বিভিন্ন স্থানে ইঁদুরের গর্ত কতটি রয়েছে তার হিসাব করতে হবে। প্রতি গর্তে একটি করে ফসটক্সিন গ্যাস বড়ি প্রয়োগের জন্য ক্রয় করাতে হবে। সবাইকে নিয়ে তাদের দ্বারা গ্যাসবড়ি প্রয়োগ করাতে হবে। এদের একদিন দমন বিষয়ের উপকারিতা বুঝাতে হবে। ঘরের ইঁদুর দমনের জন্য প্রত্যেক বাড়ির জন্য ৩-৫টি কেচিকল বা তারের ফাঁদ ক্রয় করে একসাথে ব্যবহার করতে হবে।
গোলাজাত শস্যের ক্ষয়ক্ষতি রোধ
গোলাজাত শস্যের ক্ষতি ন্যূনতম ব্যয়ে উন্নত গোলা ব্যবহারের মাধ্যমে রোধ করা সম্ভব। বাঁশের তৈরি শস্যদানা গুদামের প্লাটফর্মে উপস্থাপন করা হয়, যেখানকার খুঁটি টিনের পাতা দিয়ে মুড়িয়ে প্রতিরোধ করা হয় যাতে ইঁদুর মাটি হতে গুদামটিতে আরোহন করতে না পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শস্যদানা গুদামটির ওপরের অংশ অবশ্যই সঠিক টেকসই আবরণ দ্বারা বন্ধ বা ঢেকে রাখতে হবে যাতে ঘরের দেয়াল অথবা ছাঁদ হতে ইঁদুর লাফ দিয়ে অথবা আরোহণ করতে না পারে এমন প্রতিরোধক সম্পন্ন করতে হবে। টিনের পাত অথবা অন্য ধাতব জিনিস দ্বারা বিদ্যমান গুদাম কাঠামোটির উপরি অংশ ভালোভাবে মুড়িয়ে দিতে হবে। পাশে ঝুলে থাকা প্রান্ত ইঁদুরকে আরোহণ বা উঠতে বিরত রাখবে।
খড়ের গাদার ক্ষয়ক্ষতি রোধ
খড়ের গাদা ইঁদুরের অন্যতম নিরাপদ বাসস্থান, বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে। খড়ের গাদার নিচে গর্ত খুঁড়ে ও কেটেকুটে ১০-২০% খড় নষ্ট করে থাকে। এ খড় পশুকে খাওয়ালে ইঁদুরবাহিত রোগ দ্বারা পশু আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খড়ের গাদা করার সময় মাচা বা মঞ্চ করে রাখলে ইঁদুরের ক্ষয়ক্ষতি হতে খড়কে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এতে খড়ের গুণগতমানও ভাল থাকবে। সাধারণত ৬০-৭০ সেন্টিমিটার উঁচু মাচা তৈরি করে খড়ের গাদা তৈরি করলে এবং মাচার নিচের অংশ সব সময় পরিষ্কার রাখলে ইঁদুরের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যায়।
আঁঠার ফাঁদ দ্বারা ইঁদুর দমন
বাজারে দোকানে ইঁদুর মারার আঠার তৈরি গ্লুবোর্ড বা আঠার ফাদ পাওয়া যায়। ইঁদুরের চলাচলের রাস্তায় পেতে রাখলে ইঁদুর আঠায় আটকা পড়ে যেতে পারে না। ইঁদুর আটকা পড়ার পর যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি তুলে মেরে ফেলতে হবে। কারণ দেরি হলে অন্যান্য ইঁদুর দেখে ফেলে ঐ স্থানে ইঁদুররা যাবে না। তাই একটা ইঁদুর ধরা পড়ার পর আঁঠার ফাঁদ একটু দূরে পাততে হবে। ঘরে একটি আঁঠার ফাঁদ ব্যবহার না করে ২-৩টি ফাঁদ ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।
ইঁদুরভোজী প্রাণী পালন
বিড়াল ও কুকুর পালন করলে ইঁদুরের উপদ্রব কম থাকবে। বিড়ালকে রাতে কম খাবার দিতে হবে। ইঁদুরভোজী বেজি, গুইসাপ মারা যাবে না।
পরিশেষে ইঁদুর যেকোনো পরিবেশে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার কৌশল জানা স্তন্যপায়ী প্রাণী। একজন কৃষক বলেছেন, ইঁদুরকে মারতে হলে প্রযুক্তিগত দক্ষ ও স্মার্ট হতে হবে। সঠিক দমনপ্রযুক্তি সিলেকশন, সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। একের অধিক দমন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। সারা বছর ধরে সবাই মিলে ইঁদুর মারতে হবে। তবেই খাদ্যশস্য, সম্পদ ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি হবেনা। পাশাপাশি দেশ সমৃদ্ধিতে কৃষি দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে। য়
মুখ্য প্রশিক্ষক (অব.), ডিএই, রূপায়নলোটাস ৬বি, ১৩ তোপখানা রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৪২২২১৫৭
ই-মেইল : Santoshsarker10@gmail.com
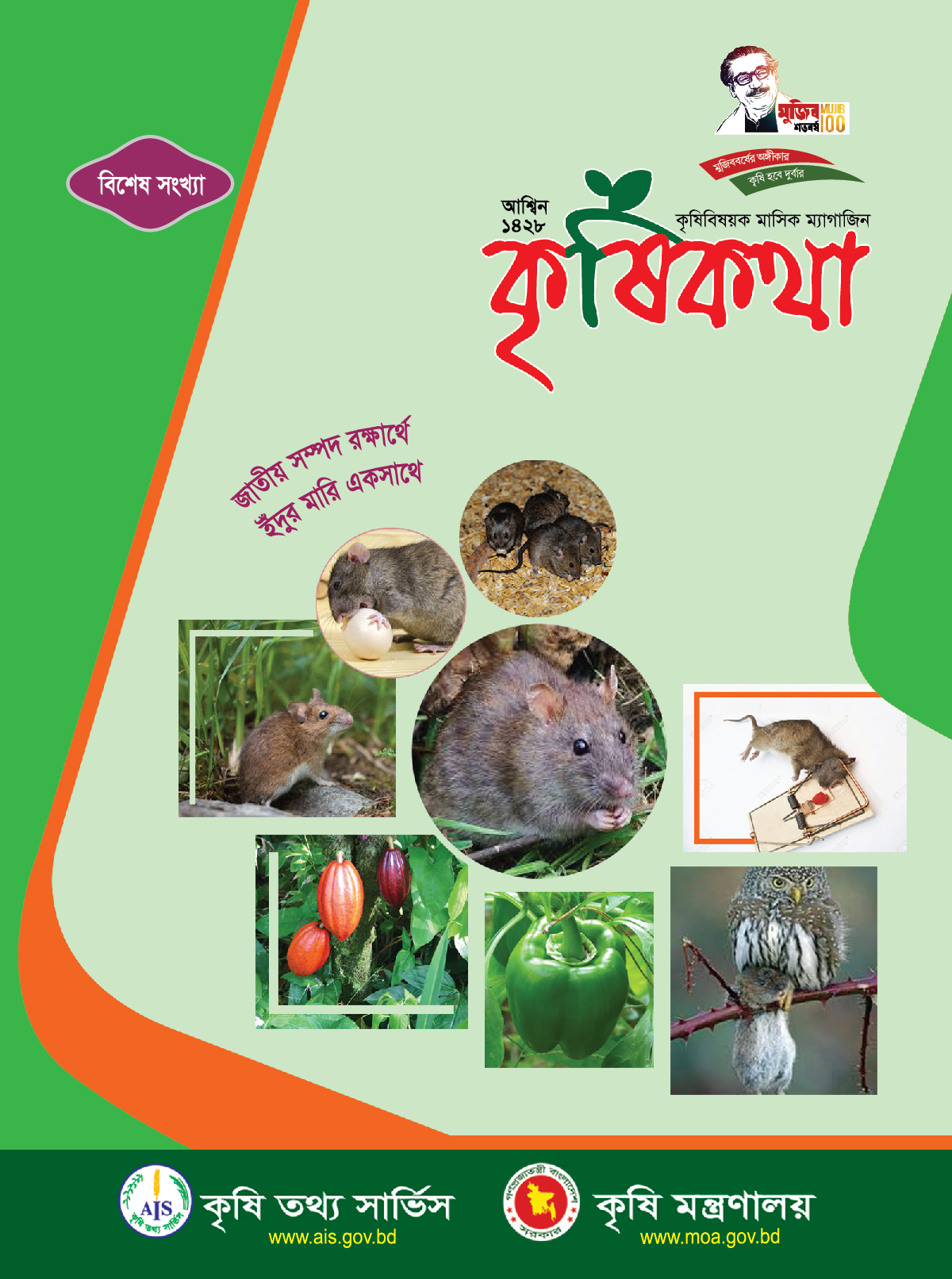 কোকো ফলের গুণাগুণ ও বাংলাদেশে আবাদ সম্ভাবনা
কোকো ফলের গুণাগুণ ও বাংলাদেশে আবাদ সম্ভাবনা
কোকো ফলের গুণাগুণ ও বাংলাদেশে আবাদ সম্ভাবনা
সমীরণ বিশ্বাস
কোকো দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান উপত্যকার উদ্ভিদ। মধ্য আমেরিকায়ও চাষ হয় এ ফল। তারপর আফ্রিকার ঘানা, আইভরিকোস্ট, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন এ ফল চাষ শুরু করে। এশিয়ার মালায়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নিউগিনি ও বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে ও উড়িষ্যায় কোকো ফলের চাষ হচ্ছে।
কোকো গাছে ফুল ও ফল ধরতে সময় লাগে ৩-৪ বছর। ফুল ফলে পরিণত হয় ৬ মাসে। প্রতিটি কোকো ফলের ৫টি সারিতে ৩০-৪০টি বীজ থাকে। বীজ কলাপাতায় পেঁচিয়ে গাজানো হয়, তারপর বীজ সংগ্রহ করে রোদে শুকানো হয়। শুকানো কোকো বীজ সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে শাস পাওয়া যায়, যাকে বলে কোকো বিন। এই কোকো বিন থেকে অতি মূলবান কোকো গুড়া বা ডাস্ট (পাউডার) তৈরি হয়। কোকো বিনের গুঁড়াই কোকো পণ্য তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। কোকো ডাস্ট (পাউডার) দিয়ে উৎকৃষ্ট মানের চকোলেট, মাখন, আইসক্রিম, রুটি, পুডিং, প্রসাধনী সামগ্রী ও পানীয় তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য যে, ক্যাডবেরির চকোলেট তৈরি হয় কোকো ডাস্ট (পাউডার) দিয়ে।
কোকো পাউডার থেকে তৈরি পণ্য প্রোটিন, ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেটসমৃদ্ধ। কোকো পাউডারের মিশ্রণে ভিটামিন, মাইক্রো, ম্যাক্রো উপাদান এবং অন্যান্য সক্রিয় পদার্থ বিদ্যমান যা শরীরের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। প্রাকৃতিক কোকো পাউডারের প্রধান উপকরণ হলো ফ্লেভোনয়েড, ক্যাটাচিন এবং ইপেক্টিন। শরীরের মধ্যে এই পদার্থগুলো এন্টিঅক্সিডেন্টসমূহের কাজ করে। পাশাপাশি এই পদার্থ রক্ত সঞ্চালন এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, চাপ স্বাভাবিক রাখে। ব্রোচিয়ার, হাঁপানি রোগীদের জন্য কোকো পাউডারে থিওফিলিন ও জ্যান্থাইন উপাদান খুব দরকারী। এই সক্রিয় পদার্থের এন্টিস্পাজমোডিক প্রভাব আছে যা ব্রোঙ্কাইটিস, হাঁপানি প্রতিরোধ এবং শ^াসপ্রশ^াস সহজ করে। কোকো পাউডারের অন্য উপাদান হলো ফেনিলেথিল্যামাইন যার কারণে ক্লান্তি ও বিষণ্নতা থেকে রোগীরা মুক্তি পায়। এর অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে যে, কোকো পাউডারের উপাদান ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধিকে দমন করে। ইহা কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, পেশি এবং টিস্যুসমৃদ্ধ করে শরীরকে ক্ষতিকারক বেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। কোকো পাউডারের পানীয় মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।
আমরা অনেকে জানি কোকো বিদেশি ফল। তবে একেবারেই নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। সিসিডিবি হোপ সেন্টার ছাড়াও আমাদের দেশে আছে কোকো গাছ। এখানেও কোকো ফল হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সংরক্ষিত বাগানে আছে একটি গাছ। ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস জার্মপ্লাজম সেন্টারে আছে আরও ১১টি গাছ। সিসিডিবি হোপ সেন্টারের গাছটি সুদূর ইন্দোনেশিয়া থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহ করে গাছটি তৈরি করা হয়। এই গাছগুলোর বৃদ্ধি ও ফলন বেশ স¦াভাবিক। তবে ফলটি নিয়ে আমাদের দেশে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি।
কোকো গাছের চারা তৈরির জন্য পরিপক্ব ফল থেকে বীজ সংগ্রহের পরপরই সাধারণ মাটির বেডে চারা তৈরি করতে হবে। চারার বয়স একমাস হলেই নির্দিষ্ট জমিতে কোকো চারা রোপণ করা যাবে। বীজ সংগ্রহের পর নরমাল তাপমাত্রায় বেশি দিন বীজ রাখলে বীজ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হারিয়ে যায়।
কোকো চির সবুজ গাছ, দেখতে ঝোপাল, ৭ থেকে ৮ মিটার পর্যন্ত উঁচুু হতে পারে। কাণ্ড ও ডালপালার গায়ে গুচ্ছবদ্ধ গোলাপি ও হলুদ রঙের ফুল ধরে। গাছের বয়স সাধারণত ৩ থেকে ৪ বছর সময়ে ফুল ধরতে শুরু করে। ফুল থেকে পরিণত ফল হতে সময় লাগে ৬ মাস। ফলের রং বাদামি, ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১০ সেন্টিমিটার পুরু, বাইরের আবরণ চামড়ার মতো শক্ত। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় ১০০ বছর আগে কোকো চাষ শুরু হলেও ফলটি অনেক পুরনো এবং হাজার হাজার বছর আগে থেকেই প্রকৃতিতে ছিল। মায়ানমারা মনে করত, কোকো ঈশ্বর প্রদত্ত ফল। পৃথিবী জুড়ে প্রায় ২৩ জাতের কোকো ফল দেখা গেলেও সাধারণত দুইটি জাতই প্রধান। সবচেয়ে বেশি কোকো ফল উৎপন্ন হয় আইভরিকোস্টে। বার্ষিক গড় উৎপাদন ১,৩৩০ টন। তারপর ঘানার অবস্থান, ৭৩৬ টন।
কোকো গাছ এমন একটি জায়গায় লাগানো দরকার যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো পড়বে না। সাথী ফসল হিসেবে কোকো গাছ লাগানো যেতে পারে। পূর্ণাঙ্গ একটি কোকো গাছ থেকে প্রতি বছর ৩৫ কেজি বীজ পাওয়া যায়, যার প্রতি কেজি কোকো চকোলেট পাউডারের দাম ৪০ ডলার। প্রতিটি কোকো গাছ থেকে বছরে ১২০০ ডলার বা ৮৪ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। প্রতি বছর ভারত ও পাকিস্তান থেকে ২ লাখ টন কোকো ফল আমদানি করা হয় যাহার মূল্য প্রায় ৫শ’ কোটি টাকা।
বাংলাদেশে কোকো গাছ আবাদের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। কোকো গাছের চাষ করলে আমরা আন্তর্জাতিক বাজারেও অনায়াসেই একটা স্থান করে নিতে পারব। কারণ বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু নিরক্ষীয় ও উপনিরক্ষীয় ফল চাষের জন্য উপযোগী। কোকো গাছের জন্য রেইনফরেস্ট সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের আধ্যাপক ডঃ সৈয়দ শফিউল্লাহ বেতছড়ি উপজেলায় তার নিজস্ব উদ্যোগে ১০০টি কোকো গাছ লাগিয়েছেন। এই ফল চাষ করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে সারা বিশ্বে রপ্তানি করা সম্ভব।
কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে বাংলাদেশের জলবায়ু কোকো চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত। ছাদ বাগানেও কোকো ফল চাষ করা যায়। কোকো গাছ ছাঁটাই করে গাছকে ছোট করে রাখা যায় এবং বড় বড় ছায়াবীথির নিচে এদের শ্রীবৃদ্ধি ভালো হয়। য়
কোঅর্ডিনেটর, অ্যাগ্রিকালচার, সিড অ্যান্ড বায়োচার প্রোগ্রাম, সিসিডিবি। ই-মেইল :srb-ccdbseed@yahoo.com, মোবাইল : ০১৭৪১১২২৭৫৫
 মিষ্টিমরিচ চাষাবাদের আধুনিক কলাকৌশল
মিষ্টিমরিচ চাষাবাদের আধুনিক কলাকৌশল
মিষ্টিমরিচ চাষাবাদের আধুনিক কলাকৌশল
কৃষিবিদ লিমু আক্তার
মিষ্টিমরিচ একটি মূল্যবান সবজি এবং বাজারে এর চাহিদা অন্যতম। আকৃতি এবং গন্ধ তীব্রতায় এটি মরিচ থেকে ভিন্ন। মিষ্টিমরিচ মাংসল, আকার ও রঙে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চল মরিচের উৎপত্তিস্থল। বিশ্বে আবাদকৃত সব মরিচই হচ্ছে ঈধঢ়ংরপঁস ধহহঁঁস প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। ঈধঢ়ংরপঁস ধহহঁঁস এর মধ্যে ১১টি গ্রুপ রয়েছে যাদেরকে ঝালবিহীন ও ঝালমরিচ হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে। মিষ্টিমরিচের ফল গোলাকার ও ত্বক পুরু হয়। বড় বড় শহরের আশে পাশে সামান্য পরিমাণে কৃষকরা এর চাষ করে থাকে, মার্কেটে বিক্রি হয়ে থাকে। মিষ্টিমরিচের রপ্তানি সম্ভাবনাও প্রচুর রয়েছে। বিশ্বে টমেটোর পরে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সবজি হচ্ছে মিষ্টিমরিচ। এর বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে যেমন-সালাদ অথবা সুপ তৈরিতে ব্যবহার হয় এবং ওষুধি গুণাগুণ রয়েছে। পুষ্টিমানের দিক থেকে মিষ্টিমরিচ একটি অত্যন্ত মূল্যবান সবজি। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকার কারণে এবং টবে চাষের উপযোগী বলে দেশের জনসাধারণকে মিষ্টিমরিচ খাওয়ার জন্য উদ্বুুদ্ধ করা যেতে পারে।
মিষ্টিমরিচ চাষাবাদ প্রযুক্তি
সুনিষ্কাশিত দোঁআশ বা বেলে-দোআঁশ মাটি মিষ্টিমরিচ চাষের জন্য উত্তম। মিষ্টিমরিচ খরা এবং জলাবদ্ধতা কোনোটিই সহ্য করতে পারে না। মিষ্টিমরিচের জন্য মাটির অম্লক্ষারত্ব ৫.৫-৭.০ এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মানসম্মত মিষ্টিমরিচ উৎপাদনের জন্য ১৬০-২৫০সে. তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশ সবচেয়ে উপযোগী। রাতের তাপমাত্রা ১৬০-২১০সে. এর কম বা বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল ঝরে পড়ে, ফলন ও মান কমে যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই ফলন হয় না। ফুল এবং ফল ধারণ দিবস দৈর্ঘ্য দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু আলোক তীব্রতা এবং আর্দ্রতা ফল ধারণে প্রভাব ফেলে। অক্টোবর মাসে বীজ বপন করে নভে¤¦রে চারা রোপণ করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। গাছের স¦াভাবিক বৃদ্ধির জন্য পলিথিন ছাউনি, পলি হাউজ, পলিভিনাইল হাউজে গাছ লাগালে রাতে ভেতরের তাপমাত্রা বাহির অপেক্ষা বেশি থাকে। উন্নত বিশ্বে যেমন-জাপান, আমেরিকা, বৃটেন, নেদারল্যান্ড, তাইওয়ান এ গ্রিন হাউজ, গ¬াস হাউজ, পলি হাউজ ইত্যাদির মাধ্যমে তাপমাত্রা ও আলো নিয়ন্ত্রণ করে সারা বছরব্যাপী লাভজনকভাবে এটির চাষ করছে। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও একই পদ্ধতি গ্রহণ করে প্রচুর মিষ্টিমরিচের চাষ হচ্ছে।
সবজি বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৯ সালে বারি মিষ্টিমরিচ ১ এবং ২০১৫ সালে বারি মিষ্টিমরিচ ২ জাত দুটি মুক্তায়িত হয়েছে।
বারি মিষ্টিমরিচ ১ এর বৈশিষ্ট্য
গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেমি., পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের, অপরিপক্ব (এৎববহ ঝঃধমব) এবং পরিপক্ব (গধঃঁৎব ঝঃধমব) উভয় অবস্থায় ভক্ষণযোগ্য। অপরিপক্ব অবস্থায় গাঢ় সবুজ বর্ণের ইবষষ ংযধঢ়বফ ফল হয়। চারা লাগানোর ৭০-৮০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। বড় আকর্ষণীয় ফল এবং ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম। কাচা অবস্থায় ফল চকচকে সবুজ এবং পাকলে গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করে। পরিপক্ব (ঊফরনষব) ফলের রঙ গাঢ় লাল বর্ণের। দীর্ঘদিন ফল কর্তনযোগ্য (প্রায় ৫০-৬০ দিন), ফলন ১৫-২০ টন/হেক্টর।
বারি মিষ্টিমরিচ ২ এর বৈশিষ্ট্য
গাছের উচ্চতা ৭০-৮০ সেমি., পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের, অপরিপক্ব (এৎববহ ঝঃধমব) এবং পরিপক্ব (গধঃঁৎব ঝঃধমব) অবস্থায় ভক্ষণযোগ্য, অপরিপক্ব অবস্থায় সবুজ বর্ণের ইবষষ ংযধঢ়বফ ফল হয়, চারা লাগানোর ৬৫-৭৫ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। ৮০-৯০ গ্রাম ওজনের বড় আকর্ষণীয় ফল। চকচকে সবুজ ফল, পাকলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। ফলন ২০-২৫ টন/হেক্টর, দীর্ঘদিন ফল কর্তনযোগ্য (প্রায় ৫০-৫৫ দিন)। জাত ও মৌসুমভেদে মিষ্টিমরিচের জীবনকাল ১২০ থেকে ১৪০ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে।
বীজের মাত্রা
প্রতি এক গ্রাম বীজে থাকে প্রায় ১৬০টি বীজ। অঙ্কুরোদগমের হার ৯০% বিবেচনায় প্রতি হেক্টরে বীজের পরিমাণ ২৩০ গ্রাম এবং চারার সংখ্যা ৩০,০০০ প্রয়োজন।
চারা উৎপাদন
প্রথমে বীজগুলো ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সুনিষ্কাশিত উঁচু বীজ তলায় মাটি মিহি করে ১০х২ সেমি. দূরে দূরে বীজ বপন করে হালকাভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজনানুসারে ঝাঝরি দিয়ে হালকাভাবে সেচ দিতে হবে। বীজ গজাতে ৩-৪ দিন সময় লাগে। বীজ বপনের ৭-১০ দিন পর চারা ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট হলে ৯х১২ সেমি. আকারের পলিব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে। পটিং মিডিয়াতে ৩ঃ১ঃ১ অনুপাতে যথাক্রমে মাটি, কম্পোস্ট এবং বালু মিশাতে হবে। পরে পলিব্যাগ ছায়াযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে, যাতে প্রখর সূর্যালোকে এবং ঝড় বৃষ্টি আঘাত হানতে না পারে।
জমি তৈরি ও চারা রোপণ
ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে যাতে জমিতে বড় বড় ঢিলা এবং আগাছা না থাকে। মিষ্টিমরিচ চাষে প্রতি শতাংশে সারের পরিমাণ সারণি দ্রষ্টব্য। জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর, টিএসপি, জিংক অক্সাইড, জিপসাম এবং ১/৩ ভাগ ইউরিয়া এবং এমওপি পরবর্তীতে দুই ভাগ করে চারা লাগানোর ২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত ২০-২৫ দিন বয়সের চারা ৫০ী৪০ সেমি. দূরত্বে রোপণ করা হয়। মাঠে চারা লাগানোর জন্য বেড তৈরি করতে হবে। প্রতিটি বেড প্রস্থ ১ মি. হতে হবে এবং লম্বায় দুটি সারিতে ১২টি চারা সংকুলানের জন্য ৩ মিটার বেড হবে। চারা বিকেল বেলা রোপণ করা উত্তম। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে। প্রতিদিন মাঠ পরিদর্শন করতে হবে। যদি কোনো চারা মারা যায় তাহলে ওই জায়গায় পুনরায় চারা রোপণ করতে হবে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা অনেক কমে যায়। এ সময় গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কাজেই গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য নাইলন নেট এবং পলিথিন ছাউনিতে গাছ লাগালে রাতে ভেতরের তাপমাত্রা বাহির অপেক্ষা বেশি থাকে এবং গাছের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।
সেচ প্রয়োগ
জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। আবার অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলেপড়া রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থা করতে হবে।
ফসল তোলা
সাধারণত সপ্তাহে একবার গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ফল সংগ্রহের পর ঠাণ্ডা অথচ ছায়াযুক্ত স্থানে বাজারজাতকরণের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য, ফসল সংগ্রহের সময় প্রতিটি ফলে সামান্য পরিমাণে বোঁটা রেখে দিতে হবে।
মিষ্টিমরিচ চাষাবাদে বিভিন্ন পোকামাকড় (জাব পোকা, লালমাকড়) রোগবালাই (অ্যানথ্রাকনোজ, উইল্টিং) প্রভৃতি আক্রমণ হয়ে থাকে। এসব বালাই থেকে নিরাপদে মিষ্টিমরিচ চাষাবাদের ক্ষেত্রে বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দমন করতে হবে। তাহলেই নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে। পাশাপাশি কৃষি ও কৃষকের সমৃদ্ধ হবে। য়
সায়েন্টিফিক অফিসার, অলেরিকালচার বিভাগ, হর্টিকালচার গবেষণা বিভাগ, বারি, জয়দেবপুর। মোবাইল ০১৭২৬৬২০৬৩০, ই-মেইল : limuakter@gmail.com
 মাছ চাষে জাতীয় শত্রু ইঁদুর নিধনে করণীয়
মাছ চাষে জাতীয় শত্রু ইঁদুর নিধনে করণীয়
মাছ চাষে
জাতীয় শত্রু ইঁদুর নিধনে করণীয়
কৃষিবিদ মোঃ আলতাফ হোসেন চৌধুরী
১৯৭২ সালের জুলাই মাসে কুমিল্লার এক জনসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন মাছ হবে ২য় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ। এরই অংশ হিসেবে ১৯৭৩ সালে গণভবনের লেকে বঙ্গবন্ধু মাছের পোনা অবমুক্তকরণের মাধ্যমে মাছ উৎপাদনের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেন। দীর্ঘদিন পরে হলেও বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে যুগান্তকারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশাল কর্মযজ্ঞের অন্যতম হলো দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ব্যাপকভাবে প্রাণিজ (মৎস্য) প্রোটিনের উপর যেমন জাতিকে নির্ভর করতে হয় তেমনি দেশের প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার ৬০% প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পুরণ হচ্ছে মৎস্য থেকে। জনপ্রতি বাৎসরিক মাছ গ্রহণ ২৩.০০ কেজি। মাছের বাৎসরিক চাহিদা ৪৩.৪১ লাখ মে.টন। উৎপাদন হচ্ছে ৪৪ লাখ মে.টন। জনপ্রতি মাছের বার্ষিক চাহিদা ২১.৯০ কেজি, জনপ্রতি মাছের দৈনিক চাহিদা ৬০ গ্রাম, আর প্রানিজ আমিষ সরবরাহে মাছের অবদান ৬০ শতাংশ। প্রচলিত আছে পরিবেশে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ পারস্পরিক দেয়া নেয়ার মাধ্যমে একটি জটিল ও জুতসই খাদ্য শৃঙ্খল তৈরি করে। ইঁদুর নামক প্রাণীটি তার ব্যতিক্রম এবং দেয়ার চেয়ে ক্ষতি করে অনেক বেশি। এটি পরিবেশবান্ধব সুবিধাজনক প্রাণী নয় বরং ক্ষয়ক্ষতির ‘রাজা’ নামে পরিচিত। ইঁদুর নামক প্রাণীটি মানুষের খাদ্যে ভাগ বসিয়ে খাদ্য নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। ইঁদুর বা ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর অনবরত কাটাকাটির অভ্যাস বিদ্যমান। কাটাকাটি করতে গিয়ে ইঁদুর কৃষি ফসলের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় রুপালি মাছের ও বেশ ক্ষতি করে। মাছ ও চিংড়ির ঘেরের বিশেষভাবে ক্ষতি করে থাকে। মাছ চাষের উত্তম সময়ে মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত ঘের বা পুকুরের চারদিকে গর্ত করে এবং গর্ত পর্যায়ক্রমে বড় হয়ে নদী-খাল বা অন্য জলাশয়ের সাথে সংযোগ তৈরি করে। এতে ঘেরে পানি কমে যায়, ঘের/পুকুরের পাড় ভেঙে যায় এবং কৃষকের জন্য বাড়তি ঝামেলা ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি ঘের/পুকুরে মাছের খাদ্য খায় এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছের খাদ্য নষ্ট করে। বর্ষাকালে দরিদ্র কৃষক বাঁধের ধারে বিদ্যমান বরো-পিটে মাছ চাষ করে সাময়িক অর্থ রোজগার করে। সেখানে ইঁদুর চেলা/গর্ত তৈরি করে স্বল্প সময়ের জন্য তেলাপিয়া, পাংগাশ ও পুঁটি মাছ চাষ বিঘ্নিত করে। এ ছাড়াও ইঁদুর খামারের/পুকুরের গভীর ও অগভীর নলকূপের সেচের নালা নষ্ট করে পানির অপচয় করে থাকে।
কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৯৮৩ সাল থেকে ইঁদুর নিধন অভিযান পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে সারাবিশ্বে মৎস্য ও পোলট্রি শিল্প ইঁঁদুর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এবং মৎস্য ও পোলট্রি উৎপাদনকারীদের অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। ইঁদুর মৎস্য বা পোলট্রি খামারে গর্ত করে খামারের আর্থিক ক্ষতি করে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অমেরুদণ্ডী প্রাণী বিভাগের হিসেবে ইঁদুর প্রতিটি মুরগির খামারে বছরে ১৮০০০ টাকার ক্ষতি করে থাকে। যদিও এই বিষয়ে সরকারি/বেসরকারি মৎস্য খামারে ইঁদুরের ক্ষয়ক্ষতির স্বীকৃত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি তবুও মৎস্য সেক্টরে ইঁদুরের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নেহায়েত কম না ।
রুপালি মৎস্য উৎপাদন তিনটি বিষয়ের উপর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিষয়গুলো হলো- ১. ফিড, ২. রেণু (পোনা), ৩. ব্যবস্থাপনা। বিষয়গুলোর একটির ঘাটতি হলে মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হবে। জাতীয় শত্রু ইঁদুর নিধন কার্যক্রমটি মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। অতএব, বুঝতে বাকি থাকেনা এই প্রাণীটি মাছ চাষে কতটুকু ক্ষতির কারণ?
মৎস্য চাষে ইঁদুর নিধনের ব্যবস্থাপনা : মৎস্য চাষে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণে কতিপয় ব্যবস্থাপনা নেয়া যেতে পারে। যেমন-
১. মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য জাতীয় শত্রু ইঁদুরের বাসযোগ্য পরিবেশ ধ্বংস করা। সঠিক উপায়ে পুকুরপাড় প্রস্তুতকরণ (পুকুর শুকানো, তলদেশের পচাকাদা অপসারণ, বার বার চাষ দিয়ে শুকানো এবং চুন প্রয়োগ)।
২. পানির উন্নত গুণাবলী বজায় রাখা (পিএইচ, অক্সিজেন, এ্যামোনিয়া ইত্যাদি) কারণ ময়লা আবর্জনার দিকে ইঁদুরের ঝোঁক বেশি।
৩. শীতের শুরুতে পুকুর পাড় মেরামত করা ইঁদুরের গর্তে পানি ঢেলে বা প্রয়োজনে গাইডওয়াল বেধে ইঁদুর নিধন করা।
৪. ইঁদুর ‘প্লেগ’সহ অন্যান্য রোগ ও পরজীবী রোগের প্রধান বাহক তাই সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইঁদুর নিধন জরুরি।
৫. ব্রুড মাছ ও খামারের নিয়মিত পরিচর্যা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন।
৬. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সরবরাহ নির্মিত মৎস্য খামার বা পুকুর সঠিক পদ্ধতিতে তৈরি করতে হবে এবং যথাযথ মনিটরিংয়ের মাধ্যমে উন্নত খামার গড়ে তুলতে হবে।
৭. বদ্ধ জলাশয়ের মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করতে হলে পাড়সমূহ আবর্জনামুক্ত ও সঠিকভাবে তৈরি করতে হবে।
৮. পরিবেশবান্ধব চিংড়ির পি.এল (পোস্ট লার্ভি) এর চাষ সম্প্রসারণ করতে হলে হ্যাচারি বা ঘেরের গুদাম/হ্যাচারি ইউনিটে ইঁদুর যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
৯. মৎস্য উৎপাদন এবং সরবরাহ কাজে ব্যবহৃত উপাদান যেমন- পিটুইটারি গ্রান্ড (পি.জি), এইচসিজি, ট্রাক, ভ্যান, পিকআপ, জালদড়ি এবং অন্যান্য উপাদানসমূহ গুণগত মানসম্পন্ন হতে হবে যাতে এসবের ভেতর/কোঠরে ইঁদুর বা ইঁদুরের বাচ্চা ঢুকতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
১০. ইঁদুর নিধনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরগুলোর মাঝে সমন্বিত ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে।
১১. সরকারি বেসরকারি মৎস্য খামারের গুদামসমূহে (জাল, নেট, খাবার ইত্যাদির) ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্য মাচাং করা এবং বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করা।
১২. এ ছাড়া সরকার অনুমোদিত ব্রমাডিওলোন ও জিংক ফসফাইড গ্রুপের ইঁদুরনাশক ল্যানির্যাট, ব্রমাপয়েন্ট, জিংক ফসফাইড ইত্যাদি) গুদামে সাবধানে রাখা ও ব্যবহার করা।
অধিক মৎস্য উৎপাদনের চেয়ে গুণগত মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যকর ও জীবাণুমুক্ত মৎস্য উৎপাদন অধিক শ্রেয়। মাছ চাষের ক্ষেত্রে এই প্রবাদটির গুরুত্ব অপরিসীম। ইঁদুর একটি স্থলজ প্রাণী। অতএব, উন্নত জলজ পরিবেশ ও খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছকে সুস্থ রাখা অধিকতর সহজসাধ্য, কম ব্যয়বহুল, কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং পরিবেশবান্ধব। যাই হোক ‘রুপালি মৎস্য চাষ দিচ্ছে ডাক, দরিদ্রতা ঘুচে যাক’ এই প্রতিপাদ্যকে বাস্তবায়ন করতে হলে এবং বর্তমান সরকারের ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে এক কাতারে দাঁড়ানোর জন্য মাছ চাষের জাতীয় শত্রু ইঁদুর নিধনে কোনো আপস করা যাবে না। এই হোক ইঁদুর নিধনের অঙ্গীকার। ৎ
খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সদর, লালমনিরহাট। মোবাইল : ০১৭১২৪০৮৩৫৩, ই-মেইল : chowdhari_33@ yahoo.com
 প্রাণিসম্পদে ইঁদুরের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিরোধের উপায়
প্রাণিসম্পদে ইঁদুরের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিরোধের উপায়
প্রাণিসম্পদে ইঁদুরের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিরোধের উপায়
ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ সেক্টর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন অগ্রগতি বিশ্বের প্রথম ১০টি দেশের কাতারে এসেছে। ছাগলের মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। আবার গরু পালনে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদের অবস্থান ১২তম। প্রাণিসম্পদ জিডিপিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। মাংস উৎপাদনে আমরা এখন স্বনির্ভর। কোরবানির জন্য আর কোনো দেশের উপর নির্ভর করতে হয় না। দেশে ব্রয়লার উৎপাদন চাহিদা মিটিয়ে এখন রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। করোনার কারণে খামারিদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রণোদনা পেয়েছে খামারিরা। বাজারের অস্থিতিশীল অবস্থাসহ বেশ কিছু সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। এসবের মধ্যে ইঁদুরের উৎপাত একটি অন্যতম সমস্যা। এর কারণে প্রতি বছরে প্রাণিসম্পদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ অনেক। ইঁদুরের বংশ বৃদ্ধি হার বেশি হওয়ায় এর দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়। খাবার নষ্ট করা, খাবারের গুণগতমান নষ্ট করাসহ নানা রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে এই রোডেন্ট ইঁদুর। প্রাণিসম্পদের প্রায় সকল প্রজাতির জন্যই ইঁদুর অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিশেষ করে পোল্ট্রি পালনে এবং গবাদিপ্রাণি পালনে বেশি ঝামেলা সৃষ্টি করে।
খামারে ইঁদুর যেসব ক্ষতি করে থাকে
ইঁদুর যা খায় তার চেয়ে বেশি খাবার নষ্ট করে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ইঁদুর তার দেহের মোট ওজনের প্রায় ১০% ওজন পর্যন্ত ফিড খেতে পারে। একটি ইঁদুর দৈনিক প্রায় ২৫ গ্রাম খাবার খায় সে হিসেব করলে দেখা যায় বছরে ৯.১ কেজি খেয়ে থাকবে। একটি হিসেবে দেখা যায় যদি কোনো শেডে ২০টি ইঁদুর থাকে তাহলে বছরে প্রায় ০.১৮ টন নষ্ট হয়ে যায়। ইঁদুর যা খায় তার ৪-৫ গুণ খাবার নষ্ট করে আর মুরগি ও ডেইরি খামারে সেসব খাবার খায় না। এসব ক্ষতি খামারিদের পালনের খরচ বাড়ায় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতির মধ্যে পড়ে। ইঁদুর শেডের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করলে মুরগি ও গবাদিপশু ভয় পেয়ে যায়। বিশেষ করে ডিমপাড়া সময়ে মুরগি ইঁদুর দেখলে আতঙ্কিত হয়ে যায়। প্রতিনিয়ত ইঁদুর মুরগির শেডে এভাবে চলাচল করলে ডিমপাড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় ফলে অনেক সময় ডিম উৎপাদন কমে যায়। ডিম সময়মতো সংগ্রহ না করা হলে ডিম ভেঙে যাওয়াসহ নানা সমস্যা হতে পারে। বাচ্চার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলে অথবা তাদের গলাকেটে মেরে ফেলে। গবাদিপ্রাণির দুধ উৎপাদন কমিয়ে দেয়। ইঁদুর খামারে থাকলে বায়োলজিক্যাল দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় বায়োসিকিউরিটি সমস্যা। অনেক খামারে অন্য প্রিডেটর না আসলে কোনো রোগের আউটব্রেক হওয়ার কারণ হতে পারে ইঁদুর। কারণ ইঁদুর প্রায় ৬০ ধরনের রোগবাহী জীবাণু বহন করে। ইঁদুর বিভিন্ন প্রজাতির রোগবালাই যেমন- সালমোনেলা, পাসচুরেলোসিস, মাইক্রোপ্লামোসিস, হেমরেজিক এন্টারাইটিস, হাইমেনোলপসিস, ক্যাপিলারিসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ট্রক্সোপ্লাজমোসিস, র্যাবিস এবং এসক্যারিয়াসিস প্রভৃতি জীবাণুর বাহক হিসেবে কাজ করে। সাধারণত ইঁদুরের প্রস্রাব, বিষ্ঠা এবং চুল ফিডের সাথে মিশে সংক্রমণের কারণ হয়ে থাকে। এমনকি শেডের কর্মীদের মধ্যেও কিছু সংক্রমণ ছড়াতে সাহায্য করে এইসব ইঁদুর।
ফার্মে ইঁদুরের উপস্থিতি
খামারে ইঁদুর আছে তা সবসময় বোঝা যাবে না। তবে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখলে সহজে বোঝা যায় খামারে ইঁদুর আছে। শেডের মধ্যে ইঁদুরের কিচ কিচ আওয়াজ, দেয়ালের নিচের দিকে কোনো ছিদ্র, দেয়ালে উঠার শব্দ এবং ইঁদুরে ইঁদুরে ঝগড়া করা, ঘর বা গুদামে রক্ষিত ফিড ও অন্যান্য উপকরণ বস্তা কাটা দেখে, ইঁদুরের বিষ্ঠা, নষ্ট করা ফিড বা অন্য কিছুর মধ্যে যদি ইঁদুরের বিষ্ঠা পাওয়া যায় তাহলে বুঝবেন আপনার খামারে ইঁদুরের রাজত্ব চলছে। দেয়ালের দুর্বল বা সংযোগ স্থানে ইঁদুর গর্ত করে তাদের বাসা বানায়, লুকিয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার স্থানে তারা গর্ত করে। আবর্জনা মুক্ত স্থানে ইঁদুরের দৌড়াদৌড়ি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে গুদামঘরে তাদের উপস্থিতি বেশি দেখা যায়।
ইঁদুরের উৎপাদন খুব বেশি হলেই কেবল দিনের বেলায় দেখা যায়। তাদের দেখার জন্য রাতের বেলায় খুব শান্তভাবে খামারে প্রবেশ করে প্রায় ৫ মিনিট মতো নিশ্চুপ থেকে দেখলেই ইঁদুরের উপস্থিতি দেখা যাবে। ইঁদুরের গন্ধ এবং পোষাপ্রাণির লাফঝাঁপ বা অদ্ভুত আচরণ বা উত্তেজনা ইঁদুরের উপস্থিতি নির্দেশ করে। ইঁদুরের স্বভাবই হলো কাটাকুটি করা। কাঠের গুঁড়া, দরজা, জানালা, ফ্রেম, গুদামের জিনিসে ক্ষতির চিহ্ন দেখে এর আক্রমণের লক্ষণ বুঝা যায়। ঘরে বা তার পাশে ইঁদুরের নতুন মাটি অথবা গর্ত, ঘরের মধ্যে ইঁদুরের বাজে দুর্গন্ধ থাকলে বোঝা যাবে যে ইঁদুরের জনসংখ্যা বেশি।
ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ
ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের ২টি বিষয় থাকে। ১টি হলো ইঁদুর মেরে ফেলা এবং ফাঁদ দিয়ে ইঁদুর ধরা। অনেক পোল্ট্রি ফার্মে ইঁদুর পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। যারা ইঁদুর মারতে পারেন তাদের পুরস্কৃত করারও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ব্রিডার ফার্মে বেশি ভাগ সময়ই বড় জাতের ইঁদুরগুলোকে ফার্ম কর্মীরা পিটিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে।
প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। তাই নতুন শেড নির্মাণের ক্ষেত্রে ইঁদুরের প্রবেশ এবং বংশ বিস্তার রোধে সব ধরনের ব্যবস্থা রেখে ডিজাইন করে শেড নির্মাণ করতে হবে। ইঁদুর প্রবেশের সকল পথ বন্ধ করতে হবে। ইঁদুর অন্ধকার বা লুকানো জায়গায় থাকতে পছন্দ করে। তাই ইঁদুরের বিস্তার রোধ করতে অবশ্যই শেডের মধ্যের জায়গা পরিষ্কার এবং আলোযুক্ত রাখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় কিছুই রাখা যাবে না। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে যেন ইঁদুরের বসতি গড়ে উঠতে না পারে। শেডের মধ্যে নষ্ট অপ্রয়োজনীয় এবং ছিদ্রযুক্ত কোনো খাবার বা পানির পাত্র যেন থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
খামারে যদি ইঁদুরের বিস্তার লক্ষ করা যায় তাহলে নিম্নলিখিত উপায়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে- যেখানে ইঁদুরের ঘনত্ব কম থাকে সেখানে ফাঁদ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। ইঁদুর বিশুদ্ধ ছোলা, মাছ, মাংস ইত্যাদি খেতে খুব পছন্দ করে। ফাঁদ ব্যবহারের সময় এসব পছন্দের খাবার দিয়ে রাখতে হবে। তবে একটা বিষয় খেয়াল করলে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া যায় আর তা হলো আসল ফাঁদ দেয়ার পূর্বে কয়েক দিন ডেমো ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। এতে করে ইঁদুর তাতে প্রবেশ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। পরে ঘরের কোনায় বা অন্যান্য বস্তুর আড়ালে দিয়ে রাখলে অনেক ইঁদুর ধরা পড়বে। যেসব স্থানে ইঁদুরের প্রাদুর্ভাব বেশি সেসব স্থানে রাখতে হবে। বর্তমানে অনেক ধরনের ফাঁদ পাওয়া যায়। ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে ইঁদুর পিটিয়ে মেরে ফেলা যায়। ইঁদুরের গর্তে পানি ঢেলে ইঁদুর বের করে মেরে ফেলা যায়। ইঁদুর ধরার জন্য গুদামে বা ঘরে এক প্রকার আঠা সাধারণত কাঠের বোর্ডে, মোটা শক্ত কাগজে, টিনে, লাগিয়ে ইঁদুর চলাচলের রাস্তায় ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে এ ক্ষেত্রে বোর্ডের মাঝখানে লোভনীয় খাবার রাখতে হবে।
এ ছাড়াও ইঁদুর নির্মূলের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। সবার সমন্বয়ে একসাথে সমন্বিত ইঁদুর দমন পদ্ধতি ব্যবহার করলে নিরাপদ থাকবে কৃষিজ ও প্রাণিসম্পদের সকল প্রজাতি। নিরাপদ হবে আমাদের প্রাণিজ আমিষ। উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও খাদ্যের মান ভালো রেখে লাভবান হবেন খামারিরা। ইঁদুরের বিস্তার রোধ হলে রোগের বিস্তার কমবে খামারিদের চিকিৎসা খরচ কমবে এবং তারা লাভজনক অবস্থায় ফার্ম পরিচালনা করতে পারবে। এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। য়
প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (এলডিডিপি), উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মোবাইল : ০১৭২৩৭৮৬৮৭৭, ই-মেইল : : mmrdvm10@gmail.com
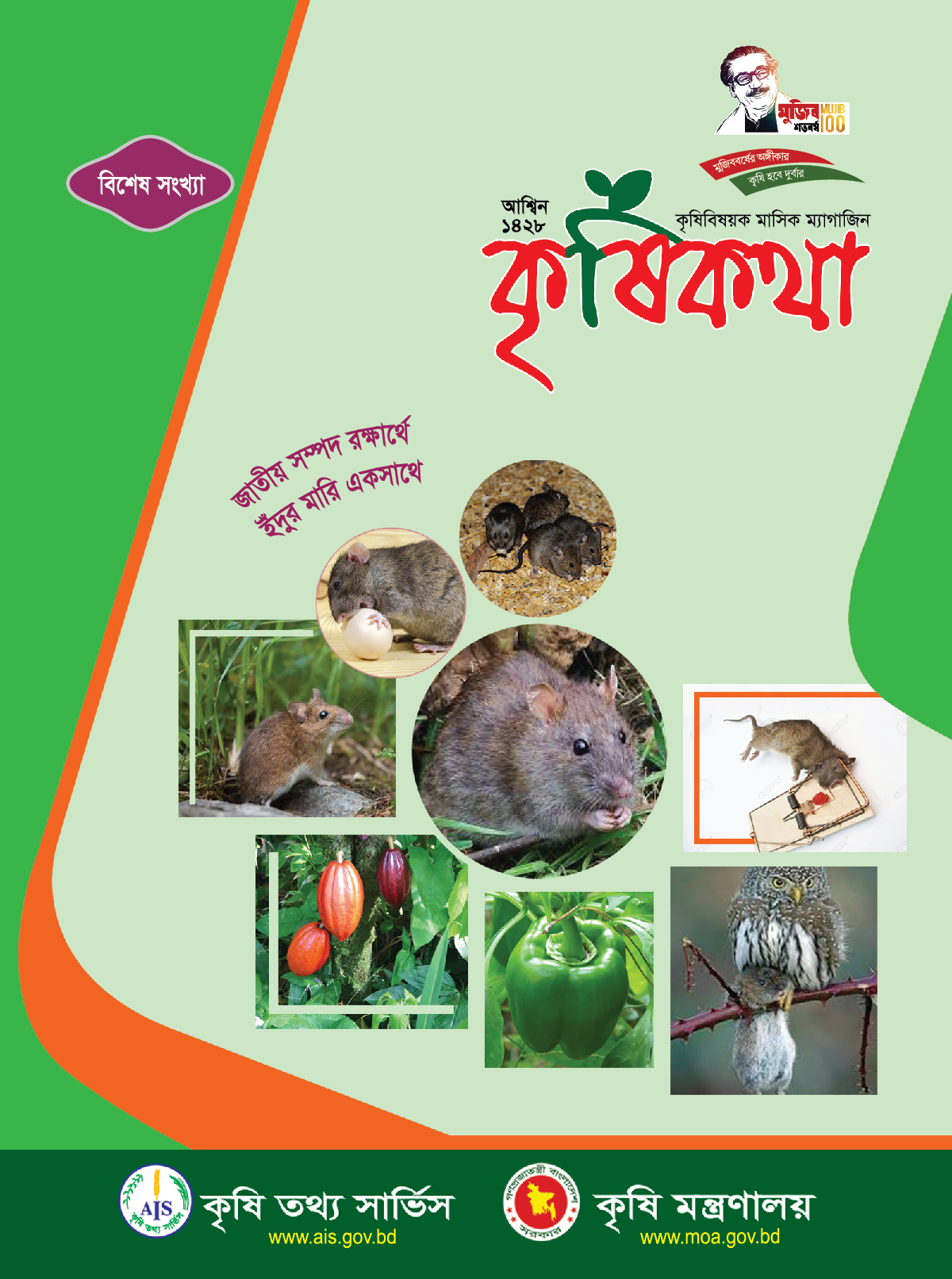 কবিতা (আশ্বিন-১৪২৮)
কবিতা (আশ্বিন-১৪২৮)
ইঁদুর নিধন
কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ
সেই কবেকার কথা
হ্যামিলনের বংশীবাদক ছিল একদা।
কোটি কোটি ইঁদুরের অত্যাচারী প্রাণ
বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুরে দেহ দিল দান।
আজ আর বাঁশি নেই, নেই তার সুর
ইঁদুরেরা রাজ করে, ফসলের ওপর।
লাখ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হয় বছরে
রাস্তা, বাঁধ, রেললাইন ভাঙে অকাতরে।
ঘরের কাপড় কাটে, কাটে সব তার
ঘরে মাঠে সবেতে রয়, রয় হাটবাজার।
ইঁদুর অনেক ছোট প্রাণী, বংশ বাড়ে দ্রুত
ইঁদুরের মল, লোম রোগ ছড়ায় শত।
টাইফয়েড, প্লেগ, কৃমি হয়, হয় জন্ডিস
আরো কত রোগ হয়, নেই তার হদিস।
কোটি কোটি মানুষের বছরের খাবার
ইঁদুর তা নষ্ট করে, করছে সাবাড়।
ধান, গম, সবজি, বাদাম, আলু, নারিকেল
কোনো কিছুই যায় না বাদ, নেই আক্কেল।
মাঠে ঘাটে ঘরে বাইরে যেখানেই পাবে
সমন্বিত দমন কর, তবেই সে যাবে।
দমনের পদ্ধতি আছে হাজার হাজার
রাসায়নিক, অরাসায়নিক পছন্দ যার যার।
দীর্ঘস্থায়ী বিষটোপ দিলে বেশি বেশি
সহজ হবে ইঁদুর নিধন, মরবে রাশি রাশি।
শিয়াল, বনবেড়াল, গুইসাপ, বেজি
পেঁচাও আছে তাদের দলে, মারতে ইঁদুর রাজি।
কাঠ, বাঁশ, লোহা দিয়ে তৈরি হয় ফাঁদ
গ্লুবোর্ড, টেঁটা আছে কিছু নেই বাদ।
একা কভু নয় সম্ভব ইঁদুর দমন
সম্মিলিত প্রচেষ্টার আছে প্রয়োজন।
একই দিনে একই সময়, সকলে করলে নিধন
দেশ হবে ইঁদুরমুক্ত, লাভবান হবে প্রতি জন।
নষ্ট হবে না একটি দানাও, অভাব হবে শেষ।
মাসব্যাপী নিধন অভিযান চলবে সারাদেশ
সোনার দেশের সোনার ফসল গড়বে সোনার দেশ। য়
ইঁদুর মারুন
পরিমল কুমার সাহা
সারামাঠ ঘুরে দেখলাম ইঁদুর খাচ্ছে ধান
ইঁদুর ধরে লেজ কাটছে গ্রামের যত পোলাপান
ইঁদুর থেকে কেমনে মুক্তি পাবো কওতো দেখি ভাই
ফসল রক্ষার কোনো উপায় কি কারোর জানা নাই!
মন্ডল চাষি ডেকে বলে শোন হিরন ভাই
মাঠের ইঁদুর কত ক্ষতি করে চলো দেখে যাই
শাকসবজি লাউ মুলা ক্ষেত, যতদূর চোখ যায়
হায়নার মতো ইঁদুরের দল সব লুট করে খায়
সেচ কাজে বিদ্যুতের তার কেটে ইঁদুর করে সাবাড়
সব জিনিসকে ইঁদুর ভাবে এটা তাদের খাবার
ছেলেমেয়ের বই খাতা কাটে, কাটে আলনার শাড়ি
হাঁস-মুরগির খাবার নষ্ট করে গ্রামের প্রতি বাড়ি।
মাথার ঘাম পায় ফেলে কৃষক ফলায় ধান
গর্তে বসে মনের সুখে ইঁদুর ধরে গান
গবেষণায় দেখা যায় ইঁদুরের ক্ষতির পরিমাণ
অর্ধকোটি মানুষের এক বছরের খাবারের সমান।
রাত কাটে দলবেঁধে ক্ষেতের কচি ধানের চারা
মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে, কৃষক দিশেহারা
জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক প্লেগ জন্ডিস রোগ
ইঁদুর ছড়ায় এসব রোগ,
বাড়ে মানুষের দুর্ভোগ
হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা আসবে কী আর ফিরে
সচেতন হয়ে ইঁদুর মারব দেখে যাও ভাই ধীরে
নারিকেল গাছের চারি দিকে ধাতবপাত ব্যবহারের ফলে
রক্ষা পাবে ডাব নারকেল টাকা যাবে না জলে
ধানের গোলা বসতবাড়ি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ
এসব জায়গায় পেতে রাখুন ইঁদুর মারা ফাঁদ
ইঁদুর ধরুন ইঁদুর মারুন ইঁদুর করুন শেষ
বদলে যাবে অর্থনীতি জেগে উঠবে দেশ।
১আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৭৫২৬৮৪০; ২ পোস্ট মাস্টার (অব.), ১১৭ লোহার গেট, বানিয়াখামার, খুলনা। মোবাইল : ০১৯৩০৩৫৯২০৩;
 প্রশ্নোত্তর (আশ্বিন-১৪২৮)
প্রশ্নোত্তর (আশ্বিন-১৪২৮)
প্রশ্নোত্তর
কৃষিবিদ ড. মো. তৌফিক আরেফীন
কৃষিবিষয়ক
নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য আপনার ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও রোগ দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করুন।
মো. বনী আদম, গ্রাম : সরফরাজপুর, উপজেলা : চৌগাছা, জেলা : যশোর।
প্রশ্ন : ডালিম গাছের পাতায় পানি ভেজা দাগ এবং ফলের উপর ছত্রাকের আবরণ পড়ে। ফল পচে যায়। কী করবো ?
উত্তর : ডালিম গাছের এ ধরনের রোগকে ডালিমের গ্রে মোল্ড বলে। এ রোগ হলে বোর্দো মিশ্রণ বা কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় ছত্রাকনাশক পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে সঠিক নিয়মে স্প্রে করতে হবে। তবেই আপনি উপকার পাবেন। এ ছাড়া রোগটি যাতে না হয় সেজন্য ফল সংগ্রহের পর মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা পোকা আক্রান্ত ডালপালা অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
মোছা: আসমা খাতুন, গ্রাম : পিরোজপুর, উপজেলা : মেহেরপুর সদর, জেলা : মেহেরপুর
প্রশ্ন : আমড়া গাছের পাতায় কালচে দাগ পড়ে এবং পিপীলিকার উপস্থিতি দেখা যায়। কী করবো?
উত্তর : শুঁটি মোল্ড হলে এমনটি হয়ে থাকে। এ সময় মিলিবাগ এর আক্রমণ বেশি হয়। এ রোগের প্রতিকার হলো-আক্রান্ত ডালপালা কেটে ফেলা, সময় মতো প্রুনিং করা। আর এসবের পাশাপাশি যদি আক্রমণ বেশি হয় তবে ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক ১ মিলি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে সঠিক নিয়মে স্প্রে করলে আপনি উপকার পাবেন।
মোঃ আলমগীর কবীর, গ্রাম : বাগমারা, উপজেলা : হোমনা, জেলা : কুমিল্লা
প্রশ্ন : আমার গোলাপ বাগানে কচি ডাল আগা শুকিয়ে মারা যাচ্ছে। এ সমস্যা রোধে কী করণীয়?
উত্তর : গোলাপের এ সমস্যাটিকে গোলাপের ডগা শুকানো রোগ বা ডাইব্যাক রোগ বলে। ডিপ্লোডিয়া রোসেরাম নামক ছত্রাক দ্বারা সাধারণত এ রোগ হয়ে থাকে। পুরাতন বাগানে এ রোগের প্রকোপ বেশি। এ সমস্যা রোধে আক্রান্ত ডাল কেটে পুড়ে ফেলতে হবে। এ ছাড়া ডাল কাটার সময় কালো অংশসহ কেটে বাদ দিতে হবে। কাটা ডালের মাথায় ৪ ভাগ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ৪ ভাগ রেড লেড ও ৫ ভাগ তিসির তেল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে লাগাতে হবে। এসবের পাশাপাশি কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের (যেমন-অটোস্টিন) প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে এবং প্রোপিকোনাজল (যেমন-টিল্ট ২৫০ ইসি) ১ লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। তাহলেই আপনি এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবেন।
মোঃ সাইদুর রহমান, গ্রাম : বামনডাঙ্গা, উপজেলা : আশাশুনি, জেলা : সাতক্ষীরা
প্রশ্ন : সরিষাক্ষেতে এক ধরনের আগাছার আক্রমণ যা সরিষার গাছের শিকড়ের সাথে যুক্ত। এখন আমি কী করবো?
উত্তর : অরোবাংকি নামক পরজীবী উদ্ভিদ এর কারণে সরিষা ক্ষেতে এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। বারবার একই জমিতে সরিষা ফসল চাষ করলে এ পরজীবী উদ্ভিদের বিস্তার হয়। এ সমস্যা দূরীকরণে ফুল আসার আগেই পরজীবী উদ্ভিদ জমি থেকে তুলে ধ্বংস করতে হবে। পরিমিত হারে টিএসপি সার ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়া পূর্বে আক্রান্ত জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে। আর সব শেষ ব্যবস্থা হিসেবে আগাছানাশক যেমন: ২, ৪-ডি ছিটিয়ে পরজীবী উদ্ভিদ দমন করা যায়। আশা করি এসব পদক্ষেপ নিলে আপনি উপকার পাবেন।
মোঃ আরশেদ আলী, গ্রাম : পূর্ব শ্যামপুর, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রশ্ন : আনারস গাছের কেন্দ্রীয় পাতার গোড়া পচে যায়। এ সমস্যা রোধে কী করণীয়?
উত্তর: এ সমস্যা আনারস গাছে দেখা দেওয়ার সাথে সাথে মেটালেক্সিল ও মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন রিডোমিল গোল্ড ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ থেকে ১০ দিন পরপর ২ থেকে ৩ বার সঠিক নিয়মে আনারস গাছে স্প্রে করতে হবে। আশা করি উপকার পাবেন।
মোছাঃ সনজিদা খাতুন, গ্রাম : সনগাঁও, উপজেলা : বালিয়াডাঙ্গি, জেলা : ঠাকুরগাঁও
প্রশ্ন : স্ট্রবেরি গাছের পাতায় ছোট বেগুনি রঙের দাগ পড়ে। পরবর্তীতে দাগের মাঝে সাদা আর চারদিকে বেগুনি রঙ দেখা যায়। এ ধরনের সমস্যায় কী করতে হবে? জানাবেন।
উত্তর : স্ট্রবেরি গাছের পাতায় এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়ার সাথে সাথে ইপ্রোডিয়ন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে অথবা এমিস্টার টপ ৩২৫এসসি ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ থেকে ১০ দিন পরপর ২ থেকে ৩ বার সঠিক নিয়মে আনারস গাছে স্প্রে করতে হবে। তাহলেই আপনার উল্লেখিত সমস্যার সমাধান হবে।
মৎস্য বিষয়ক
মোঃ আলমগীর, গ্রাম : দৌলতপুর, উপজেলা : নড়াইল সদর, জেলা : নড়াইল
প্রশ্ন : চিংড়ির ফুলকা কালো হয়ে গেছে কী করবো?
উত্তর : চিংড়ির ফুলকায় কালো ও পচন দেখা যায়, শ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটে এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা যায়। এ রোগের কারণ হচ্ছে পুকুরের তলদেশে জৈব পদার্থের পচন বৃদ্ধি পেলে এবং ফুসোরিয়াম ও ম্যাপ্রোলেগনিয়া ছত্রাক এ রোগের কারণ। এ সমস্যার প্রতিকারে হররা টেনে দ্রুত পানি পরিবর্তন করতে হবে। অ্যাসকরবিক এসিড ২০০ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি খাদ্যে মিশিয়ে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যাবে।
মোঃ শরীফ তালুকদার, গ্রাম : সরদারপাড়া উপজেলা : বাঘা, জেলা: রাজশাহী
প্রশ্ন : পানির রঙ গাঢ় সবুজ, মাছ মরে যাচ্ছে। কী করবো ?
উত্তর : অতিরিক্ত প্লাংকটন তৈরি হওয়ার কারণে এবং অক্সিজেন এর অভাব হলে এমন হয়। এ ধরনের সমস্যার প্রতিকারে প্রতি শতকে ১ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। খাবার ও রাসায়নিক সার সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে। পানির পরিমাণ বাড়াতে হবে। তুঁতে বা কপার সালফেট ১২-১৪ গ্রাম শতকহারে ছোট পোঁটলায় বেঁধে উপর থেকে ১০-১৫ সেমি. নিচে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে রাখলে ভালো হবে। সিলভার কার্প মাছ ছাড়া যেতে পারে। এ ছাড়া জিপসাম সার প্রয়োগ করতে পারেন শতকপ্রতি ১ কেজি করে। এভাবে ব্যবস্থা নিলে উপকার পাবেন।
প্রাণিসম্পদ বিষয়ক
মোঃ কবীর হোসেন, গ্রাম : বামইন, উপজেলা : নিয়ামতপুর, জেলা: নঁওগা
প্রশ্ন : আমার টার্কি মুরগির চোখের উপরে গুটি উঠে চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া মাথায়ও গুটি উঠেছে। এ অবস্থায় আমি কী করবো। পরামর্শ চাই।
উত্তর : আপনার টার্কির বসন্ত রোগ হয়েছে। এটি ভাইরাসজনিত রোগ। ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য ফাউল পক্সের ভ্যাকসিন দিতে হয়। আর রোগ হয়ে গেলে দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মক্সাসিল ভেট পাউডার অথবা এনফ্লক্স ভেট সলিউশন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।
মো: ফারুক হোসেন, গ্রাম : রনসিয়া, উপজেলা : পীরগঞ্জ, জেলা : ঠাকুরগাঁও
প্রশ্ন : আমার মুরগির বাচ্চার বয়স ১০-১৫ দিন। ঝিমাচ্ছে, মাথা ঝুলে পড়েছে। লাইটের নিচে জড়ো হয়ে আছে। বুকের চামড়ার নিচে ফুলে আছে। কী করবো পরামর্শ চাই।
উত্তর : অ্যামোক্সিসিলিন অথবা মোক্সাসিলিন অথবা কলিস্টিন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক খাওয়াতে হবে। ফুসিড ট্যাবলেট ১টা ২ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১ দিন খাওয়াতে হবে। স্যালাইন খাওয়াতে হবে। হ্যাচারির ইনকিউবেটরের মাধ্যমে আর্দ্রতা, তাপমাত্রা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে রোগের প্রতিরোধ ও বিস্তার রোধ করা সম্ভব।
(মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রশ্ন কৃষি কল সেন্টার হতে প্রাপ্ত এবং কৃষির যে কোনো প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান পেতে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে কল করতে পারেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ এ নাম্বারে।)
উপপ্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৫৫০২৮৪০০, ই মেইল :taufiquedae25@gmail.com
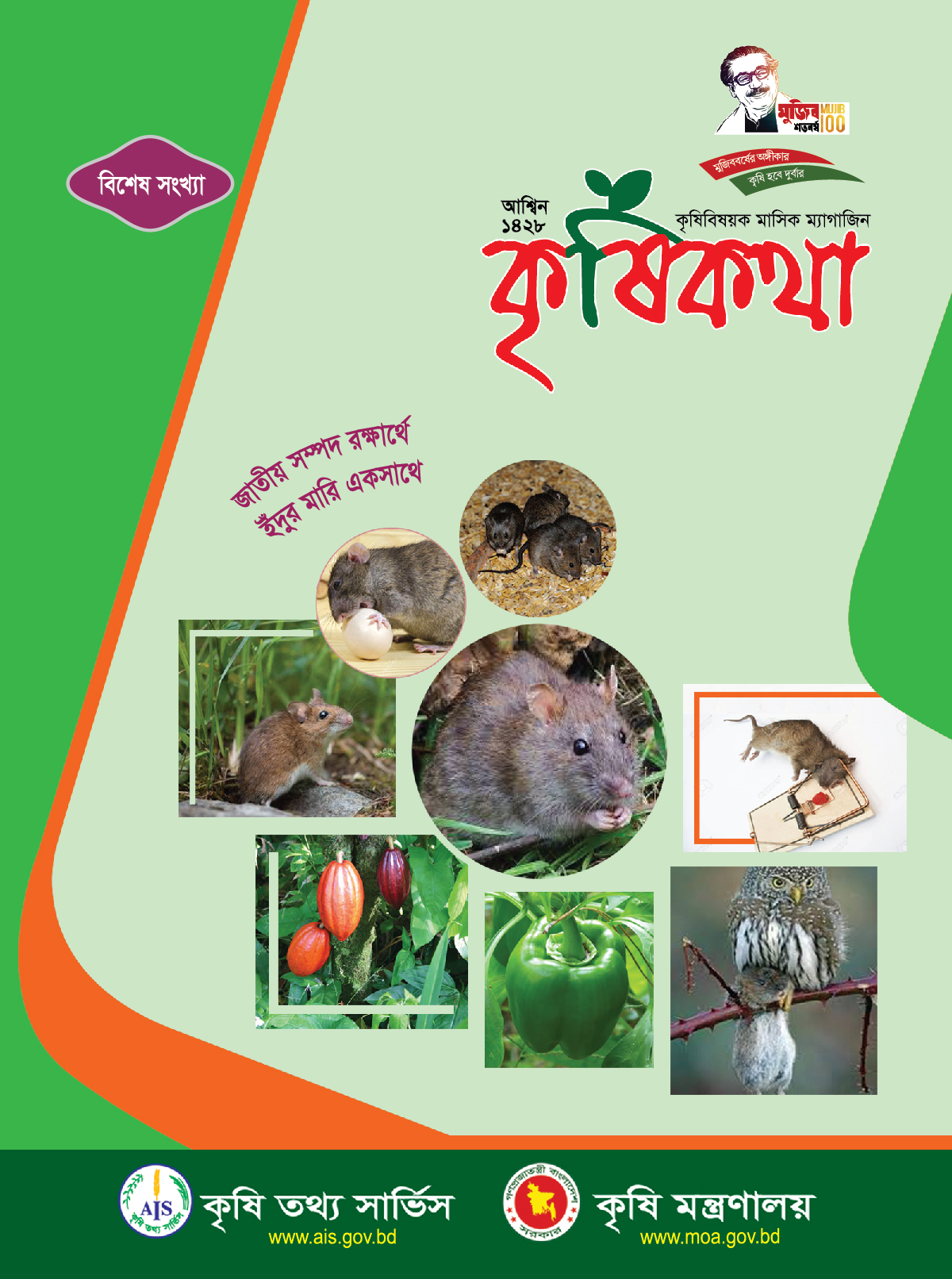 কার্তিক মাসের কৃষি (আশ্বিন-১৪২৮)
কার্তিক মাসের কৃষি (আশ্বিন-১৪২৮)
কার্তিক মাসের কৃষি
১৭ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর
এল কার্তিক, এল হেমন্ত। নতুন ঋতুর আগমনে রূপ বদলায় প্রকৃতি। এ যেন বর্ষা আর শীতের মিলনক্ষণ। বাংলার মাঠ প্রান্তর সোনালী ধানের সম্ভার সুঘ্রাণে ভরে থাকে । খাদ্য নিরাপত্তায় সোনালী প্রান্তরে বেড়ে যায় কৃষকের ব্যস্ততা। তাহলে আসুন আমরা জেনে নেই কার্তিক মাসে সমন্বিত কৃষির সীমানায় কোন কাজগুলো আমাদের করতে হবে।
আমন ধান
এ মাসে অনেকের আমন ধান পেকে যাবে তাই রোদেলা দিন দেখে ধান কাটতে হবে। আগামী মৌসুমের জন্য বীজ রাখতে চাইলে প্রথমেই সুস্থ সবল ভালো ফলন দেখে ফসল নির্বাচন করতে হবে। এরপর কেটে, মাড়াইঝাড়াই করার পর রোদে ভালোমতো শুকাতে হবে। শুকানো গরম ধান ঝেড়ে পরিষ্কার করে ছায়ায় রেখে ঠাণ্ডা করে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ রাখার পাত্রটিকে মাটি বা মেঝের উপর না রেখে পাটাতনের উপর রাখতে হবে। পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে ধানের সাথে নিম, নিসিন্দা, ল্যান্টানার পাতা শুকিয়ে গুঁড়া করে মিশিয়ে দিতে হবে।
গম
কার্তিক মাসের দ্বিতীয় পক্ষ থেকে গম বীজ বপনের প্রস্তুতি নিতে হয়। দো-আঁশ মাটিতে গম ভাল হয়। অধিক ফলনের জন্য গমের আধুনিক জাত যেমন- বারি গম-২৫, বারি গম-২৮, বারি গম-৩০, বারি গম৩২, বারি গম৩৩, ডাব্লিউএমআরআই গম১, ডাব্লিউএমআরআই গম২, ডাব্লিউএমআরআই গম ৩ এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু বিনা গম১ রোপণ করতে পারেন। বীজ বপনের আগে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। সেচযুক্ত চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ১৬ কেজি এবং সেচবিহীন চাষের জন্য বিঘা প্রতি ১৩ কেজি বীজ বপন করতে হবে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় এবং ইউরিয়া তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। বীজ বপনের ১৩-২১ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ প্রয়োজন এবং এরপর প্রতি ৩০-৩৫ দিন পর ২ বার সেচ দিলে খুব ভালো ফলন পাওয়া যায়।
আখ
এখন আখের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। ভালোভাবে জমি তৈরি করে আখের চারা রোপণ করা উচিত। আখ রোপণের জন্য সারি থেকে সারির দূরত্ব ৯০ সেমি. থেকে ১২০ সেমি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৬০ সেমি. রাখতে হয়। এভাবে চারা রোপণ করলে বিঘাপ্রতি ২২০০-২৫০০টি চারার প্রয়োজন হয়।
ভুট্টা
ভুট্টা চাষ করতে চাইলে এ সময় যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে এবং জমি তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে। ভুট্টার উন্নত জাতগুলো হলো খই ভুট্টা, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৭ বারি মিষ্টি ভুট্টা-১, বারি বেবি কর্ন-১ এসব। খরা প্রধান এলাকা ও সাদা দানার ক্ষেত্রে বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩, ঝড় বাতাসে হেলে ও ভেঙে পড়া প্রতিরোধী জাত ডাব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা ১ ডাব্লিউএমআরআই বেবি কর্ণ ১ আবাদ করতে পারেন।
সরিষা ও অন্যান্য তেল ফসল
কার্তিক মাস সরিষা চাষেরও উপযুক্ত সময়। সরিষার প্রচলিত স্বল্পমেয়াদি জাতগুলোর মধ্যে বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৭, বিনাসরিষা-৪, বিনাসরিষা-৯ ইত্যাদি, মধ্যমেয়াদি বারি সরিষা-১৮ এবং দীর্ঘমেয়াদি জাতগুলোর মধ্যে বারি সরিষা-১১, বারি সরিষা-১৬ উল্লেখযোগ্য। জাতভেদে সামান্য তারতম্য হলেও বিঘাপ্রতি গড়ে ১ থেকে ১.৫ কেজি সরিষার বীজ প্রয়োজন হয়। বিঘাপ্রতি ৩৩-৩৭ কেজি ইউরিয়া, ২২-২৪ কেজি টিএসপি, ১১-১৩ কেজি এমওপি, ২০-২৪ কেজি জিপসার ও ১ কেজি দস্তা সারের প্রয়োজন হয়। সরিষা ছাড়াও অন্যান্য তেল ফসল যেমন- তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী এ সময় চাষ করা যায়।
আলু
আলুর জন্য জমি তৈরি ও বীজ বপনের উপযুক্ত সময় এ মাসেই। হালকা প্রকৃতির মাটি অর্থাৎ বেলে দো-আঁশ মাটি আলু চাষের জন্য বেশ উপযোগী। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত আগামজাত ও উচ্চফলনশীল জাতগুলো নির্বাচন করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি ও খাবার উপযোগী জাত নির্বাচন করা প্রয়োজন। প্রতি একর জমি আবাদ করতে ৬০০ কেজি বীজ আলুর দরকার হয়। এক একর জমিতে আলু আবাদ করতে ১৩০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি, ১০০ কেজি এমওপি, ৬০ কেজি জিপসাম এবং ৬ কেজি দস্তা সার প্রয়োজন হয়। তবে এ সারের পরিমাণ জমির অবস্থাভেদে কমবেশি হতে পারে। তাছাড়া একরপ্রতি ৪-৫ টন জৈবসার ব্যবহার করলে ফলন অনেক বেশি পাওয়া যায়। আলু উৎপাদনে আগাছা পরিষ্কার, সেচ, সারের উপরিপ্রয়োগ, মাটি আলগাকরণ বা কেলিতে মাটি তুলে দেয়া, বালাই দমন, মালচিং করা আবশ্যকীয় কাজ। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মালচিং দিয়ে আলু আবাদ করা যায়।
মিষ্টিআলু
নদীর ধারে পলি মাটিযুক্ত জমি এবং বেলে দো-আঁশ প্রকৃতির মাটিতে মিষ্টিআলু ভালো ফলন দেয়। কমলা সুন্দরী, বারি মিষ্টিআলু-১২, বারি মিষ্টিআলু-১৪ বারি মিষ্টিআলু-১৫ ও বারি মিষ্টি আলু-১৬ আধুনিক মিষ্টি আলুর জাত। প্রতি বিঘা জমির জন্য তিন গিঁটযুক্ত ২২৫০-২৫০০ খণ্ড লতা পর্যাপ্ত। বিঘাপ্রতি ৪-৫টন গোবর/জৈবসার, ১৬ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৬০ কেজি এমওপি সার দিতে হবে।
ডাল ফসল
মুসুর, মুগ, মাসকলাই, খেসারি, ফেলন, অড়হর, সয়াবিন, ছোলাসহ অন্যান্য ডাল এসময় চাষ করতে পারেন। এজন্য উপযুক্ত জাত নির্বাচন, সময়মতো বীজ বপন, সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ, পরিচর্যা, সেচ, বালাই ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করতে হবে।
শাকসবজি
শীতকালীন শাকসবজি চাষের উপযুক্ত সময় এখন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বীজতলায় উন্নতজাতের দেশি-বিদেশি ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, বাটিশাক, টমেটো, বেগুন এসবের চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে। আর গত মাসে চারা উৎপাদন করে থাকলে এখন মূল জমিতে চারা রোপণ করতে পারেন। মাটিতে জোঁ আসার সাথে সাথে শীতকালীন শাকসবজি রোপণ করতে হবে। এ মাসে হঠাৎ বৃষ্টিতে রোপণকৃত শাকসবজির চারা নষ্ট হতে পারে। এ জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। রোপণের পর আগাছা পরিষ্কার, সার প্রয়োগ, সেচ নিকাশসহ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে। তাছাড়া লালশাক, মুলাশাক, গাজর, মটরশুঁটির বীজ এ সময় বপন করতে পারেন।
প্রাণিসম্পদ
সামনে শীতকাল আসছে। শীতকালে পোল্ট্রিতে রোগবালাইয়ের আক্রমণ বেড়ে যায়। রানীক্ষেত, মাইকোপ্লাজমোসিস,
ফাউল টাইফয়েড, বসন্ত রোগ, কলেরা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। এসব রোগ থেকে হাঁস-মুরগিকে বাঁচাতে হলে এ মাসেই টিকা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গত মাসে ফুটানো মুরগির বাচ্চার ককসিডিয়া রোগ হতে পারে। রোগ দেখা দিলে সাথে সাথে চিকিৎসা করাতে হবে।
গবাদিপ্রাণির আবাসস্থল মেরামত করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গবাদি প্রাণীকে খড়ের সাথে তাজা ঘাস খাওয়াতে হবে। ভুট্টা, মাসকলাই, খেসারি রাস্তার ধারে বা পতিত জায়গায় বপন করে গবাদি প্রাণীকে খাওয়ালে স্বাস্থ্য ও দুধ দুটোই বাড়ে। রাতে অবশ্যই গবাদি প্রাণীকে বাইরে না রেখে ঘরের ভিতরে রাখতে হবে। তা না হলে কুয়াশায় ক্ষতি হবে। গবাদি প্রাণীকে এ সময় কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে। এ ছাড়া তড়কা, গলাফুলা রোগের বিষয়ে সচেতন থাকলে মারাত্মক সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।
মৎস্যসম্পদ
এ সময় পুকুরে আগাছা পরিষ্কার, সম্পূরক খাবার ও সার প্রয়োগ করতে হবে। জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাও জরুরি। রোগ প্রতিরোধের জন্য একরপ্রতি ৪৫-৬০ কেজি চুন প্রয়োগ করতে পারেন। অংশদারিত্বের জন্য যেখানে যৌথ মাছ চাষ সম্ভব নয় সেখানে খুব সহজে খাঁচায় বা প্যানে মাছ চাষ করতে পারেন। এ ছাড়া মাছ সংক্রান্ত যে কোনো পরামর্শের জন্য উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আধুনিক কৃষির সবকটি কৌশল সঠিক সময়ে যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরা আমাদের কাক্সিক্ষত গন্তব্যে পৌঁছতে পারব। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।
সম্পাদক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা। টেলিফোন :০২৫৫০২৮৪০৪, editor@ais.gov.bd














